আমার ইংরেজী শেখা
সুকান্ত রায়, ১৯৭৭ ইলেকট্রনিক্স ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং
বীরভূম জেলা স্কুলে পড়ার সময় আমাদের ইংরেজীর শিক্ষক ছিলেন শ্রী সুধীর সেনগুপ্ত। রাবিন্দ্রীক চেহারা, চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা, আমাদের স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র, পরে প্রেসিডেন্সী। বাংলাও খুব সুন্দর বলতেন। আমরা যে মাঠটায় খেলতে যেতাম তারই একধারে ছিলো ওনাদের পৈতৃক বাড়ি। খেলা শেষ হলে প্রায়ই জল খেতে চলে যেতাম। সঙ্গে মিলতো গুড় বাতাসা, কখনও কখনও সন্দেশ।
অবিবাহিত লোক, মায়ের সঙ্গে থাকতেন। ভালো আবৃত্তি করতেন, দু’একদিন গুনগুন করে গান করতেও শুনেছি। সব মিলিয়ে বেশ একটা রমনীমোহন ব্যাপার। যে কোন যাত্রাপালায় (তখন আমাদের ওখানে যাত্রাই হতো বেশি, নাটক নয়) নায়কের ভূমিকায় অনায়াসেই মানানসই হতে পারতেন।
সুধীরবাবুর খুবই আফশোষ ছিল যে মফস্বল শহরে ইংরেজী পড়ানোর মতো হতাশা ও দুঃখজনক কাজ আর কিছু নেই। স্কুলে ইংরেজী পড়তে আসে পাশ করার জন্য, ভাষাটা শেখার জন্য নয়। বাংলা তবু মাতৃভাষা, শেখাটা সহজ কিন্তু ইংরেজী? গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা কি সম্ভব?
মাঝেমাঝেই এই সব দুঃখের কথা আমাকেই বিশেষ করে বলতেন। একদিন সন্ধ্যেবেলা ‘দেবতার গ্রাস’ আবৃত্তি করছেন, আমি বললাম “আপনিও তো বাংলায় কবিতা বলেন।” মুহূর্তের মধ্যে সুধীরবাবুর মুখের ভাব পালটে গেল। আমার দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষন তাকিয়ে থেকে বলতে শুরু করলেন “To be ,or not to be , that is the question: Whether ‘tis nobler in the mind to suffer. The slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing, end them. To die, to sleep; No more and by a sleep to say we end the heart ache and the thousand natural shocks. That flesh is heir to: ‘tis a consummation devoutly to be wished. To die, to sleep; to sleep perchance to dream – ay there’s the rub: For in that sleep of death what dreams may come, when we have shuffled off this mortal coil, must give us pause – there’s the respect that makes calamity of so long life …….”
আমি হতভম্বের মতো হাঁ করে বসে আছি দেখে নিজেই বললেন “আত্মহত্যা সম্পর্কিত ইংরেজী ভাষায় এর থেকে ভালো বিবরন কোন নাটকে বা লেখায় পাবিনা। ইংরেজী ভাষা শিখতে চাস? না ভাষাটাকে ভালোবাসতে চাস? আমি গুটিগুটি বাড়ি ফিরে এলাম। তখন আমার ক্লাস এইট, আর সুধীরবাবুর (আমরা সুধীরদা বলেই ডাকতাম) বয়স হবে সাতাশ।
গরমের ছুটিতে বাবা মা আমাদেরকে নিয়ে কোলকাতা চলে আসতেন। দিন সাতেক কলকাতায় থেকে বোনকে নিয়ে ওনারা আবার সিউড়ি ফিরে আসতেন। আর আমি দাদুর কাছে থেকে যেতাম স্কুল না খোলা পর্যন্ত। এটা প্রতিবছরের নিয়ম ছিল, এ বছরেও কোন অন্যথা হয়নি। কিন্তু এবার একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, আমার কলকাতার বন্ধুরা (আমি খুব ছোটবেলায় সেন্ট লরেন্সে পড়তাম) নিজেদের মধ্যে মাঝে মাঝেই ইংরেজীতে কথা বলছে। আমার বুঝতে একটু অসুবিধা দেখে ওরা আবার বাংলায় কথা বলা শুরু করে দিত। যদিও আমার বয়স তখন খুব বেশি নয়, তবুও আমি বেশ অপমানিত বোধ করলাম আর আমার রোখও চেপে গেল। আমায় ইংরেজি ভাষায় ভালো করে কথা বলা শিখতে হবে। গরমের ছুটির পর বাড়ি ফিরে সুধীরবাবুর বাড়ি গেলাম। কোন কুশল প্রশ্নের আগেই ওনাকে বললাম “আমি ইংরেজী শিখতে চাই।” উনি হেসে বললেন “শিখতে না ভালোবাসতে?”
– কাল থেকে বাবাকে বলে Statesman কাগজ রাখা শুরু কর। আর পড়বি খালি Editorial, আর খুব মন দিয়ে। তারপর খবরগুলো পড়বি।
আমি বললাম “আর বইপত্র?”
– আপাতত কোন দরকার নেই। তবে কিছুদিন বাদে নিজেই নিজের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলতে পারিস।
– লোকে পাগল ভাববে যে?
– বুঝলে তো? আমি যেরকম গুনগুন করে বাংলা গান গাই।”
সেই আমার প্রকৃত ইংরেজী ভাষা শেখার শুরু। প্রথম প্রথম গলদঘর্ম হয়ে যেতাম Editorial এর শক্ত শক্ত কথাগুলোর মানে বুঝতে। সুধীরবাবুর কাছে যাবার উপায় নেই। এই ঘটনার একমাসের মধ্যে উনি কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুলে বদলী হয়ে চলে গেলেন।
যারা সেইসময় Statesmen এর Editorial পড়তো, তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে ওই Editorial লেখার স্টাইল, আর শব্দচয়নের এক বিশেষত্ব ছিলো, যাকে বলে একেবারেই unique। ইংরেজী ভাষা ভালোবাসতে শেখানোর পক্ষে একেবারে আদর্শ। এখন এই বয়সে এতদিন পরেও আমি টাইমসের Editorial মাঝে মাঝে পড়ি কিন্তু সেই পুরু সর ওঠা খাঁটি ঘন দুধের স্বাদ আর পাইনা। তবে আমি আজ যেটুকে ইংরেজি পড়তে, বলতে লিখতে পারি, তার ভিত তৈরি করে দিয়েছিলেন ঐ বীরভুমের স্কুলের ইংরেজীর শিক্ষক শ্রী সুধীর সেনগুপ্ত।
স্কুলের গণ্ডী পেরিয়েছিলাম ১৯৭২ সালে। আর সম্প্রতি এই ২০২২ সালে, মানে পাশ করার পঞ্চাশ বছর পর মাথায় হঠাৎই ভুত চাপলো, স্কুল দেখতে যাবো। ১৯৭৭ সালে কলেজ থেকে পাশ করে কর্মসূত্রে প্রায় ৯০% সময় আমার কেটেছে বম্বে, দিল্লি আর আমেদাবাদে। বেশ কিছুটা সময় বিদেশে। সুতরাং গত পঞ্চাশ বছরে যে স্কুলের বা সুধীরদার কথা একবারও মনে পড়েনি, তা নয়। কিন্তু দূরে থাকার দরুন বা অত্যধিক আলস্যে আর যাওয়া হয়নি। তাই এবার ঠিক করলাম, আর দেরি নয়। কলকাতায় পারিবারিক কাজে এসেছি। ব্যাগ গুছিয়ে একদিন সকালে শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে চড়ে বেরিয়ে পরলাম ছোটবেলার স্কুল দেখতে।
ট্রেনে যেতে যেতে স্কুল, স্কুলের বন্ধু এবং অন্যান্য শিক্ষকদের থেকেও কেন জানি সুধীরদার কথাই বেশি করে ভাবতে লাগলাম। স্কুলের কোনো বন্ধুর সাথেই এখন আমার যোগাযোগ নেই। কলেজে ঢোকার পরই ডানা গজিয়েছিলো তাই মফস্বল স্কুলের বন্ধুরা বড় হবার পর কে যে কোথায় ছিটকে গেছে, খোঁজ রাখিনি, রাখার চেষ্টাও করিনি। তারপর differential equation, acoustic theory, digital electronics, microwave আর line communication, এদের যাঁতাকলে ইংরেজীর ভালোবাসা যে কখন কোথায় হারিয়ে গেল বুঝতেই পারিনি। তবুও প্রথম প্রেম কি সহজে ভোলা যায়? যতবারই ইংরেজী পড়তাম, সুধীরদার কথাগুলো বুকে বাজতো।
সুধীরদা এখন কেমন আছে? বিয়ে করেছে নিশ্চয়ই, সংসারী যখন, ছেলেপুলেও হয়েছে। ছেলেপুলেরা কি সুধীরদার মতোই ইংরেজী পাগল, নাকি বিজ্ঞান বা অর্থনীতির ছাত্র? তারা কি সিউড়িতেই থাকে, সেই বাড়িটাতেই? ওটা তো ওদের পৈতৃক বাড়ি ছিলো। সুধীরদা কি রিটায়ার করার পর ওখানেই ফিরে এসেছে? দেখতে তো দারুন ছিলেন, বৌদিও কি সেরকমই দেখতে? প্রেমে পড়েছিল বলে তো জানতাম না। নাতি, নাতনীও থাকবে হয়তো। এইসব ভাবতে ভাবতে ট্রেনটা যখন বোলপুর স্টেশনে ঢুকছিল, হঠাৎ মনে হল সুধীরদা বেঁচে আছে তো? বড় দেরী হয়ে গেছে, অনেক আগেই আসা উচিত ছিলো। হয়তো অনেক অভিমান জমে আছে, পাশ করার পর কোনো যোগাযোগ রাখার চেষ্টাও করিনি। স্বার্থপরের মতো নিজের সুবিধাটুকু হাতিয়ে কেটে পড়েছি। ট্রেন থেকে নামতে নামতে ঠিক করলাম, এসেই যখন পড়েছি একবার দেখে যাবো।
পরদিন সকালে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সিউড়ি। বর্ষাকাল, সারাক্ষন টিপটিপে বৃষ্টি। সিউড়ি শহরটা এতো ঘিঞ্জি হয়ে গেছে চেনাই যায়না। স্টেশনের লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে যখন শহরে ঢুকছি, মনে হল এটা কি আমার শহর? কোথায় সেই ডাঙ্গালপাড়ায় সাইকেল চালানোর মাঠ? এ তো বাড়ির পাশে বাড়ি, রাস্তা ভর্তি প্রাইভেট বাস, স্কুটার, টোটো আর প্রাইভেট গাড়ি। তারই পাশে ঝুপড়ি দোকানঘর, আর ক্রমাগত বিকট আওয়াজে হর্ণের শব্দ। কোর্টের মোড়ে প্রচন্ড জ্যাম, ট্র্যাফিক সিগনাল অচল, এক সিভিক ভলান্টিয়ার ততোধিক ছোট একটি কঞ্চি নিয়ে ভগ্নদূতের মতো রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে যে কি করছে, তা সেই জানে। মোড়টা থেকে ডানদিকে জেলা স্কুলের রাস্তায় ঢুকে দেখি দুদিকে ঝুপড়ি দোকানে রাস্তা এতো সরু যে একটা গাড়ি গেলে উল্টোদিক থেকে আরেকটা গাড়ি আসতে পারবে না। গোদের ওপর বিষফোঁড়া রাস্তার দুধারে তরকারির বাজার বসেছে। সব মিলিয়ে সে এক ক্যাডাভ্যারাস অবস্থা। আমার ড্রাইভার উত্তম বলল “স্যার, নেমে হেঁটে চলে যান। বেশিদূর নেই, আমি গাড়িটা পার্কিংয়ের চেষ্টা করি।”
স্কুলের হেডমাস্টার চন্দন সাহা, মাথায় চকচকে টাক, মুখে পুরুষ্টু গোঁফ, চোখে চশমা, অমায়িক লোক। কথায় কথায় বললেন যে আমি যে বছর পাশ করেছি, উনি তার চার বছর বাদে, ১৯৭৬ সালে পৃথিবীর আলো দেখেছেন। আমাদের সময়কার হেডমাস্টারমশাইদের যেরকম গোমড়াথেরিয়ামের মতো মুখ, কড়া চাউনি আর হাতে একটা বেত থাকতো, ইনি মোটেই সেরকম নন। ইনি বেশ হাসিখুশি, জিন্স আর টি শার্ট পরা একজন গপ্পে লোক। আমি পঞ্চাশ বছর বাদে এসেছি শুনে চোখ কপালে তুলে বললেন “চলুন, আপনাকে স্কুলটা ঘুরিয়ে আনি”। কথায় কথায় জানতে চাইলাম সুধীরদার কথা। উনি বললেন যে সুধীরবাবু এখানেই থাকেন, মাসে একবার করে স্কুলেও আসেন। এই স্কুল থেকেই রিটায়ার করেছেন। আমি আর দেরি না করে বৃষ্টির অজুহাত দিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম।
আমাদের স্কুলের যে খেলার মাঠটা ছিল, সেটা এখন আর স্কুলের নেই, সিউড়ি পুরসভার অধীনে। সেটা এখন মাঠ বলে চেনা যায়না, তার চারধারে পাঁচিল, চারদিকে দোকান। অনেক খুঁজেপেতে, দিকনির্ণয় ও জিজ্ঞাসাবাদ করে বাড়িটার সামনে দাঁড়ালাম। আগে একতলা বাড়ি ছিলো, এখন দোতলা হয়েছে। দরজায় বেল দিতে আটপৌরে শাড়ি পরা এক প্রৌঢ়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দাঁড়ালেন। আন্দাজে বুঝলাম মাষ্টারগিন্নী, মুখটা চেনাচেনা লাগছিল, তবুও মাঝখানে পঞ্চাশ বছর, তাই বেশি মাথা না ঘামিয়ে বলে ফেললাম “আমি সুধীরবাবুর ছাত্র”।
“সুধীরবাবুর ছাত্র? উনি স্নানে গেছেন, আপনি একটু বসুন। আপনার নামটা?”
নিজের নাম বললাম।
উনি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন “সোনাতোড় পাড়ায় থাকতে?”
– হ্যাঁ
– তোর নাম মিঠু?
এতো তাড়াতাড়ি আপনি থেকে তুমি থেকে তুই তে নেমে যাওয়ায় এবার আমার অবাক হবার পালা। চোখ কপালে তুলে বললাম “আপনি কি করে জানলেন?”
– আপনি? সেকি রে? তুই আবার কবে থেকে আমায় আপনি বলতি?
সব্বোনাশ, এতো দেখছি মহা ফ্যাসাদ, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবার যোগাড়। আমার হতভম্ব অবস্থা দেখে বললেন “চা খাবি না কফি?”
আমি শত চেষ্টাতেও চিনতে না পেরে বললাম “এক গ্লাস জল।”
– বোস, পাঠিয়ে দিচ্ছি। এতোদিন পরে এদিকে কি ভেবে?
এ প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই, তাই চুপ করে রইলাম। উনি কিছুক্ষন আমার দিকে তাকিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।
মিনিট দুয়েক পর একটি বাচ্চা মেয়ে এক গ্লাস জল নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল “তুমি ঠাম্মার বন্ধু?”
– কি জানি, বুঝতে পারছিনা।
– মিথ্যে বলবেনা, ঠাম্মা যে বললো তুমি ঠাম্মার বন্ধু।
– তাহলে হবে হয়তো।
– বন্ধুকেও চিনতে পারোনা? কিরকম লোক রে বাবা।
মেয়েটি কথাগুলো বলে গ্লাসটা রেখে ভেতরে চলে গেল।
আমার তখন এক একটা মূহুর্ত এক একটা ঘন্টা। কিছুতেই মনে করতে পারছিনা মহিলাটি কে। সুধীরদার স্ত্রী হবে হয়তো, কিন্তু আমায় কি করে চিনলো? জিজ্ঞেস করার আগেই কেটে পড়লো। তুই করে কথা বলায় মনে হয় ভালোই চিনতাম। কি কুক্ষনেই যে এসেছিলাম। এখন যখন চিনে গেছে আর তো কেটে পড়া যাবেনা। এইসব ভাবতে ভাবতে ঢকঢক করে জলটা খেয়ে ফেললাম।
দরজার পর্দা সরিয়ে এক ভদ্রলোক “জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণাধারায় এসো…………” গুনগুন করতে করতে বসার ঘরে ঢুকলেন। সেই নায়কোচিত চেহারা, বয়স আশি ছুঁই ছুঁই, শরীর টানটান, মেদের চিহ্নমাত্র নেই, সোনালী ফ্রেমের চশমার ফাঁকে উজ্জ্বল দৃষ্টি – চুল পাকলেও এনাকে চেনা সহজ। সেই চেনা দরাজ গলা
“To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
Creeps in this pretty face from day to day,
To the last syllable of recorded time;
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out, brief candle!
Life’s but a walking shadow, a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more.
It is a tale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing.”
আমি অস্ফুট স্বরে ম্যাকবেথ বলে নীচু হয়ে প্রণাম করতেই মাথায় হাত দিয়ে বললেন “এতোদিনে মনে পড়লো?

I cannot teach anybody anything; I can only make them think.
– Socrates
******

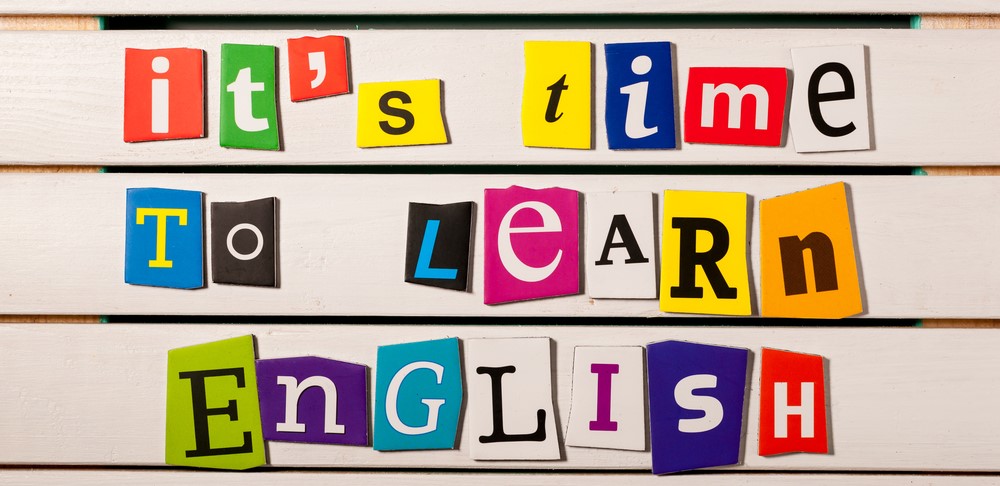














বাঃ এই তো বেশ ঝরঝরে বাংলাতে একটা অপূর্ব সুন্দর লেখা লিখেছিস।এত সুন্দর বাংলা ভাষা থাকতে কেন যে সবাই মাইকেল হতে চায় বুঝি না।আহাঃ বেশ ভাল লেখা,একটু কি কল্পনার ছোঁয়া আছে?হতেই পারে বহুদিন আগের কথাতো! খালি গুরু পত্নীর সাথে পরিচয়টা একটু রহস্যের আড়ালেই থেকে গেল।যাক,সব জানতে নেই।