এলোমেলো বেড়ানো: ধারাবাহিক পঞ্চদশ পর্ব
@অমিতাভ রায়, ১৯৭৯ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
আগের পর্ব পড়তে হলে, লিংক
https://sahityika.in/2025/07/25/%e0%a6%8f%e0%a6%b2%e0%a7%8b%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b2%e0%a7%8b-%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8b-%e0%a6%a7%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b9-10/
মৈদাম
পিরামিড দেখতে লোকে মিশরে যায়। তবে পা এবং পকেটের জোর বেশি থাকলে অনেকেরই পছন্দ হবে মেহিকো। উত্তর আমেরিকা মহাদেশের কালাকমুল বায়োস্ফিয়ারে অবস্থিত মায়া সভ্যতার সময়কালের পিরামিড দেখতে হলে মেহিকো না গেলেই নয়। আর নিতান্তই ছোটো আকারের পিরামিড দেখতে হলে দক্ষিণ কোরিয়ার পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে হবে। ১৩৯২ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত জোসেওন বংশের যে রাজারা কোরিয়া শাসন করতেন তাঁদের সমাধি দেশের অন্ততঃ ১৮টি জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে। চূড়ান্ত বিচারে সব পিরামিডই তো রাজা-রানির সমাধিগৃহ। কিন্তু আহোম রাজাদের সমাধিগৃহ যা স্থানীয় ভাষ্যে মৈদাম বলে পরিচিত সেটি দেখতে যায় কতজন?


মৈদাম দেখতে হলে চরাইদেউ যেতে হবে। সে আবার কোথায়? আসামের শিবসাগর জেলার অন্যতম মহকুমা ছিল চরাইদেউ। ২০১৫-র ১৫ আগস্ট থেকে চরাইদেউ হয়ে গেলো আলাদা জেলা। ভু-গর্ভস্থ তেল আর প্রাকৃতিক গ্যাসের সুবাদে জেলার সদর শহর সোনারি অবিশ্যি দেশের শিল্প মানচিত্রে বহুদিন ধরেই সুপরিচিত।
শিবসাগরে বিমানবন্দর নেই। কাজেই ট্রেনে অথবা জাতীয় সড়ক ধরেই শিবসাগর আসতে হবে। এখান থেকে শিমলুগুড়ি যাওয়ার রাস্তায় সোনারির দিকে কমবেশি তিরিশ কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করলেই চরাইদেউ-র বিশাল তোরণ স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। তোরণের উপর বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা রয়েছে, – সুকাফা নগর।
এখানে রেলিং দিয়ে ঘেরা সুরক্ষিত সমাধি স্থল। টিকিট কেটে ভেতরে প্রবেশ করলেই নজরে পড়ে লাল পাথরের জাফরি গাঁথা একটি অষ্টভূজাকৃতি ছোট্ট মন্দির। স্থানীয় ভাষ্যে, – লেঙডন মন্দির। লেঙডন দেবতাদের রাজা। ১২২৮ থেকে ১৮২৬ পর্যন্ত সিংহাসনে আসীন আহোম রাজারা নিজেদের লেঙডনের উত্তরসূরি বলে বিবেচনা করতেন। আহোম রাজারা বংশের প্রাচীন প্রজন্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্যই নাকি চরাইদেউ-র প্রবেশ পথে স্থাপন করিয়েছিলেন স্বর্গ-মর্ত্যের অধীশ্বর লেঙডনের মন্দির। লেঙডনের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রেই নাকি আহোম রাজারা নিজেদের নামের শেষে ফা উল্লেখ করতেন। ফা শব্দের অর্থ,– অধিপতি। এবং আহোম রাজবংশের প্রবর্তক প্রথম রাজার নাম,– সুকাফা।
পরিক্রমা শুরু করলে ডাইনে-বামে যেদিকে নজর যায় সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে অর্ধ-গোলাকার মৃত্তিকা স্তুপ। অনেকটা বৌদ্ধ স্তুপের আকারে নির্মিত ঘাসাচ্ছাদিত মাটির স্থাপত্য। প্রতিটি সমাধি-স্তুপের অর্থাৎ মৈদামের অভ্যন্তরে রয়েছে একেকজন রাজার সমাধি। চরাইদেউ-র সদর দরজা থেকে শুরু করে বহু দূরে আবছা আবছা নজরে আসা নাগা পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ৭০০ একর জমির ওপর স্থাপিত হয়েছে ৪২টি মৈদাম। অর্থাৎ আহোম রাজবংশের ৪২ জন রাজার সমাধি।

আহোম রাজত্বে রানিরা কি অবহেলিত? মোটেও নয়। চরাইদেউ থেকে বেরিয়ে শিমলুগুড়ি যাওয়ার পথে তিন-চার কিলোমিটার এগোলেই রাস্তার বাঁ পাশে পড়ে দৌলবাগান চা বাগিচা। এই চা বাগিচার শেষ সীমানা থেকে শুরু করে নাগা পাহাড় পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে অনেকগুলি মৈদাম। আকারে অনেক ছোটো। লোকশ্রুতি যে এইসব মৈদামের গর্ভগৃহে শায়িত রয়েছে আহোম রানিদের সমাধি। আহোম রাজত্বের বিভিন্ন জায়গায় সবমিলিয়ে শ’-দেড়েক মৈদামের হদিশ পাওয়া গেলেও শুধুমাত্র চরাইদেউতে অবস্থিত রাজকীয় মৈদামগুলিই যথার্থ ভাবে সংরক্ষিত।
আকারে ছোটো বড়ো হলেও প্রতিটি মৈদামের স্থাপত্য রীতি প্রায় একই রকম। ইঁটের দেওয়াল গেঁথে ঘিরে রাখা এক খন্ড অষ্টভুজ আকারের জমি। এই দেওয়ালই আসলে মৈদামের ভিত। সবচেয়ে বড়ো ভূখণ্ডের পরিসীমা ৩৬০ মিটার। অর্থাৎ অষ্টভুজ ভূখণ্ডের এক একটি বাহু কমবেশি ৪৫ মিটার দীর্ঘ। দেওয়ালের উচ্চতা ১ মিটার হলেও প্রস্থ কিন্তু ১ মিটার ছাড়িয়ে গেছে। ইটগুলিও দেখার মতো। নানান মাপের ইট। সবচেয়ে বড়োটির দৈর্ঘ্য ২৫ সেন্টিমিটার। আর সবচাইতে ছোটো ইটটির উচ্চতা সাড়ে তিন সেন্টিমিটার। সবমিলিয়ে অন্ততঃ ছ’-ছটি মাপের ইট প্রতিটি মৈদাম তৈরির সময় ব্যবহার করা হয়েছিল। এমন বিভিন্ন মাপের ইট ভারতীয় উপ-মহাদেশের অন্য কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে নজরে পড়ে কি?

দেওয়াল ঘেরা এই ভূখণ্ডের মধ্যে গড়ে উঠেছিল মৈদামের গর্ভগৃহ। প্রয়াত রাজার মরদেহর সঙ্গে তাঁর পাত্র-মিত্র মায় পরিচারক-পোষ্য প্রাণীও মৈদামের গর্ভগৃহে স্থান পেত। কাঠ ও হাতির দাঁতের কারুকার্য করা শবাধারে অলঙ্কার-রত্নাদিও সাজিয়ে রাখা হত বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। কথিত আছে ব্রিটিশ আমলে বিদেশি সৈন্যরা বেশ কয়েকটি মৈদামের গর্ভগৃহে রাখা মূল্যবান সম্পদ লুট করে নিয়ে যায়। এখনও পর্যন্ত যে দু’-তিনটি মৈদামের ভেতরে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সর্বেক্ষণের বিশেষজ্ঞরা প্রবেশ করতে পেরেছেন তার থেকে এই ধারণাই স্পষ্ট হয় যে বহুকাল ধরে চলতে থাকা লুটতরাজের লোকশ্রুতি মোটেও কাল্পনিক নয়।
সযত্নে নির্মিত মৈদামের গর্ভগৃহে প্রয়াত রাজা এবং তাঁর সঙ্গীসাথীদের যথাযথ মর্যাদায় সমাধিস্থ করার পর তার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হত মাটি। মৈদামটি অর্ধ-গোলাকৃতির আকার না পাওয়া পর্যন্ত মাটি চাপানোর কাজ বন্ধ হত না। নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে মৈদামের চূড়োয় স্থাপিত হত একটি ছোট্ট মন্ডপ। চৌ চালি । চৌ চালিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার প্রচলন ছিল।
এখনকার মতো সে যুগেও রাজা বা প্রশাসনিক প্রধানের মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুঃসংবাদ প্রকাশ্যে প্রচারিত হত না। রাজার প্রয়াণের পর রাজ-পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যবৃন্দ এবং রাজসভার মন্ত্রী-পাত্র-মিত্র অর্থাৎ যাঁরা ডাঙ্গরীয়া নামে স্বীকৃত, তাঁরা সমবেত হয়ে নতুন রাজা নির্বাচনের পর একই সঙ্গে প্রচারিত হত রাজার প্রয়াণের দুঃসংবাদ ও নতুন রাজা নির্বাচনের শুভ বার্তা।
নতুন রাজার প্রথম কাজ ছিলো পূর্বসূরীর মরদেহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কী ধরনের শবাধার নির্মাণ করা হবে তা নির্ধারণ। সমান্তরাল ভাবে চলতে থাকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত প্রচলিত লৌকিক ক্রিয়াকর্মাদি। এবং মৈদাম নির্মাণের কাজ।
মৈদাম নির্মাণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল জমি নির্বাচন। জমি বাছাই হয়ে গেলে শুরু হত ভূমির শুদ্ধিকরণ। নির্বাচিত ভূ-খণ্ডের ওপর সোনা-রূপার মুদ্রা ছড়িয়ে দিলেই ভূমি শুদ্ধ হয়ে যায় বলে প্রচলিত বিশ্বাস। অতঃপর মৈদামের গর্ভগৃহে অবস্থিত সমাধি নির্মাণের সূচনা।
সমাধি কক্ষ, যা কারেং-রুয়াং-ডাং নামে পরিচিত, সাধারণত শাল কাঠ দিয়ে তৈরি তিন-চার কামরা বিশিষ্ট একটি কক্ষ। আহোম রাজের সূচনাপর্বে আবশ্যিক ভাবে শাল কাঠের কারেং-রুয়াং-ডাং নির্মাণ করার প্রচলন থাকলেও পরবর্তী সময়ে ইট-পাথরের তৈরি কারেং-রুয়াং-ডাং নির্মিত হয়েছিল। ১৬৯৬-এ আহোম রাজা সুপাতফা ওরফে গদাধর সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুখরুংফা ওরফে স্বর্গদেও রুদ্র সিংহ ইট-পাথরের একটি দ্বিতল কারেং-রুয়াং-ডাং নির্মাণ করিয়েছিলেন।

মৈদামের গর্ভগৃহে অবস্থিত কারেং-রুয়াং-ডাং এত প্রশস্ত আকারে নির্মাণের মূল কারণ, – প্রয়াত রাজার সঙ্গে তাঁর পরিচারক-পরিচারিকা তো বটেই এমনকি তাঁর পোষ্য প্রাণীদেরও সমাধি দেওয়া হত। ক্ষেত্র বিশেষে হাতি-ঘোড়াও নাকি সমাধিতে স্থান পেত। আহোম রাজা প্রতাপ সিংহ যিনি ১৬০৩ থেকে ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন, তাঁর মা মারা যাওয়ার পর যে মৈদাম তৈরি হয় তার গর্ভগৃহে শবাধারের সঙ্গে পাঠানো হয়েছিল চারটি হাতি, দশটি ঘোড়া এবং সাতজন মানুষ।
রাজবাড়ির রীতিনীতি প্রজারা অনুকরণ করে। সারা বিশ্বে এমনটাই দস্তুর। কাজেই সাধারণ মানুষ মারা গেলেও তাঁর বাড়িতে গাঁথা হত মৈদাম। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের জন্য নির্মিত মৈদাম আকারে রাজা-রানির মৈদামের তুলনায় অনেক ছোটো। আর সেইসব মৈদামে রাজবাড়ির অনুকরণে জীবিত মানুষ অথবা প্রাণি পাঠানো হত কিনা তার খবর পাওয়া যায়নি।
কালের প্রবাহে মৈদাম গুরুত্ব হারিয়েছে। তবে একেবারে গুরুত্বহীন হওয়ার আগেও একটা পর্যায় ছিল। ১৭৫১ থেকে ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করার পর মারা গেলেন আহোম রাজ রাজেশ্বর সিংহ। মরদেহ সৎকারের জন্য তাঁর উত্তরসূরি লক্ষ্মী সিংহ তিন সদস্যের মন্ত্রিসভা অর্থাৎ ডাঙ্গরীয়া-র সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। সিদ্ধান্ত হল প্রয়াত রাজার মরদেহ ব্রহ্মপুত্রর তীরে দাহ করা হবে। এবং সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয় অর্থাৎ মরদেহ দাহ করা হয়। রাজকীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রচলিত প্রথা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া দেওধাই বা পুরোহিতদের পছন্দ নয়। দেওধাইদের উদ্যোগে সর্বত্র অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ল। রাজতন্ত্রের সঙ্গে পুরোহিততন্ত্র সাধারণত সখ্যতা বজায় রাখতে অভ্যস্ত। পৃথিবীর সব দেশেই এমনটাই প্রচলিত রীতি। তার ব্যতিক্রম হলেই শুরু হয় নানানারকমের অশান্তি। নতুন রাজা লক্ষ্মী সিংহ অশান্তি দূর করতে আগ্রহী। কিছুদিন বাদে বিষয়টি একটু থিতিয়ে যাওয়ার পর দেওধাইদের সঙ্গে রাজবাড়ির আলোচনার মাধ্যমে একটা সমাধান সূত্র খুঁজে পাওয়া গেল। চরাইদেউ-তে প্রয়াত রাজার মৈদামের স্থান পূর্বনির্ধারিত। রাজার নশ্বর দেহ দাহ করার পর ভষ্মাবশেষ পূর্বনির্ধারিত স্থানে সমাধিতে রেখে তার উপরে গড়ে তোলা যায় মৈদাম।
এমন সহজ সমাধান সূত্র মেনে নিয়ে কিন্তু রাজেশ্বর সিংহের মৈদাম নির্মাণ করা গেল না। কারণ, রাজেশ্বর সিংহের নশ্বর দেহ দাহ করার পর ভষ্মাবশেষ সংরক্ষণ করা হয়নি। অতএব শুরু হল আবার আলাপ-আলোচনা। কিঞ্চিৎ জটিল হলেও বেরিয়ে এল নতুন সমাধান। সোনা এবং কুশ দিয়ে রাজেশ্বর সিংহের দু’টি মূর্তি তৈরি করা হল। কুশের মূর্তিটিকে দাহ করে তার ভষ্মাবশেষ সযত্নে সংগ্ৰহ করে চরাইদেউতে নিয়ে গিয়ে স্বর্ণমূর্তির সঙ্গে একত্রে সমাধিস্থ করে তার উপরে গড়ে তোলা হল রাজেশ্বর সিংহের মৈদাম।
প্রচলিত সামাজিক প্রথা পরিবর্তন বা সংস্কারের প্রচেষ্টা স্থান-কাল নির্বিশেষে পৃথিবীর সর্বত্র প্রাথমিক পর্যায়ে প্রত্যাখ্যাত হয়। এটাই বোধ হয় চিরায়ত বিধি। আহোমেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। পরবর্তী সময়ে আহোম রাজত্বের অবসানের পর নানাবিধ কারণে ভষ্মাবশেষ সমাধিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা বাতিল হয়ে গেলেও আহোম রাজবংশের কোনো কোনো শাখা-প্রশাখার উত্তরসূরিরা নিয়ম রক্ষার তাগিদে মরদেহের ভষ্মাবশেষ সাদামাটা ভাবে সমাধিস্থ করার আয়োজন করে থাকেন। এমনকি আহোম রাজত্বের প্রভাব যে সমস্ত এলাকায় ছিল সেখানেও সাধারণ মানুষের মধ্যে এই পদ্ধতির প্রচলন এখনও রয়েছে।
বাগরাকোট

বাগরাকোট। অচেনা অজানা জায়গা নয়। শিলিগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার হয়ে কোচবিহার যাতায়াতের সময় বাগরাকোটের ওপর দিয়েই যাওয়া-আসা করতে হয়। এমনকী ডুয়ার্সের পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে যেতে গেলেও বাগরাকোটকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। অর্থাৎ এককথায় বাগরাকোট ডুয়ার্সের দুয়ার। শিলিগুড়ি থেকে রেলপথে ঘন্টা দেড়েক। গুলমা, সেবক পার হলেই পরের স্টেশন বাগরাকোট। সড়ক সফরে দূরত্ব দশ কিলোমিটার বেশি হলেও সময় লাগে সোয়া ঘন্টা। উছলে পড়া সবুজ। উন্মুক্ত আকাশ। ঝকঝকে রোদ্দুর। শনশন হাওয়া। রাতের আকাশে তারারা কাঁপে। আর চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে চা বাগান। দূরে দিগন্তরেখায় সাজানো রয়েছে হিমালয়। শীতের দিনে ঝকঝকে রোদ্দুর উঠলে এখন থেকেই দেখা যায় বহু বিখ্যাত পর্বত-শৃঙ্গ।
শান্ত রেল স্টেশন, ব্যস্ত জাতীয় সড়ক, বহতা নদী, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, দূষণহীন বাতাস আর বিশাল চা বাগান হল বাগরাকোটের সম্পদ। রীতিমতো বনেদী ও অভিজাত চা বাগান। দেশের প্রাচীন চা বাগানগুলির অন্যতম। ১৮৭৬-এ বাগরাকোট চা বাগান যাত্রা শুরু করলেও এখন আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। বাগানের প্রাণচঞ্চল কর্মজীবন মাঝেমধ্যেই হোঁচট খেয়ে থমকে গিয়ে এখন ধুঁকছে। অপুষ্টি-অনাহার-আত্মহননে গত কয়েক বছরে অন্ততঃ জনা পঞ্চাশ শ্রমিক অথবা তাঁদের পরিবারের সদস্যের জীবনাবসান হয়েছে।
বাগরাকোটে আর রয়েছে ভারতীয় বিমানবাহিনীর ফায়ারিং রেঞ্জ। অনেককালের পুরোনো চাঁদমারি। দেশের পঞ্চাশটি ফায়ারিং রেঞ্জের অন্যতম। দিনের পারাবারে রাত্রি মিশে যাওয়ার লগ্নে কানে ভেসে আসে ‘ঠাস ঠাস দ্রুম দ্রুম’। অর্থাৎ শুরু হয়ে গেছে চাঁদমারির কর্মব্যস্ততা। পদাতিক সৈন্যের দল গুলি করতে করতে এগোতে থাকে। কামান দাগে গোলন্দাজ। গুলি ছোটে। মর্টার থেকে ছিটকে পড়ে গোলা। সবমিলিয়ে এক ধুমধুমার পরিস্থিতি।
এই পরিসরে অকুস্থলে উপস্থিত আরেক বাহিনী। এদের পরনে নেই ফৌজি উর্দি। দেখলেই বোঝা যায় এরা কোনো সুশৃঙ্খল বাহিনীর সদস্য নয়। এদের বয়সের কোনো বাঁধন নেই। বাচ্চা-বুড়ো-নবীন-প্রবীণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সের পুরুষ ও নারী এই বাহিনীর সদস্য। ক্ষুধায় ক্লান্ত শুকনো মুখ। শতচ্ছিন্ন ময়লা পরিধান। অথচ উদ্দেশ্যে অবিচল। দায়িত্ব পালনে অনিশ্চল। মৌনতা মুখর নৈর্ব্যক্তিক আচরণ।
চাঁদমারিতে সেনাবাহিনীর সদস্যদের দুটো ভাগ। একদল তোপ দাগে। আরেকদল না-ফাটা গোলাগুলি নিষ্ক্রিয় করার কাজে নিযুক্ত। সকলেই নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে নিজের নিজের দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত। যান্ত্রিক নিয়মে কাজ চলে। একেক লপ্তে চার বার বিস্ফোরণ। প্রথম তিনবার নিয়মের নিগড়ে উত্তেজনাবিহীন ভাবেই হয়ে গেল বিস্ফোরণ। আর একবার হলেই সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় দল না-ফাটা গোলাগুলি নিষ্ক্রিয় কাজ শুরু করে দেবে। না-ফাটা বোমা-গোলা-গুলি সবচেয়ে বিপজনক। যে কোনো মুহুর্তে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিপদ ডেকে আনতে পারে।

তবে তৃতীয় বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙে পড়ে নিয়মের শৃঙ্খল। এতক্ষণ নিস্পৃহ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মূক-মলিন বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে চাঁদমারির ময়দানে। রীতিমতো আলোড়ন। ব্যবহৃত গুলির শেল, কার্তুজের আবরণ, মর্টারের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে নিজের নিজের ঝোলায় ভর্তি করার জন্যে সে এক ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতা। নাকি প্রতিদ্বন্দ্বিতা? চতুর্থ বারের বিস্ফোরণ এখনও কিন্তু বাকি আছে। কার নিষেধ, আর কে-ই বা শুনছে!
প্রত্যেক লপ্তের শেষ বা চতুর্থ তোপ দাগার আগে সেনাবাহিনী যথেষ্ট সতর্ক। ময়দানে হুটোপাটি করতে থাকা শতখানেক বা শ’-দেড়েক মানুষের ক্ষয়-ক্ষতির আশঙ্কায় সৈনিকের অবস্থান বদলায়। আগের জায়গা থেকে অনেকটা পিছিয়ে এসে তোপ দেগে পালিত হয় নিয়ম রক্ষার দায়িত্ব।
বাগরাকোট চাঁদমারিতে বিমানবাহিনীও মহড়া দেয়। একসঙ্গে নীল দিগন্তে উড়ে যায় চার চারটে ফৌজি বিমান। আকাশে ভাসতে থাকা বিমান থেকে একসঙ্গেই বোমা বর্ষণ করে প্রতিদিন যাচাই হয় বিমান এবং বোমার সক্রিয়তা। একই সঙ্গে বৈমানিকের দক্ষতারও পরীক্ষা হয়ে যায়। সারাদিনে অন্তত বারো-চোদ্দো বার বিমানগুলি আকাশে ওড়ে। এবং উড়ন্ত বিমান থেকে চাঁদমারির ময়দানে আছড়ে পড়ে নানান ধ্বংস ক্ষমতার বিভিন্ন ওজনের বোমা। শুধু দিনের আলোয় নয় রাত্রির অন্ধকারেও অনেক সময় গুলি-গোলা, বোমা-মর্টার পরীক্ষার কাজ চলে। এবং সবসময়ই অকুস্থলে উপস্থিত স্থানীয় মানুষের মূক -মলিন বাহিনী।

বিধি মেনে মহড়ার আগে স্থানীয় থানায় খবর পাঠালে মালবাজার থানা থেকে একজন হোমগার্ড চাঁদমারিতে আসেন। বেচারি! সমবেত মানুষের বাহিনীকে সামলানো কি একাকী মানুষের পক্ষে সম্ভব? আবার থানা থেকে সুবিশাল পুলিশবাহিনী পাঠানোও সম্ভব নয়। থানায় আর কতজন পুলিশ থাকে! কাজেই মহড়ার সময় সেনা আধিকারিকরাই রীতিমতো আশঙ্কা আক্রান্ত। বহিরাগতদের সংখ্যা বেড়ে গেলে বাধ্য হয়েই মহড়ার সঙ্গে সমঝোতা না করে উপায় কী! যে দূরত্ব থেকে গুলি ছোঁড়ার কথা, সময় বিশেষে তা কমিয়ে আনতে হয়। কারো গায়ে কার্তুজের সামান্য আঁচড় কেটে গেলেও চতুর্দিকে হই চই পড়ে যাবে। সেই হট্টগোল ক্ষণেকের মধ্যে আইন শৃঙ্খলার সমস্যায় পরিণত হতে পারে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রত্যন্ত এলাকার ছাউনিতে দায়িত্ব পালন করতে এসে অযাচিত সমস্যায় জড়িয়ে না পড়ে সামান্য সমঝোতা করে কার্যোদ্ধার অনেক সহজ।
যাঁদের নিয়ে এত চিন্তা-ভাবনা তাঁরা কিন্তু নির্ভীক। তাঁদের জীবন যেন শাঁখের করাত। পেটের জ্বালা তাঁদের চাঁদমারিতে টেনে আনে। আবার এখানে সামান্য অসতর্ক হলেই প্রাণ নিয়ে টানাটানি। জীবনধারণের জন্যে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যে মানুষগুলি প্রতিদিন এক ভয়ঙ্কর আপোস করে দিন কাটায় তা বোধ হয় সামরিকবাহিনীর নিয়ম রক্ষার সমঝোতার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
সামরিকবাহিনী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। স্থানীয় মূক-মলিন বাহিনীর সদস্যদের কাছে অস্ত্র নেই। প্রত্যেকের কাঁধে শুধুই ঝোলা আর হাতে শিক। রাতের বেলায় হাতে ওঠে একটা টর্চ। বাগরাকোট চাঁদমারিতে মাঝে-মধ্যে রাত-বিরেতেও আকাশ থেকে বোমা বর্ষণের মহড়া হয়। তখনও যে তড়িঘড়ি ছুটে আসাটা একান্তই প্রয়োজন। রাত পোহালে যে কিছুই পড়ে থাকবে না।
নৈশ অভিযানের আগাম খবর পেয়ে গেলে অনেকে আবার একটু বাড়তি ঝুঁকি নিয়ে চাঁদমারিতেই রাত কাটানোর আয়োজন করে। অবশ্যই গোপনে। সারা রাত নয়। বোমা বর্ষণ পর্যন্ত। মহড়া শেষ হলেই ব্যাগ-বস্তা ভরে, যদি কিছু পাওয়া যায়, রাস্তায় নামা। চাঁদমারির ময়দানের কোনো এক প্রান্তে কোনো এক গর্তে কানে আঙ্গুল চাপা দিয়ে প্রতীক্ষা। কখন মহড়া শেষ হবে।
গর্ত কে খোঁড়ে? আকাশ থেকে ঝরে পড়া বোমার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত চাঁদমারির ময়দান। সেই গর্তগুলিকেই আড়ে-বহরে আর গভীরতায় একটু বাড়িয়ে নিলেই হয়ে যায় মাথা গুঁজে, হাঁটু দুমরিয়ে, কোমর মুচড়িয়ে লুকিয়ে থাকার সাময়িক ঠাঁই।
সামরিকবাহিনীর আধুনিকতম আগ্নেয়াস্ত্র থেকে ছোঁড়া গুলি বা কামানের গোলা কিংবা মর্টার চাঁদমারির কোন বিন্দুতে গিয়ে পড়ল সেদিকে সকলের তীক্ষ্ণ নজর। ছুঁড়ে দেওয়া গুলি-গোলা বা মর্টারের ধাতব খোল মাটিতে গড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একাধিক দাবিদার। অনেকসময় বিস্ফোরণের সাদা-কালো ধোঁয়া কুন্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে ওপরে ওঠা বন্ধ হওয়ার আগেই একাধিক হাত দখল নিতে চায় শূন্য খোলের দখল। ধাতব খোল হয়তো তখনও গনগনে গরম। হাত পুড়ে যাওয়ার আশঙ্কাকে ভ্রূক্ষেপ না করেই কোনো এক দাবিদার পরম আদরে খোলটিকে তুলে নিয়ে সরাসরি কাঁধের ঝোলায় চালান করে। সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে বিজয়ীর হাসি।
মাটির ভেতরে সেঁধিয়ে যাওয়া খোলটিকে উদ্ধারের জন্যে কাজে লাগে হাতের শিক। সদ্য ব্যবহৃত খোল উদ্ধারে অনেক দাবিদার একসাথে হানা দেওয়ায় অনেক সময় একটু আধটু গালিগালাজ, হাতাহাতি, মারামারি হয় বইকি। তা হোক, খোলটার পাতাল প্রবেশ তো আটকানো গেল।
রাতের বিমান মহড়ায় ব্যবহৃত বোমার খোল খুঁজতে একটু অসুবিধা হয়। ওজন-গতি এবং বিস্ফোরণের মাত্রা বেশি হওয়ায় খোলগুলি তাড়াতাড়ি মাটির গভীরে গেঁথে যায়। অন্ধকারে ধোঁয়ার কুন্ডলীও ভালো করে নজরে আসে না। তখন কিছুটা আওয়াজে, খানিকটা আন্দাজে আর বাকিটা অভিজ্ঞতায় খুঁজে নিতে হয় অকুস্থল। বাঁ হাতের টর্চ আর ডান হাতের শিক কাজে আসে। রাতে ঝুঁকি বেশি হলেও প্রতিদ্বন্দী কম।
গোলা-গুলি-বোমা-মর্টারের খোল থেকে কী মেলে? লোহা, পিতল, সীসা, সিলভার এবং অন্য কিছু সঙ্কর ধাতব পদার্থ। সিলভার মানে কিন্তু রূপা নয়। স্থানীয়রা যাকে সিলভার বলতে অভ্যস্ত তা আসলে খুব ভালো মানের আল্যুমিনিয়াম। বিক্রি করতে অসুবিধা নেই। মালবাজারে নিয়ে গেলেই হাতে হাতে নগদ টাকা। ব্যবসার প্রয়োজনে অনেক ক্রেতা চাঁদমারির বাইরেই দাঁড়িপাল্লা সাজিয়ে বসে থাকেন। এক কেজি লোহা আট থেকে দশ টাকা। পিতল দুশো। কখনও আরও বেশি। সরাসরি বাসনপত্র তৈরি করা যায় বলে পিতলের দাম একটু চড়া। সীসা একশো দেড়শো। আর সিলভার সত্তর-আশি টাকা।
সাহসে ভর করে উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাজ করতে পারলে দিনে একশো দেড়শো টাকা রোজগার কোনো ব্যাপার নয়। শক্তিশালী, কর্মক্ষম এবং সাহসী কমবয়সীদের জন্যে এত সহজ রোজগারের কোনো বিকল্প আছে কি? বয়স্কদের অবিশ্যি বেশির ভাগ দিনই খালি হাতে ফিরতে হয়। তবু যেতে হয়। সেই যে,–কথায় আছে না–আশায় বাঁচে চাষা।
নদীর ধারের এই চাঁদমারিতে কোনো সীমানা প্রাচীর নেই। সেনা ছাউনির মতো স্থানীয় প্রশাসনও বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত। যে কোনো দিন বড়োসড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ছোটোখাটো আঘাত লাগা, হাত পুড়ে যাওয়া বা আহত হওয়া তো নিত্যকার ঘটনা। না-ফাটা গুলি-গোলা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়ার সময়ও দুর্ঘটনা ঘটে। প্রাণহানিও হয়। ঘটনাস্থলে না হলেও গুরুতর আহতদের অনেকেই পরে মারা যায়। নিয়মিত সীসা ঘাঁটাঘাঁটি থেকে শরীরে যে সংক্ৰমণ ছড়ায় তার হিসেব কে রাখে?
বছর কয়েক আগে ওরাওঁ জনজাতির চার চারটি কিশোর, সকলেরই বয়স বারো-চোদ্দো বছর, চাঁদমারির এক দুর্ঘটনায় আহত হল। চাঁদমারির ময়দানে কুড়িয়ে পাওয়া এক ধাতব গোলক নিয়ে ওরা লোফালুফি করছিল। বস্তুটি যে না-ফাটা কোনো গলা সেটা বুঝে ওঠার আগেই বিস্ফোরণ ঘটে। আহত চারজনকে একই সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। একটি কিশোর বাঁচেনি। পাড়া-পড়শিরা কদিন কান্নাকাটি করল। পুলিশ গ্রামে এল। স্থানীয় খবরের কাগজে একটা খবর ছাপা হল। তারপর, যে কে সেই। পেশাগত ব্যাধির মতো এ হল পেশার ঝুঁকি।
বাগরাকোট চাঁদমারির মতো দেশের অন্যান্য চাঁদমারিগুলিও দূর দূরান্তের প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত। সত্যি বলতে কী, অন্যান্য অনেক চাঁদমারির তুলনায় বাগরাকোটের সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশি। সড়ক ও রেল পরিষেবার সুবাদে বাগরাকোট দুর্গম নয়। কাছাকাছির মধ্যে রয়েছে শিলিগুড়ির মতো ব্যস্ত শহর। জেলা শহর জলপাইগুড়ির দূরত্ব মাত্র সত্তর কিলোমিটার। অন্য কোনো চাঁদমারিতে এমনটা ঘটে কিনা বলা মুশকিল। অন্তত তেমন কোনো খবর নেই। অথচ সেইসব চাঁদমারিরও আশপাশে ছড়িয়ে আছে চুড়ান্ত দারিদ্র। শুধুমাত্র বাগরাকোট চাঁদমারিতেই কেন স্থানীয় মানুষের এমন আগ্রাসী অন্বেষণ?
উত্তর খুঁজতে সরেজমিনে তদন্তে নামলে জানা যায় যে অন্যত্র চাঁদমারির চারপাশে বসবাসকারী মানুষদের সামান্য হলেও চাষবাসের সুযোগ আছে। যেখানে কৃষিকাজ নেই সেখানে অন্য পেশায় যুক্ত থাকার সুযোগ আছে। কোথাও মাছ ধরার কাজ আবার কোথাও রয়েছে অরণ্যের সম্পদ আইনি প্রথায় সংগ্রহের সুযোগ। পাথরের খাদান খোঁড়া বা নদীর বালি সংগ্রহের অবকাশও অনেক চাঁদমারির আশপাশের এলাকায় রয়েছে। বাগরাকোটে কিন্তু সেই ভাবে কোনো বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই।
বাগরাকোট চাঁদমারির পাশেই সাড়ে সাত হাজার হেক্টর জমিতে ছড়িয়ে রয়েছে বিশাল চা বাগান। শুরুর সময় থেকেই পূর্ব ভারতের নানান এলাকা থেকে বিভিন্ন জনজাতির মানুষকে এখানে এনে বাগিচার কাজে জুতে দেওয়া হয়েছিল। এখনকার ওডিশা, ঝাড়খন্ড, বিহার এবং পশ্চিম বাংলার কয়েকটি জেলা থেকে নিয়ে আসা সাঁওতাল, মুন্ডা, ওরাওঁ থেকে শুরু করে পাহাড় থেকে নেমে আসা গোর্খা জনজাতির মানুষ প্রায় দেড়শো বছর ধরে একসঙ্গে একই পেশায় যুক্ত থাকার ফলে তাঁদের একটাই পরিচয়,– চা শ্রমিক। চা বাগানের কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজেই তাঁদের পারদর্শিতা নেই। এখানে কোনো কৃষিকাজের সুযোগও নেই। কাজেই চাঁদমারির পাশের সোনালী বা সাতগাঁও থেকেই নয়, প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও রোজগারের আশায় বহুদূরের ময়নাগুড়ি থেকে শুরু করে ওদলাবাড়ি, এলেনবাড়ি, ফুলবাড়ি, শিকারপুর, ডামডিম থেকেও লোক আসে।
একশো চল্লিশ বছরের পুরোনো চা বাগানকে বনেদী বা অভিজাত যা-ই আখ্যা দেওয়া যাক না কেন বাস্তবে এখন তা ধুঁকছে। অন্য কোনো কাজের সুযোগ না থাকায় স্থানীয় মানুষ হানা দেয় চাঁদমারির ময়দানে। লুটপাট নয়, চুরিচামারিও নয় নেহাতই বর্জ্য সংগ্রহ। জীবন বাজি রেখে রোজগারের এমন রোজনামচা আরও কতদিন চালু থাকবে বলা কঠিন।
ডুয়ার্সের অন্যত্র পর্যটনের প্রসার হলেও বাগরাকোট সেই মানচিত্রে জায়গা পায়নি। আশার কথা, বাগরাকোট থেকেই শুরু হবে সরাসরি গ্যাংটক যাওয়ার নতুন জাতীয় সড়ক। হয়তো তখনই এখানকার জনজীবনে আসবে এক নতুন মাত্রার পরিবর্তন। এবং খুলে যাবে জীবনের ঝুঁকি না নিয়ে রোজগারের কোনো এক নতুন রাস্তা।
** লেখক পরিচিতি: অমিতাভ রায়
প্রশিক্ষিত প্রযুক্তিবিদ ও পরিচিত পরিকল্পনাবিশারদ। পড়াশোনা ও পেশাগত কারণে দেশে-বিদেশে বিস্তর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। তার ফসল বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় বই। জোয়াই, আহোম রাজের খোঁজে, প্রতিবেশীর প্রাঙ্গণে, কাবুলনামা, বিলিতি বৃত্তান্ত ইত্যাদি।
******

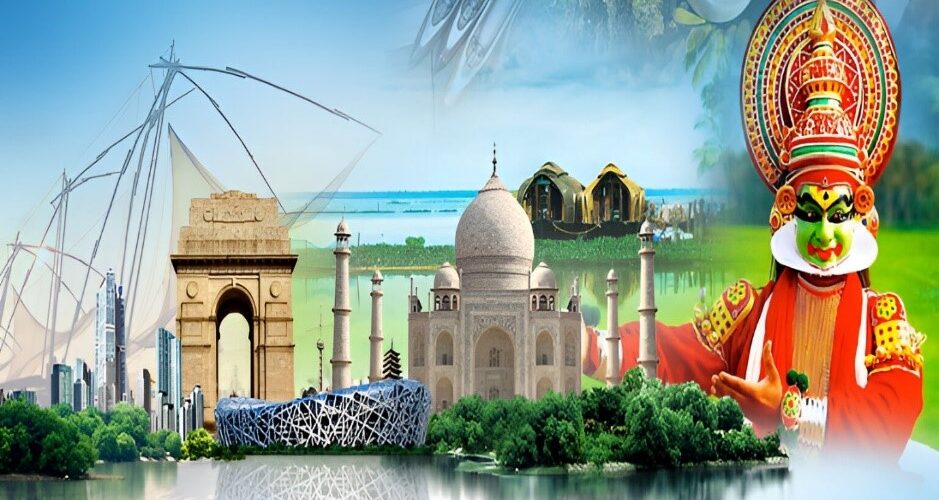
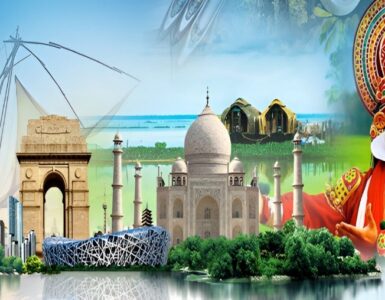













অসাধারণ একটা গল্প পড়লাম বাগরাকোট নিয়ে।গতবছর ডুয়ার্সের একটা চা বাগান,মূর্তি নদীর তীরে বাংলোতে রাতে থেকেছি,হয়তো যাতায়াত করার সময় অজান্তেই বাগরাকোট অঞ্চল পেরিয়ে গেছি ।জায়গাটার যে এমন একটা করুন কাহিনী আছে তা আমার অজানা ছিল,হয়তো অনেকেই এখনও জানেন না।অনেক ধন্যবাদ জানাই।