রবীন্দ্রনাথের কন্যা (ধারাবাহিক) (দ্বিতীয় পর্ব সোহিনী)
@অমিতাভ দত্ত, ১৯৭০ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সে, ১৯৪০ সালে প্রকাশিত “তিনসঙ্গী” গ্রন্থে রয়েছে “রবিবার”, “শেষ কথা” আর “ল্যাবরেটরি”, এই তিনটি ছোটগল্প। “রবিবার”-এর “বিভা”, “শেষকথা”-র “অচিরা” ও “ল্যাবরেটরি”-র সোহিনী সময় ও সভ্যতা – কেন্দ্রিক নারীর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার একেকটি উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, গল্প এবং কবিতায় বিভিন্ন নারী চরিত্র এমন ভাবে বর্ণিত হয়েছে যে বিস্মিত হতে হয় রবীন্দ্রনাথ একজন পুরুষ হয়েও নারীমনের বিভিন্ন দিক এমন নিঁখুত ভাবে আবিষ্কার করেছিলেন কি ভাবে?
“মুক্তি” কবিতায় একটি ব্যর্থ নারীজীবনের আর্তি রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন এই ভাবে –
“এ সংসারে এসেছিলাম ন – বছরের মেয়ে,
তারপরে এই পরিবারের দীর্ঘ গলি বেয়ে
দশের ইচ্ছা বোঝাই করা এই জীবনটা টেনে টেনে শেষে
পৌঁছিনু আজ পথের প্রান্তে এসে।
জানি নাই তো আমি যে কী, জানি নাই এ বৃহৎ বসুন্ধরা
কী অর্থে যে ভরা।
শুনি নাই তো মানুষের কী বাণী
….. আমি কেবল জানি
রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা
বাইশ বছর এক – চাকাতেই বাঁধা।“
সোহিনীকে জানতে হ’লে শুরু ক’রতে হবে নন্দকিশোর মল্লিককে দিয়ে। ভদ্রলোক ছিলেন ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র, লন্ডন য়ুনিভার্সিটি থেকে পাস করা এঞ্জিনিয়ার। জীবনের প্রয়োজনও ছিল প্রচুর কিন্তু আর্থিক সম্বল ছিল না। তিনি ঢুকে পড়লেন রেলওয়ে কোম্পানির ব্রিজ বিভাগে। দুটো বড় ব্রিজ তৈরীর কাজে বাঁ হাতে প্রচুর অর্থ রোজগার করলেন। সেই রোজগারে নন্দকিশোরের মনে কোন “দোষী” ভাব ছিল না। উনি মনে করতেন (এবং ঠিকই মনে করতেন) যে ওঁর উপরওয়ালা সাহেবদের জ্ঞান এবং দক্ষতা কম হওয়া সত্ত্বেও তাদের পারিশ্রমিক ওঁর থেকে বেশী ছিল। এর ফল হয়েছিল এই যে নিজের প্রাপ্য টাকার একটা প্রাইভেট হিসেব ওঁর মনের মধ্যে ছিল। সেই টাকা বানানোর ফন্দি উনি ভালো করেই জানতেন।
প্রচুর অর্থ উপার্জন করেও নন্দকিশোর খুব সাধারণ ভাবেই থাকতেন; জীবনযাত্রায় বাবুগিরির নাম গন্ধ ছিল না। কিন্তু প্রচুর অর্থ তিনি ব্যয় করতেন জর্মানি, আমেরিকা থেকে দামি যন্ত্র কেনায়। সেই যন্ত্র ভারতবর্ষের বড়ো বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়েও মিলতো না। নন্দকিশোরের বক্তব্য ছিল “ওদের দেশে বড় বড় যন্ত্র ব্যবহারের যে সুযোগ আছে আমাদের দেশে না থাকাতেই ছেলেরা টেক্সটবুকের শুকনো পাতা থেকে কেবল এঁটোকাঁটা হাতড়িয়ে বেড়ায়……… ছেলেদের জন্য বিজ্ঞানের বড়ো রাস্তাটা খুলে দিতে হবে বেশ চওড়া করে”
এক্ষেত্রে যা হয়, সহকর্মীদের নিশানা হয়ে উঠলেন নন্দকিশোর। আএ সেই বিপদের থেকে নন্দকিশোরকে রক্ষা করলেন বড়সাহেব। নন্দকিশোরের দক্ষতার উপর তাঁর ছিল প্রচুর শ্রদ্ধা আর রেলওয়ের কাজে মোটা মুঠোয় অপসারণদক্ষতার দৃষ্টান্তও তাঁর জানা ছিল। চাকরি ছাড়তে হল নন্দকিশোরকে। নন্দকিশোর সেই বড়সাহেবের আনুকূল্যেই রেল কোম্পানির পুরনো লোহালক্কড় সস্তা দামে কিনে কারখানা বসালেন। তখন য়ুয়োরোপের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বাজার সরগরম। সেই বাজারে নন্দকিশোরের ব্যবসায়বুদ্ধি আর কৌশলে তাঁর মুনাফার টাকার বান এলো।
একবার তিনি গেলেন পাঞ্জাবে তাঁর ব্যবসার তাগিদে। সেখানেই এক সঙ্গিনী জুটলো, বিশ বছরের পাঞ্জাবি যুবতী। সবাই ডাকতো সোহিনী নামে। পশ্চিমী ছাঁদের, সুকঠোর এবং সুন্দর তার চেহারা, জ্বলজ্বলে চোখ, ঠোঁটের হাসি যেন শান দেওয়া ছুরি। যে দশায় সোহিনী ছিল সেটা খুব নির্মল বা নিভৃত ছিল না। যদিও রবীন্দ্রনাথ তেমনটি লেখেন নি তবুও নন্দকিশোর যে সোহিনীর থেকে বয়সে অনেক বড় ছিলেন সেটা ধরে নেওয়া অযৌক্তিক হবে না।
পরিচয়ের প্রথম পর্বেই সোহিনীী অসঙ্কোচে নন্দকিশোরকে বলে “আমার জন্মস্থানে শয়তানের দৃষ্টি আছে …. জগতে সবচেয়ে বড়ো নাম হচ্ছে শয়তানের। তাকে যে নিন্দে করে করুক। কিন্তু সে খুব খাঁটি … তোমার মধ্যেও ঐ শয়তানের মন্তর আছে … তাই তোমারই হবে জিত। অনেক পুরুষকেই আমি ভুলিয়েছি কিন্তু আমার উপরেও টেক্কা দিতে পারে এমন পুরুষ আজ দেখলুম, আমাকে তুমি ছেড়ো না বাবু, তা হলে তুমি ঠকবে।”
“কী করতে হবে?”
নন্দকিশোরের প্রশ্নের উত্তরে সে জানায় সাত হাজার টাকা দিয়ে তার আইমার দেনা মেটাতে হবে যাতে তার বাড়িঘর বিক্রি না হয়ে যায়। নন্দকিশোর দিলেন সাত হাজার টাকা। বিনিময়ে সোহিনী নিজেকে জীবনের জন্য নন্দকিশোরকে সঁপে দেওয়ার অঙ্গীকার করলো। সময়টা, গল্পের কথানুযায়ী ধরে নেওয়া যেতে পারে ১৯১০ এর দশকের শেষ ভাগ। সোহিনী এলো নন্দকিশোরের জীবনে। তাদের পুরো সামাজিক প্রথামতো বিয়ে হয়েছিল কি না সেটা রবীন্দ্রনাথ পরিস্কার লেখেননি। লিখেছেন বিয়েটা হয়েছিল সহ্যমত, খুব বেশীমাত্রায় নয়। সে যাইহোক নন্দকিশোর উঠে পড়ে লাগলেন স্ত্রীকে নিজের বিদ্যের ধাঁচে গড়ে তুলতে।
প্রৌঢ় বয়সে নন্দকিশোর অপঘাতে মারা গেলে সোহিনী সমস্ত কারবার বন্ধ করে দেয়। নন্দকিশোরের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে অধিকার বসানোর জন্য তার আত্মীয়রা যথাসাধ্য করলো, আদালতে মামলাও ঠুকে দিল। কিন্তু সোহিনী ছিল বলিষ্ঠ চরিত্রের পাঞ্জাবি মহিলা, বাঙালি ঘরের অবলা বিধবা নয়। বিবাহোত্তর জীবনে তাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন নন্দকিশোর। অতএব সব মামলাতেই সোহিনীর জয় হ’ল। সেটা নিশ্চিত ক’রতে যেখানে প্রয়োজন অসংকোচ নৈপুণ্যে নারীর মোহজালও বিস্তার করলো। সেটাতে তার সংস্কার মানার কোন বালাই ছিল না।
নন্দকিশোর – সোহিনীর একটি কন্যা সন্তান ছিল। নাম নীলিমা। বড় হয়ে সেই মেয়ে নিজেই তার নামটিকে ছেঁটে করে নিল নীলা। নীলা ফুটফুটে গৌরবর্ণ, দেহে কাশ্মীরী শ্বেতপদ্মের আভা, চোখে নীলপদ্মের আভাস। চুলে চমক দেওয়া পিঙ্গল বর্ণ। অল্পবয়সেই বিয়ে করেছিল ধনী পরিবারের এক মাড়োয়ারি ছেলেকে, যারও বয়স ছিল অল্প। বিয়েটা হয়েছিল সিভিল মতে, সমাজের ওপারে। কিন্তু সেই দাম্পত্যের মেয়াদ বেশীদিন হয়নি। ছেলেটি টাইফয়েডে মারা যায়।
সোহিনী তার মেয়ের ছটফটানি দেখে, আর মনে পড়ে যায় তার নিজের প্রথম বয়সের অগ্নিচাঞ্চল্য। নীলাকে সংরক্ষিত রাখতে যা কিছু করা প্রয়োজন সবই করেছিল সোহিনী। কিন্তু না পারা গেল নীলাকে ঘরের মধ্যে নিয়ন্ত্রনে রাখা, না আটকানো গেল বাইরের ছেলেদের নীলাকে প্রেম নিবেদনের প্রচেষ্টা। নন্দকিশোর যাদের বৃত্তি দিয়েছিলেন সেই সব ভালো ভালো ছাত্রমহলে মেয়ের জন্য পাত্র সন্ধান করতে লাগলো সোহিনী। কিন্তু সবাই প্রায় আড়ে আড়ে তাকায় সোহিনীর টাকার থলির দিকে।
এবার সোহিনীর নজর এলো রেবতী ভট্টাচার্য। অল্প বয়সেই D. Sc করেছে। বিদেশে কিছু নামও হয়েছে। রেবতীকে ধরার জন্য সোহিনী যা করলো সেটাকে আজকের দিনের ম্যানেজমেন্ট শাস্ত্রে বলা হয় Strategic Planning. প্রথমেই সোহিনী বশ করলো রেবতীর অধ্যাপক মন্মথ চৌধুরীকে। তিনি প্রখর বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন, রসিক এবং পরোপকারী মানুষ। এঁর সঙ্গে সোহিনীর সম্পর্কটা রবীন্দ্রনাথ যেভাবে দেখিয়েছেন তা থেকে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে তার মধ্যে বন্ধুত্বের বাইরেও অন্য কিছু ছিল কারণ একাধিকবার সোহিনী অধ্যাপকের দুই গালে চুমো দিয়েছে, একবার গলা জড়িয়ে ধরেছে এবং একবার প্রণামও করেছে। অধ্যাপকের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে তার কথোপথন থেকে জানা যাবে সোহিনী কি ধাতু দিয়ে তৈরী ছিল।
নন্দকিশোর তাঁর ল্যাবরেটরিতে শিক্ষা দিতেন কলেজের ছাত্রদের। সোহিনীও সেখানে বসে যেতো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সোহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার চেষ্টাও ক’রত। তাতে সোহিনীর প্রশ্রয় ছিল কি না অথবা সেই মধুলোভীদের প্রচেষ্টার কোন ফল হ’ত কি না, সেই প্রসঙ্গে সোহিনীর কথায় “বলতে ইচ্ছে করে না, নোংরা আমি। দু’চার জনের সঙ্গে জানাশোনা হয়েছে যাদের কথা মনে পড়লে আজও মনের মধ্যে মুচড়িয়ে ধরে …. আমি তো গোড়াতেই নাম ডুবিয়েছি, সত্যি কথা বলতে আমার বাধে না … ছেলেবেলা থেকে ভালোমন্দ বোধ আমার স্পষ্ট ছিল না। কোন গুরু আমায় তা শিক্ষা দেন নি। তাই মন্দের মাঝে আমি ঝাঁপ দিয়েছি সহজে, পারও হয়ে গেছি সহজে। গায়ে আমার দাগ লেগেছে কিন্তু মনে ছাপ লাগে নি ….. তিনি যাবার পথে তাঁর চিতার আগুনে আমার আসক্তিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন, জমা পাপ একে একে জ্বলে যাচ্ছে। এই ল্যাবরেটরিতেই জ্বলছে সেই হোমের আগুন …… আমি সমাজের আইনকানুন ভাসিয়ে দিতে পারি দেহের টানে পড়ে, কিন্তু প্রাণ গেলেও বেইমানি করতে পারব না।”

প্রফেসর জানিয়েছিলেন সোহিনীকে যে রেবতী জন্মলগ্নেই মাতৃহারা হয় আর তাকে বড় করেন তার পিসি। সেই পিসিই ছিলেন রেবতীর জীবনের সবকিছুর নিয়ন্ত্রক।
এইবার দেখা যাক সোহিনীর রেবতীকে ধরার Strategic Planning – এর মূল অংশ। সোহিনী জানতে পারল রেবতী বোটানিকাল গার্ডেনের এক আকাশনিম বীথিকার তলায় প্রতি রবিবার আসে। সে ঠিক করে ওখানে সকন্যা রেবতীকে ধরবে। তার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতিও নিল সে। সাদা শাড়ি পরে মাথার কাঁচাপাকা চুলে পাউডার মেখে সোহিনী নিজের মুখের উপর একটি শুচি সাত্ত্বিক আভা মেজে তুলল। যাওয়ার আগে স্বামীর লাইব্রেরি ঘেঁটে কিছু উদ্ভিদের নাম আর তাদের লাটিন নাম জেনে নিল সময়মতো ব্যবহার করার জন্য। বড়বাজারের এক চেনা দোকানে ফরমাশ দিয়ে তৈরি করা অনেকরকম মিষ্টি নিল সঙ্গে। পরে সেগুলো নীলার ‘নিজের হাতে বানানো’ ব’লে চালাবে। তার রাঁধুনি বামুনকে সাজিয়ে নিল পূজারী বামুনের বেশে। আর নীলাকে সাজালো “তাকে পরিয়েছে নীলচে সবুজ বেনারসী শাড়ি, ভিতর থেকে দেখা যায় বসন্তী রঙের কাঁচুলি। কপালে তার কুঙ্কুমের ফোঁটা, সূক্ষ একটু কাজলের রেখা চোখে, কাঁধের কাছে ঝুলেপড়া গুচ্ছকরা খোঁপা, পায়ে কালো চামরার ‘পরে লাল মখমলের কাজ করা স্যান্ডেল।“
বোটানিকালে সোহিনী গিয়েছিল মোটরলঞ্চে। সেখানে পৌঁছে, পরিকল্পনা মাফিক নীলাকে লঞ্চে বসিয়ে রেখে, সোহিনী গেল রেবতী অভিমুখে, সঙ্গে সেই “পূজারি বামুন”। প্রথম সাক্ষাতেই সোহিনী, বয়সে অনেক ছোট রেবতীকে প্রণাম করে এই অজুহাতে যে সে বাহ্মণ আর সোহিনী ছত্রি। প্রাথমিক বাক্যালাপের পরে সোহিনী রেবতীকে আমন্ত্রণ জানায় তার ল্যাবরেটরিতে আর সেটা নিশ্চিত করতে সোহিনী খেলে তার তুরুপের তাস। সেই “পূজারি বামুন”কে পাঠায় মোটর লঞ্চ থেকে নীলাকে ডেকে আনতে। পরিকল্পিত ভাবেই নীলা উঠে আসে। হাতে তার ডালি আর সেই ডালিতে ফুল আর “তার হাতে তৈরী মিষ্টান্নর” সমাহার। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন “নদীর ঘাট থেকে আস্তে আস্তে দেখা দিল নীলা। রোদদুর পড়েছে তার কপালে তার চুলে, বেনারসী শাড়ির উপরে জরির রশ্মি ঝলমল্ করে উঠছে। রেবতীর দৃষ্টি এক মুহূর্তের মধ্যে ওকে ব্যাপ্ত করে দেখে নিলে। চোখ নামিয়ে নিল পরক্ষণেই।“
এরপর নীলাকে দিয়ে রেবতীকে প্রণাম করানোর কৌশলে রেবতী যেটুকু স্পর্শ পেলো নীলার তাতে তার সমস্ত শরীর শিউরে উঠলো। এবার সোহিনীর অনুরোধ রেবতীকে “নীলার নিজের হাতে তৈরী মিষ্টি” একটু মুখে দিতে। কিন্তু রেবতীর ইচ্ছা হ’ল ওই ফুল, মিষ্টি সব তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার। মা মেয়ে যখন সে সব গোছগাছে ব্যস্ত, রেবতীর দায় হ’ল নীলার দিক থেকে চোখ ফেরানোর। এখানে রবীন্দ্রনাথ নীলাকে নিয়ে লিখছেন “মাঝে মাঝে নীলার মুখের দিকে তাকিয়ে নিচ্ছিল। এক দিকে সেই মুখের সীমানা দিয়েছে চুনিমুক্তোপান্নার – মিশোলকরা একহারা হার জড়ানো চুলের ইন্দ্রধনু, আর – এক দিকে বসন্তীরঙা কাঁচুলির উচ্ছ্রিত রাঙা পাড়টি।“
নীলার প্রতি রেবতীর এহেন মনযোগ সোহিনীর নজর এড়াল না এবং সেটা যে তার ভালো লাগল না, তার কারণটা গল্পের পরের অংশ থেকে জানা যাবে। অবশ্যই রেবতী সাগ্রহে রাজি হ’ল পরের দিনই সোহিনীর বাড়ি যেতে – ল্যাবরেটরি দেখার জন্য। এখানে এইটুকু নিশ্চয় বলা যায়, আজকের দিনের ভাষায় সোহিনীর “রেবতী পাকড়াও” মিশন অ্যাকম্প্লিশড্ হয়েছিল।
রেবতী তার বাড়িতে আসার আগে সোহিনী দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়। একটি হ’ল ল্যাবরেটরির স্বার্থে নীলার সঙ্গে রেবতীর বিয়ে না দেওয়ার। এর প্রথম কারণ ছিল এই যে, নিজের অতীতের দিকে তাকিয়েই, সে তার মেয়েকে বিশ্বাস ক’রতো না। সোহিনীর কথায় “ও ভাঙন ধরানো মেয়ে। ওর হাতে যা পড়বে তা আস্ত থাকবে না …..পুরুষের খোরাকে আমিষ পর্যন্ত ভালোই চলে কিন্তু মদ ধরালেই সর্বনাশ আমার মেয়েটি মদের পাত্র কানায় কানায় ভরা।“
আর দ্বিতীয় কারণ ছিল প্রথমবার দেখেই সোহিনী বুঝে গিয়েছিল রেবতী বিশেষভাবে দুর্বল চরিত্রের মানুষ। এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সোহিনীর বক্তব্যে লিখছেন “রেবতীর মুখের বেড়টা মেয়েলি ধাঁচের মোলায়েম। রেবতীর সম্বন্ধে ও যত খবর জোগার করেছে তার মধ্যে ও বিশেষ ভাবে লক্ষ করেছে একটা কথা। ছেলেবেলাকার বন্ধুদের ওর উপরে কান্নাকাটি জড়ানো সেন্টিমেন্টাল ভালোবাসা। ওর মুখে যে একটা দুর্বল মাধুর্য ছিল তাতে পুরুষ বালকদের মনে মোহ আনতে পারতো”

এইসব কারণেই প্রথম দর্শনেই নীলাকে দেখে রেবতীর অমন মোহিত হয়ে যাওয়াটা সোহিনীর ভালো লাগেনি। সোহিনীর দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত ছিল একটি পাবলিক ট্রাস্ট গঠন করে, তার ল্যাবরেটরি সেই ট্রাস্টকে দান করার আর রেবতীকে করার প্রেসিডেন্ট সেই ট্রাস্ট সম্পত্তির। এই সিদ্ধান্তেরও কারণ ছিল মেয়ের হাত থেকে ল্যাবরেটরিকে বাঁচানো। রেবতী এলো আর শুরু ক’রল কাজ ল্যাবরেটরিতে আর সোহিনী নীলাকে জানিয়ে দিল রেবতীর সঙ্গে তার বিয়ে সে হ’তে দেবে না।
নীলা: উনি যদি নিজেই যদি হ্যাংলাপনা করেন?
সোহিনী: তা হলে এ পাড়া তাকে ছাড়তে হবে – তোর অন্নে তাকে মানুষ করিস, তোর বাপের তহবিল থেকে এক কড়িও সে পাবে না।
ল্যাবরেটরিতে রেবতীর কাজ ক’রতে থাকল আর প্রফেসর চৌধুরীর মতে সেই কাজ বেশ ভালভাবেই এগোতে থাকলো। তবুও সোহিনীর চিন্তা যায় না। “চৌধুরীমশায় আর সবই চলছে ভালো কেবল আমার মেয়ের ভাবনায় সুস্থির হতে পারছি নে। ও যে কোন্ দিকে তাক করতে শুরু করেছে বুঝতে পারছি নে।“
এখানে বলে রাখা যেতে পারে যে সোহিনীর আশঙ্কা অমূলক ছিল না। এমত অবস্থায় সোহিনীকে যেতে হ’ল আম্বালা, অসুস্থ আইমাকে দেখতে। খবর এসেছিল নীলা সম্পত্তিতে তার অধিকারের দাবীতে আইন আদালত করার চেষ্টায় আছে এবং বঙ্কুবাবু তার সলিসিটর। আম্বালা যাওয়ার আগে সোহিনী নীলাকে সাবধান করে গেলো “তোমার বঙ্কুবাবুকে আমি সিধে করে দেব যদি আমার সীমানায় তিনি পা বাড়ান। আইনে না পারি বে আইনে।“ তারপরে নিজের কোমরবন্ধ থেকে ছুরি বের করে বলে “এ ছুরি না চেনে আমার মেয়েকে, না চেনে আমার মেয়ের সলিসিটরকে। এর স্মৃতি রইল তোমার জিম্মায়। ফিরে এসে যদি হিসেব নেবার সময় হয় তো হিসেব নেব।“
সোহিনী আম্বালা যাওয়ার আগেই প্রফেসরকে যেতে হয়েছিল গুজরানওয়ালা কিছুদিনের জন্য। ফলে “দুর্গ” রইল অরক্ষিত। মা’র সব পরিকল্পনা বানচাল করে দেওয়ার এই সুবর্ণ সুযোগ ছাড়ল না নীলা। প্রথমেই সিডিউস্ করে রেবতীকে। একদিন রাত দুটোর সময় রেবতী কাজ করছিল ল্যাবরেটরিতে। এমন সময় দেওয়ালে পড়ল ছায়া। রেবতী চেয়ে দেখে ঘরের মধ্যে এসেছে নীলা। রাত কাপড় পরা, পাতলা সিল্কের শেমিজ। নীলা এসে ওর কোলের উপর বসে গলা জড়িয়ে ধরল। পাঞ্জাবি প্রহরী এসে নীলাকে ল্যাবরেটরি থেকে বার করে দেওয়ার আগেই সে রেবতীকে দিয়ে বলিয়ে নিল যে সে নীলাকে ভালোবাসে। চলে যাবার সময় রাত কাপড়ের ভিতর থেকে নীলার নিঁখুত দেহের গঠন ভাস্করের মূর্তির মতো অপরূপ হয়ে ফুটে উঠল, রেবতী মুগ্ধ চোখে না দেখে থাকতে পারল না।
নীলা বুঝে গিয়েছিল যে রেবতীকে বিয়ে করা নিরাপদ, বিবাহোত্তর উচ্ছৃঙ্খলতায় বাধা দেবার জোর তার নেই। শুধু তাই নয়। ল্যাবরেটরির সঙ্গে যে লোভের বিষয় জড়ানো আছে তার পরিমান প্রভূত। অতএব মায়ের অমত হবে জেনেই ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে নোটিসও দেওয়া হ’য়ে গেল।
রেবতীর আসল কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। ছিন্ন হয়ে গেছে সমস্ত চিন্তাসূত্র। মন কেবলই অপেক্ষা ক’রছে নীলা কখন আসবে, হঠাৎ পিছন থেকে ধরবে ওর চোখ টিপে। চৌকির হাতার উপর বসে বাঁ হাতে ধরবে ওর গলা জড়িয়ে।
একদিন সান্ধ্যভোজ এক নামজাদা রেস্টোরাঁতে। নিমন্ত্রণকর্তা ডঃ রেবতী ভট্টাচার্য। উপস্থিত নীলা ও তার পুরুষ এবং মহিলা বন্ধুরা এবং তিন আইনজীবি। প্রায় পঁয়ষট্টি জন। চলছে পানভোজন, চলছে চারশ টাকা পারিশ্রমিক দিয়ে আনা সিনেমার বিখ্যাত নটীর গান। কয়েকদিন আগে সোহিনীর কাছ থেকে ল্যাবরেটরির খরচের নাম করে যে অর্থ রেবতী আনিয়েছিল সেটা দিয়েই মেটানো হয়েছে সান্ধ্যভোজের খরচ। এমন সময় সেখানে হাজির হয় সোহিনী। রেবতীকে পরিষ্কার বলে দিল সেই রাতেই ল্যাবরেটরির ফর্দ অনুসারে সব জিনিষপত্র মিলিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ রেবতীকে বরখাস্ত করা হ’ল। আর নীলাকেও জানিয়ে দিল সে নন্দকিশোর মল্লিকের মেয়ে নয় আর সেটা তিনি তাঁর রেজিস্ট্রিকৃত দলিলে খোলসা করে গেছেন। সুতরাং কার সম্পত্তির শেয়ার পাওয়ার চেষ্টা করছে নীলা?
এই পরিস্থিতিতেও হয়তো রেবতী আর নীলার বিয়েটা হ’ত কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাঁচিয়ে দিলেন রেবতীকে। তিনি রেবতীর পিসিমাকে এনে ফেললেন ঘটনা স্থলে। পিসিমা ডাক দিলেন “রেবি চলে আয়।” সুড় সুড় ক’রে রেবতী পিসিমার পিছন পিছন চলে গেলো, একবার ফিরেও তাকাল না। রবীন্দ্রনাথ একবার সাহিত্যের প্রকৃত ধর্ম নিয়ে বলেছিলেন “সাহিত্যবিচার স্মৃতিশাস্ত্র বিচারের অঙ্গ নয়। আর নায়িকা চরিত্রে কতটা হিন্দু – রমণীত্ব রয়েছে তার হিসাব – নিকাশ করে উপন্যাস লেখকের দায় লেখকের নয়।“
এমনটি বললেও তাঁর নারীভাবনায় রক্ষণশীলতার প্রভাব এতটাই ছিল যে তাঁর সাহিত্যে স্ত্রীচরিত্র রচনা কালে তিনি স্ববিরোধিতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি। “ঘরেবাইরে”-এর “বিমলা” তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। “ল্যাবরেটরি” গল্পের “সোহিনী” রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। সোহিনীর ব্যক্তি – চরিত্রের বৈশিষ্ট তার বলিষ্ঠ নৈতিকতা, তার কর্মদক্ষতা, আদর্শগত নিষ্ঠা, তার সতীত্ব নয়। তার সেই বলিষ্ঠতার জন্যই সোহিনী অনায়াসে বলতে পেরেছে সে সমাজের আইনকানুন ভাসিয়ে দিতে পারে দেহের টানে পড়ে কিন্তু প্রাণ গেলেও বেইমানি ক’রতে পারবে না।
যে বেইমানির কথা সোহিনী বলেছে সেটা ওই ল্যাবরেটরির সঙ্গে সম্পর্কিত, যেটি তৈরী করেছিলেন তার স্বামী, যে ল্যাবরেটরিকে সোহিনী ম’নে করতো মন্দির আর তার স্বামীকে মনে ক’রত এক মহাপুরুষ যিনি তাকে উদ্ধার করেছিলেন। সোহিনীর কথায়– “অনেক নিচে নামতে হয়েছিল। শেষকালে তুলে বসাতে পেরেছেন ….. বিদ্যার পথে মানুষকে উদ্ধার করার দীক্ষা তিনি আমাকে দিয়ে গেছেন।“
অনায়াসে সোহিনী স্বীকার করেছে তার স্বামীর কিছু ছাত্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়েছিল এবং সেইসব সম্পর্কের মধ্যে শরীরও ছিল। কিন্তু যেই সে বুঝতে পারল তাদের নজর তার টাকার থলির দিকে, তাদের রাস্তা দেখিয়ে দিতে সোহিনীর কোন দ্বিধাই হ’ল না। যে রেবতীকে সোহিনী রীতিমত ফাঁদ পেতে ধরেছিল তার ল্যাবরেটরির স্বার্থে, সেই রেবতীকে তার বেইমানির জন্য এক মুহূর্তে ছেঁটে ফেলতে দুবার ভাবল না।
সোহিনীকে তার স্বামী যে কাজের ভার দিয়ে গিয়েছিলেন তার প্রতি দায়বদ্ধতার চূড়ান্ত প্রকাশ হ’ল যখন সর্বসমক্ষে নীলাকে জানিয়ে দিল সে নন্দকিশোর মল্লিকের সন্তান নয়। এর অর্থ, যখন নন্দকিশোরের সঙ্গে তার বিয়ে হয় তখন সোহিনী অন্তঃসত্ত্বা ছিল। এমনভাবেই প্রমাণিত হয়েছে যে সোহিনী তার শারীরিক প্রয়োজনকে অবজ্ঞা করেনি, পাশ কাটিয়ে যায় নি কিন্তু তার মনকে সে কলুষিত হ’তে দেয়নি কখনোই। সুতরাং বলা যেতেই পারে সাদা আর কালো মিলিয়ে সোহিনী ছিল এক সম্পূর্ণ নারী। একমাত্র সোহিনী চরিত্রের সৃষ্টিতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্ববিরোধিতা কাটিয়ে উঠে “নারীত্ব” না “সতীত্ব” বিতর্কে নারীত্বকেই জয়ী করেছেন। তাই সোহিনী রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট নারী চরিত্রের মধ্যে অদ্বিতীয়া। গল্পটির নাম “ল্যাবরেটরি” না হয়ে “সোহিনী”ও হ’তে পারতো।
** স্বীকৃতি
১. রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী), চতুর্থ খণ্ড
২. রবীন্দ্র –রচনাবলী (বিশ্বভারতী), ত্রয়োদশ খণ্ড
৩. “ঘরে-বাইরে উপন্যাসে নারীর ব্যক্তি-স্বীকৃতি ও বিতর্কিত রবীন্দ্র-মানস”: আবেদা আফরোজা – বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, সাঁইত্রিশতম খণ্ড, পৌষ ১৪২৬/ডিসেম্বর ২০১৯
********
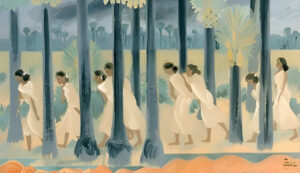 New Clouds, 1937 by Nandalal Bose
New Clouds, 1937 by Nandalal Bose

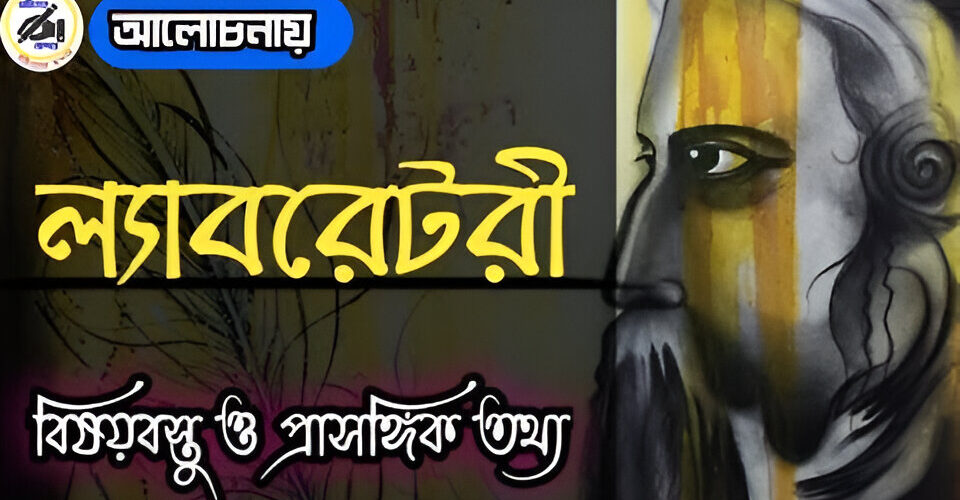
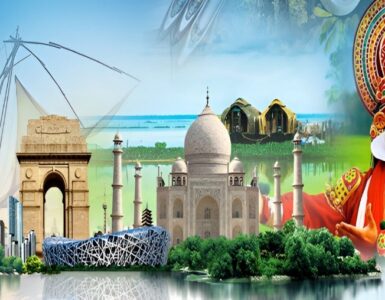













Add comment