রবীন্দ্রনাথের নারীচরিত্র
দেবপ্রসাদ দে (মামু), ১৯৭৭ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
বাংলা সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন অবিস্মরণীয় সকল নারীচরিত্র। কখনো শিশু বা কিশোরী, কখনো যুবতী, কখনো বা প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা। পোস্টমাস্টারের গ্রাম্যবালিকা রতন আর কাবুলিওয়ালার শহরের ধনীকন্যা মিনি, দুটি শিশুই বিপরীত চরিত্রের। আর বিসর্জন নাটকে একটি শিশুর প্রশ্ন ‘এত রক্ত কেন?’ এখানে কেউ শৈশবেই মাতৃরূপা, কেউ উচ্ছল, কেউ চিন্তাশীল।
স্ত্রীর পত্রে’র মৃণাল, ‘দেনাপাওনা’র নিরুপমা বিদ্রোহী। সমাজের তথাকথিত বিবাহরীতি, সংসার ধর্ম, পণপ্রথা, শ্বশুরবাড়ির নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী রূপ। নতুন বৌ মৃণাল সম্পন্ন পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে চললেন কাশী, উনি মাখন বড়ালের গলিতে আর ফিরে আসবেন না। ‘দেনাপাওনা’র নিরুপমা যৌতুকের দাবী অস্বীকার করে নিজের বিবাহে রাজি হলেন না। ‘নষ্টনীড়ে’র চারুলতা দুঃখীনী গৃহবন্দী। জীবিত ও মৃত গল্পে কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিলো যে সে মরে নাই।
বৈচিত্রের দিক থেকেও রবীন্দ্রসাহিত্যের নারীরা কেউ গ্রাম্য বা শহরের বালিকা, কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র, কেউ কৃষক গৃহবধূ, বিধবা মুসলমান বৃদ্ধা, মোগল রাজকুমারী, ব্রাহ্ম পরিবারের তরুণী, হিন্দু কূলবধূ, স্বদেশী বিপ্লবী, সংস্কারমুক্ত বিজ্ঞানমনস্কা, স্বাধীন চাকরিজীবী, সকলেই তাঁর সাহিত্যে স্থান পেয়েছে।
রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট পোস্টমাস্টারের গ্রাম্যবালিকা রতন আর কাবুলিওয়ালার শহরের ধনীকন্যা দুটি ভিন্ন রূপ। অন্যদিকে ‘রাজর্ষি’ উপন্যাসে শিশুকন্যা হাসি রাজাকে প্রশ্ন করে “মন্দিরের সোপানে এত রক্ত কেন?” এঁরা মাতৃরূপা, উচ্ছল, আবার কেউ চিন্তাশীল। প্রতিটি চরিত্র আমাদের নিজেদের ঘরোয়া চরিত্র। আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনে আমরা এঁদের সান্নিধ্যে আসি।
বৈচিত্রের মাঝে পাই ব্রজবুলিতে রচিত ভানুসিংহের পদাবলী। কবির নিজের কথায় “একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলাদিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা শ্লেট লইয়া লিখিলাম ‘গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে’।
শুনলো শুনলো বালিকা, অথবা গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে।

চন্ডালিকায় প্রভু বুদ্ধের শিষ্য আনন্দ গ্রীষ্মের প্রখর দহনে তৃষ্ণা বোধ করেন। তখন চণ্ডালকন্যা, নাম প্রকৃতি, কুয়ো থেকে জল তুলছেন। জল চাইলেন আনন্দ। কিন্তু চণ্ডালকন্যা সংকোচভরে অতিথিকে বলেন যে, সে চণ্ডালকন্যা আর তার কুয়োর জল অশুচি। আনন্দ বলেন যে, তিনি যে মানুষ, প্রকৃতিও সেই মানুষ। সব জলই তৃষ্ণার্তর তৃষ্ণা নিবারণ করে। আনন্দের কথায় ও রূপে মুগ্ধ হল প্রকৃতি। জল গ্রহণ করে এই বৌদ্ধ তার জীবনের সমস্ত অপমান ধুয়ে দিয়ে গেলেন। মায়ের সাহায্যে আনন্দকে পেতে চাইল প্রকৃতি। জাদুশক্তির প্রভাবে মা আনন্দকে টেনে আনেন। সে প্রকৃতিকে তার মায়াদর্পণে দেখতে বলে আনন্দকে। কিন্তু আনন্দের ক্লান্ত, ম্লান রূপ সহ্য করতে পারে না প্রকৃতি। সে ভেঙে ফেলে তার মায়ের জাদুমন্ত্রের সমস্ত উপকরণ। তারপর প্রকৃতি ও তার মা দু’জনেই ক্ষমাপ্রার্থনা করে আনন্দের কাছে। তাদের এই নতুন উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই শেষ হয় রবীন্দ্রনাথের ‘চণ্ডালিকা’র কাহিনী।
চতুর্দশপদী বড় কবিতায় পাই দৃঢ়চরিত্রের গান্ধারীকে। পাই কুন্তীকে, যিনি লোকলজ্জায় প্রথম সন্তানকে ত্যাগ করেন, কিন্তু নিজের দুই সন্তানের যুদ্ধের আগে বড় সন্তানের কাছে নিজের অন্য সন্তানের প্রাণ ভিক্ষা করেন। বিদায় অভিশাপে সহস্র বৎসরের গুরুগৃহে সাধনার পরে দেবতাদের কুলগুরু বৃহস্পতিপুত্র কচ যখন অসুরকুলগুরু শুক্রাচার্যর কন্যা দেবযানীকে ত্যাগ করার মনস্থ করে, তখন দেবযানী বলে তুমি যে বিদ্যাশিক্ষা লাভ করলে “তুমি শুধু তার ভারবাহী হয়ে রবে। শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।“
হে ব্রাহ্মণ। তুমি চলে ষাবে স্বর্গলোকে
সগৌরবে, আপনার কর্তব্যপুলকে
সর্ব দুঃখশোক করি দূরপরাহত;
আমার কী আছে কাজ, কী আমার ব্রত।
আমার এ প্রতিহত নিষ্ফল জীবনে
কী রহিল, কিসের গৌরব? এই বনে
বসে রব নতশিরে নিঃসঙ্গ একাকী
লক্ষ্যহীনা। যে দিকেই ফিরাইব আঁখি
সহস্র স্মৃতির কাঁটা বিঁধিবে নিষ্ঠুর;
লুকায়ে বক্ষের তলে লজ্জা অতি ক্রূর
বারম্বার করিবে দংশন। ধিক্ ধিক্,
কোথা হতে এলে তুমি, নির্মম পথিক,
বসি মোর জীবনের বনচ্ছায়াতলে
দণ্ড দুই অবসর কাটাবার ছলে
জীবনের সুখগুলি ফুলের মতন
ছিন্ন করে নিয়ে, মালা করেছ গ্রন্থন
একখানি সূত্র দিয়ে। যাবার বেলায়
সে মালা নিলে না গলে, পরম হেলায়
সেই সূক্ষ্ম সূত্রখানি দুই ভাগ করে
ছিঁড়ে দিয়ে গেলে। লুটাইল ধূলি-’পরে
এ প্রাণের সমস্ত মহিমা। তোমা-’পরে
এই মোর অভিশাপ— যে বিদ্যার তরে
মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ— তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ;
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।
রবীন্দ্রনাথের অসামান্য কল্পনাশক্তির পরিচয় পাই ক্ষুধিত পাষানের অশরীরী চরিত্রের অপূর্ব বর্ননায়। সেখানে মোহময়ী নারীদের পথচলার তিনি বর্ননা দিয়েছেন যে তাঁরা দেহহীন দ্রুতপদে শব্দহীন উচ্চকলহাস্যে ছুটিয়া গেলো। আর সেই কাল্পনিক অপরূপাদের তিনি বর্ননা দিয়েছেন বেদনাবাসনাময়ী মজ্জমানা কামনাসুন্দরী।
এরূপ ভাষা, কাহিনী ও চরিত্রের বৈচিত্র পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় বিরল।
রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে নারীরূপে কল্পনা করেছেন। বিভিন্ন সূত্রে পাই যে কবির প্রথম স্বাধীন রচনা ‘নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়’। কবির নিজের কথায় শুক্লপক্ষের কত নিস্তব্ধ রাত্রে আমি শাহিবাগ প্রাসাদের সেই সাবরমতী নদীর দিকের প্রকান্ড ছাতটাতে একলা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। এরূপ একটা রাত্রে আমি যেমন খুশী ভাঙ্গা ছন্দে একটা গান তৈরি করিয়াছিলাম নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়’। ‘বলি ও আমার গোলাপবালা’ এমনি আর এক রাত্রে লিখিয়া বেহাগ সুরে বসাইয়া গুনগুন করিয়া গাহিয়া বেড়াইয়াছিলাম।
বিদেশিনীদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কাব্যিক দুর্বলতা আমরা দেখি তাঁর গানে। কথিত আছে, আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী তিনি আর্জেন্টাইন কবি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে অনেক পরে উৎসর্গ করেন, যখন উনার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা।
মণিপুর রাজকুলের কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে রাজা পুত্ররূপেই পালন করলেন। শেখালেন ধনুর্বিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা, রাজনীতি। অর্জুন দ্বাদশবর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্যব্রত পালনে ভ্রমণ করতে করতে এসেছে মণিপুরে। দেখা মেলে পুরুষবেশী চিত্রাঙ্গদার। চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে হৃদয় নিবেদন করলে অর্জুন তাঁর ব্রহ্মচর্য ব্রতের কারণে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। নিদারুণ দুঃখে চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের হৃদয় হরণ করার জন্য মদনের আরাধনা করলে মদন মাত্র একটি বছরের জন্য চিত্রাঙ্গদাকে অপরূপা লাবণ্যময়ী রূপ দান করলেন। এবার সুরূপা চিত্রাঙ্গদাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে অর্জুন তাঁকে প্রেম নিবেদন করে। অর্জুনকে সতর্ক করে সে বলে
কিন্তু মনে রেখো,
কিংশুকদলের প্রান্তে এই-যে দুলিছে
একটু শিশির— তুমি যারে করিছ কামনা
সে এমনি শিশিরের কণা
নিমেষের সোহাগিনী॥
মদনের বরে চিত্রাঙ্গদা একটি বছরের জন্য অসামান্য রূপলাবণ্যের অধিকারী হন। নিজেকে কুরূপা থেকে সুরূপাতে, অর্থাৎ নিজেকে সুন্দর নারীতে রূপান্তরিত করেন। কালেকালে অর্জুন চিত্রাঙ্গদার যথার্থ পরিচয় লাভ করে। চিত্রাঙ্গদা ফিরে যায় মদনের কাছে। অনুরোধ করে দেবতা যেন বর ফিরিয়ে নেয়। মদনও ইচ্ছা পূরণ করলেন তাঁর। সুরূপা-ছদ্মবেশী চিত্রাঙ্গদা নিজের প্রকৃত রূপের দৈন্যের কথা উল্লেখ করেন। “ক্ষত্রিয়বাহুর ভীষণ শোভা” সেই চিত্রাঙ্গদাকে দেখে মুগ্ধ হয় অর্জুন। চিত্রাঙ্গদা উপলব্ধি করে, বাইরের যে রূপ-সৌন্দর্যের সন্ধান সে করেছিল, সেটা ভুল, ক্ষণস্থায়ী। অন্তরের সৌন্দর্য, আত্মবোধই নারীর মর্যাদা ও সম্মানের প্রধান বিষয়। ‘নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী’। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, বাইরের রূপের ভুল নয়, আপন অন্তরের ব্যক্তিত্ব আর সৌন্দর্যবোধের উপলব্ধি।
চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে বলে
আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী।
নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।
পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে সে নহি নহি।
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সঙ্কটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।
এইরূপে অর্জুনও ধন্য হলেন চিত্রাঙ্গদাকে পেয়ে।

শ্যামা নৃত্যনাট্যটি শুভ অশুভের দ্বন্দ্ব। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন উত্তরণের পথেই মঙ্গল। রাজনর্তকী শ্যামা যুবক বজ্রসেনের শরীরী সৌন্দর্যে কামমোহিত, প্রেম কামনায় উদ্বেল, পাপ-পুণ্যের বোধরহিত। বিপরীতে যুবক উত্তীয়ের প্রেমনিবেদন শ্যামার কাছে মূল্যহীন। তাই বজ্রসেনকে বাঁচানোর মরিয়া চেষ্টায় সে বলি দেয় উত্তীয়কে। এই অপরাধবোধই তার মনকে পীড়ন করেছিল, এবং অবশেষে সে বজ্রসেনের কাছে এই কাহিনী স্বীকার করে। বজ্রসেনও শ্যামার প্রেমে মুগ্ধ, কিন্তু পাপ-পুণ্যের বিবেচনার কঠিনহৃদয়। শ্যামাকে সে ত্যাগ করে কিন্তু তাকে ভুলতে পারে না। কামনার লালসায় জর্জরিত শ্যামা প্রেমিক বজ্রসেনের প্রত্যাখ্যানে বিধ্বস্ত হলেও পরিণামে প্রেমেরই জয় ঘোষিত হয়েছে।
শৈশবেই রবীন্দ্রনাথ ভারতের সনাতন নারীধর্মের চেতনায় লেখেন জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ। ১৮৭৫ সালে ১৪ বছর বয়সে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক-এর জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গানটি রচনা করেছিলেন। রচনা প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন:
রাজপুত মহিলাদের চিতাপ্রবেশের যে একটা দৃশ্য আছে, তাহাতে পূর্ব্বে আমি গদ্যে একটা বক্তৃতা রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরে পড়াশুনা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। গদ্য-রচনাটি এখানে একেবারেই খাপ খায় নাই বুঝিয়া, কিশোর রবি একেবারে আমাদের ঘরে আসিয়া হাজির। তিনি বলিলেন, এখানে পদ্যরচনা ছাড়া কিছুই জোর বাঁধিতে পারে না। আমি সময়াভাবের আপত্তি উত্থাপন করিলে, রবীন্দ্রনাথ সেই বক্তৃতার পরিবর্তে একটা গান রচনা করিয়া দিবার ভার লইলেন, এবং তখনই খুব অল্পকালের মধ্যেই “জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ” এই গানটি রচনা করিয়া আনিয়া, আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন।
উল্লেখ্য, সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক-এ নায়িকা সরোজিনীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সেকালের বিখ্যাত মঞ্চাভিনেত্রী নটী বিনোদিনী। ১৮৭৬ সালের ৩১ জানুয়ারি সরস্বতী পূজার দিন রবীন্দ্রনাথ নিজে এই কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান।
জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরান সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা।
শোন্ রে যবন, শোন্ রে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে
সাক্ষী র’লেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে।।
দেখ্ রে জগৎ, মেলিয়ে নয়ন,
দেখ রে চন্দ্রমা, দেখ রে গগন,
স্বর্গ হতে সব দেখো দেবগণ
জ্বলদ্-অক্ষরে রাখো গো লিখে।
স্পর্ধিত যবন, তোরাও দেখ রে,
সতীত্ব রতন করিতে রক্ষণ
রাজপুত সতী আজিকে কেমন
সঁপিছে পরান অনলশিখে।।

সে আনিয়া দেয় চিত্তে / কলনৃত্যে / দুস্তর প্রস্তর ঠেলা ফেনোচ্ছল আনন্দজাহ্নবী / বীণার তন্ত্রের মতো গতি তার সংগীতস্পন্দিনী / নাম কি নন্দিনী।
রবীন্দ্রনাথ ‘প্রবাসী’ পত্রিকার ১৩৩২ বৈশাখ সংখ্যায় লিখেছিলেন ‘রক্তকরবীর নন্দিনী একটি মানবীর ছবি। চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ।’
মাটির অতলে যে খনিজ মহাধন খোঁজা হয় নন্দিনী সেখানকার নয়; মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের বিকাশ, রূপের মৃত্যু, প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের সেই সহজ সৌন্দর্যের প্রতীক, যে সহজতার অনুশীলন সুস্থমনে জীবনধারনের জন্যে। সে কথা বুঝেছিল রাজা। নিজের শক্তির অহংকারে রাজা নিজেকেই বন্দি করেছে। তার সে ‘বন্দিত্ব’ থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখাতে পেরেছে শুধু নন্দিনী।




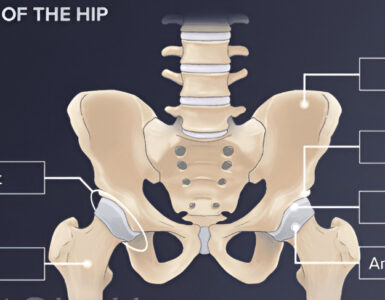











[…] কুমার বসাক, ১৯৭২ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং রবীন্দ্রনাথের নারীচরিত্র দেবপ্রসাদ দে (মামু), ১৯৭৭ সিভিল […]
বাহ্, সুন্দর লেখা। অনেকগুলি রবীন্দ্রনাথের লেখার উল্লেখ আছে এবং তারসাথে তার বিশ্লেষণও আছে। ভবিষ্যৎ এ আরো এইরকম লেখা আশা করবো। ❤
খুব সুন্দর লেখা। রবিঠাকুরের নারী চরিত্র ভাবনা নিয়ে লেখা আমাকে সমৃদ্ধ করলো।