সত্যজিৎ রায়ের জীবনে ও চলচ্চিত্রে নারী ।
প্রদীপ ভৌমিক, ১৯৭৪ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্র নির্মান করতেন মানবিকতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। নবজাগরনের যুগ থেকেই রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য মনীষিদের শিক্ষা বাঙ্গালীসমাজকে আধুনিক চিন্তাভাবনা ও নারীজাতির প্রতি সন্মানবোধ জাগ্রত করেছিল। বাংলার সমাজজীবন, সাহিত্য ও চলচ্চিত্র প্রভাবিতও হয়েছিল। সত্যজিৎ রায় নারীজীবনের গভীরতা প্রেম সুখদুঃখের নানান দিক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

পত্নী বিজয়া রায়ের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়।
ব্যক্তিগত জীবনে মা সুপ্রভা রায় ও স্ত্রী বিজয়া রায় তাঁর প্রতিভার উন্মেষণে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। সুপ্রভা রায় ছিলেন ব্যক্তিত্বপূর্ন স্বাধীনচেতা মহিলা। মাত্র দুবছর বয়সে সত্যজিৎ তাঁর পিতা সুকুমার রায়কে হারান এবং পারিবারিক প্রেস বন্ধ হয়ে যায়। স্বামীর মৃত্যুর পর অন্য কারোর উপর বোঝা না হয়ে তিনি নিজেই শিশুপুত্রের শিক্ষার দায়িত্ব নেন। শিশু সত্যজিৎকে নিয়ে দাদার বাড়িতে উঠে এলেন। হাতের নানারকম কাজে তিনি পারদর্শী ছিলেন, চাকরি নিলেন লেডি অবলা বসুর একটি হস্তশিল্প সংস্থায়। সূচিশিল্পে ও কাশ্মিরী চাদর শিল্পে তাঁর বেশ নাম ছিল। অন্যদিকে ভাল রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন। রন্ধনশিল্পেও নাম ডাক ছিল। ১৯৩০/৪০ দশকে দক্ষিন থেকে উত্তর কলকাতায় রোজ বাসে করে চাকরি করতে যেতেন।
সত্যজিৎ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিএ পাশ করে কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে এম এ পড়তে চাইলেন। ইচ্ছে কলকাতার বুদ্ধিজীবী মানুষদের সান্নিধ্য পাওয়া, চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনা -গবেষনা করা, ইত্যাদি। আরো একটি কারন ছিল প্রেমিকা বিজয়া রায়ের সান্নিধ্য বজায় রাখা। দুইজনেরই পাশ্চাত্য ক্লাসিক্যাল সংগীতের বিশেষ অনুরাগ ছিল। বিজয়া রায় বিয়ের আগে বোম্বেতে দুই তিনটি সিনেমা করেছিলেন। গানের গলা ভাল ছিল। গান শিখেছিলেন। রবীন্দ্র সংগীতের রেকর্ড করেছিলেন। দুইজনে পরস্পরের আত্মীয় ছিলেন, তাই উনাদের প্রেম অনেকদিন গোপন রাখা হয়েছিল।
মা সুপ্রভা দেবীর ইচ্ছায় সত্যজিৎ শান্তিনিকেতনে ভর্তি হলেন। কলাভবনে উনি ১৮ মাস ছিলেন, সেখানে তিনি শিক্ষক নন্দলাল বসু ও বিনোদ বিহারী মুখার্জীর সংস্পর্শে আসেন। সেখানেই তাঁর আঁকার ও দেখার অন্তর্দৃষ্টি তৈরি হয়। পরবর্তিকালে পত্নী বিজয়া রায় চলচ্চিত্রের বিভিন্ন কাজে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। পথের পাঁচালি’র শুটিং যখন অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে যায়, বিজয়া রায় তাঁর মাসী বাসন্তী দেবীকে (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পত্নী) দিয়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়কে তদ্বির করিয়েছিলেন। সুপ্রভা দেবী নিজে বাসন্তী দেবীর সঙ্গে দেখা করেন।
চারুলতা সিনেমায় দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত ছিল ‘আমি চিনিগো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনি’ এবং ‘ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে’। প্রথম গানটি কিশোরকুমার ব্যস্ততার কারনে বম্বে ছেড়ে কলকাতায় আসতে পারেন নি। সত্যজিৎ রায় বম্বে গিয়ে কিশোরকুমারের ভয়েস রেকর্ড করেন। যাবার আগে বিজয়া রায় গানটি নিজে গেয়ে টেপে রেকর্ড করে দিয়েছিলেন যাতে কিশোর কুমার অনুশীলন করতে পারেন। বিজয়া রায় দ্বিতীয় গানটি ‘ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে’ নায়িকা (চারুলতা) মাধবী মুখার্জীকে শিখিছিলেন। ‘চারুলতা’য় নায়িকা যে এমব্রয়ডারি করেছিল সেটি বিজয়া রায়ের হাতেই তৈরি। পথের পাঁচালীর অপুর চরিত্রের জন্য একজন খুদে অভিনেতার খোঁজে সবাই যখন ব্যস্ত, বিজয়া রায়ের চোখে পড়ে খুদে সুবীর ব্যানার্জীর। এমনি অনেক কাজে তিনি তাঁর স্বামীকে চলচ্চিত্রের বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করেছিলেন।
বিয়ের কিছু পরে সুপ্রভা রায় একদিন পুত্রবধূকে মা’মনি সম্বোধন করে বলেন, রায়বংশের স্থান রবিঠাকুরের বংশের পরেই। তুমি সুকুমার রায় ও উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পরিবারের সন্মান রাখতে পারবে তো? বিজয়া রায় হেসে বলেছিলেন খুব চেষ্টা করবো। ‘দেবী’ সিনেমার শুটিংয়ের সময় সুপ্রভা রায় একদিন পুত্রবধূকে বললেন, তুমি কি জানো মা’মনি তোমার স্বামী ব্রাম্ম হইয়া শ্যামাসঙ্গীত লিখ্সে? যেদিন শুনলেন যে তাঁর পুত্র রবিঠাকুরের উপর তথ্যচিত্র নির্মান করবে, সেদিন খুব খুশিই হয়েছিলেন। ১৯৫০ সালে কোম্পানী (ডি.জে.কিমার) সত্যজিৎ রায়কে ৬ মাসের জন্য বিলেত পাঠাতে চাইলে মা নির্দেশ দিলেন বিদেশে গেলে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। সত্যজিৎ রায় অফিসে এই প্রস্তাব দিলে অফিস সমস্ত খরচ বহন করা সহ তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। এবার সত্যজিৎ রায় ৬ মাসের জন্য স্ত্রীসহ ইংল্যান্ডে গেলেন।

‘পথেরপাঁচালী’ সিনেমায় সর্বজয়া, দূর্গা ও অপু।
পথের পাঁচালি সিনেমায় সত্যজিৎ রায় মানবিকতার দৃষ্টিতে গ্রামীনজীবনের অনভূতির চিত্র একেছেন। অপুকে কেন্দ্র করে গল্প হলেও নারীচরিত্রে সর্বজয়া, দূর্গা ও ইন্দির ঠাকুরনের অবস্থান স্বাতন্ত্রের দাবী রাখে। প্রত্যেকেই স্ব স্ব চরিত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যেও তাদের ব্যবহার কথাবার্তা কখনও অরুচিকর অমার্জিত মনে হয়নি। গ্রাম্য নারী চরিত্রগুলির মধ্যে ছোটখাটো ঈর্ষা লোভ হিংসা থাকলেও দূর্গার মৃত্যুর পর ও গ্রাম ছেড়ে কাশী যাবার সময় প্রতিবেশীরা সর্বজয়া ও হরিহরকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এসেছিল।
কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্রে সর্বজয়া। ছেলে অপু, মেয়ে দূর্গা, ননদ ইন্দির ঠাকুরন ও স্বামী হরিহরকে নিয়ে নিশ্চিন্দপুর গ্রামের এক দরিদ্র পরিবার। সর্বজয়ার মনে সদা সংশয় কিভাবে সংসারের গ্রাসাচ্ছদন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষের ব্যবস্থা করা। স্বামী হরিহর ভালমানুষ। যজমানগিরি ও অন্যান্য কাজ করে কোন রকমে সংসার চালায়, স্ত্রীকে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখায়। বৃদ্ধা ইন্দির ঠাকুরনের গলায় “হরি দিনতো গেল সন্ধ্যা হল পার করো আমারে” ভোলা যায়না। অশীতিপর বৃদ্ধা অভিনেত্রী চুনিবালাকে নিয়ে সত্যজিতের চিন্তার অন্ত ছিল না। দীর্ঘ তিনবছর শুটিং চলাকালীন উনার চিন্তা ছিল চুনিবালা দেবী বেঁচে থাকবেন তো! শুটিং শেষ হবার পর ছবিটি মুক্তি পাবার আগেই ১৯৫৫ সালে উনি নিউমনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি শ্রেষ্ঠ চরিত্রানেত্রী হিসাবে ম্যানিলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। পাশ্চাত্য দেশে ‘পথের পাঁচালী’ দেখে প্রতিক্রিয়া ছিল – মানবতার এক দলিল।
অপরাজিত সিনেমায় স্বামীর মৃত্যুর পর সর্বজয়া (করুনা বন্ধ্যোপাধ্যায়) বেনারসে এক বড়লোকের বাড়িতে রান্নার কাজ নিয়েছেন। একদিন দেখলেন গৃহস্বামীর জন্য অপু তামাক সাজছে। ছেলের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে মা ভয় পেয়ে বেনারস ছেড়ে ছেলেকে নিয়ে জ্যাঠামশাইয়ের গ্রামের বাড়িতে এসে উঠলেন। লোকের বাড়িতে পূজাপাঠ ও যজমানি করবার সঙ্গে সঙ্গে অপুর স্কুলে পড়াশোনা চললো। স্কুলের পাঠ শেষ করে জলপানি পেয়ে অপু কলকাতায় গিয়ে কলেজে ভর্তি হওয়ার সময় মায়ের মনে তৈরি হলো টানাপোড়েন। একদিকে ছেলেকে মায়ের কাছে রাখবার একান্ত প্রয়াস আর অন্যদিকে ছেলের ভবিষ্যতের চিন্তা। এই এক চিরকালের দ্বন্দ্ব মা ও ছেলের মধ্যে। মায়ের ভূমিকায় করুনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় মনে রাখবার মতো। ভারতের সিনেমা হলে এই ছবিটা ‘পথের পাঁচালী’ র মতোও বেশি দিন চলেনি। তবে বিদেশে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল ও অনেক পুরস্কারও পেয়েছিল।

‘অপরাজিত’ সিনেমায় মা সর্বজয়ার, বাবা হরিহরের সাথে অপু।
অপুর সংসার চলচ্চিত্রে দেখি অপু ও অপর্নার ক্ষনস্থায়ী সংসার ও প্রেম, সেই প্রেম যা গোটা সিনেমায় মনকে আচ্ছন্ন করে দেয়। বিভূতিভূষন ও সত্যজিতের যুগ্ম প্রচেষ্ঠায় আমরা পাই নারীদের মায়ামমতার অন্তসলিলা প্রবাহ। অপু তার বন্ধু পুলুর সঙ্গে ওর মামার গ্রামের বাড়িতে গেলো মামাতো বোনের বিয়ে উপলক্ষে। বিয়ের পূর্বক্ষনে জানা গেল বর পাগল। এবার সেই করুনাময়ী মা’কে দেখা গেল কঠোর হয়ে মেয়ের বিয়ে ভেঙ্গে দিতে। স্বামীর কোন আপত্তি শুনলেন না। অতঃপর অপুর সঙ্গে অপর্নার বিয়ে হলো। বিয়ের পর অপর্না কলকাতায় অপুর বাড়িতে এলো। অপুর কোন আত্মীয়স্বজন নেই বলে প্রতিবেশি মহিলারা শাঁখ বাঁজিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে নতুন বউ অপর্নাকে স্বাগত জানালো। গৃহে দারিদ্রের ছাপ, কিন্তু তারই মধ্যে সৌন্দর্যের প্রলাপ। পাশেই ট্রেন লাইন, অপুর বাঁশি, রবিঠাকুরের ছবি আর সেল্ফে রাখা বই। বড়লোক বাপের বাড়ি থেকে আসা সত্বেও দরিদ্র স্বামীর ঘরে অপর্না নিজেকে মানিয়ে নিল। হল গভীর ভালবাসা। অন্তঃসত্ত্বা অপর্না বাপের বাড়ি গেল। সেখানে সন্তান প্রসবের সময় তার মৃত্যু হয়। এই সিনেমায় আমরা পাই দৃঢ়চরিত্রের এক মহিলা (অপর্নার মা), ও এক ধনীকন্যার অবলীলায় দারিদ্রের সাথে মানিয়ে চলা।

‘অপুর সংসারে’ অপর্না ও অপু।
রবিঠাকুরের ১৯১৬ সালের লেখা ছোট গল্প ‘নষ্টনীড়’ অবলম্বনে সত্যজিৎ চারুলতা তৈরি করেন ১৯৬৪ সালে। প্রেক্ষাপট কলকাতা শহর ১৮৮০ সাল। ধনী ও বিদ্বান স্বামীর গৃহিনীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মাধবী মুখার্জী। বাড়িতে নিত্যনৈমিত্যিক কাজের ভৃত্য চাকরের অভাব নেই। সুতরাং সারাদিন চারু’র অনেক সময়। সে নভেল উপন্যাস পড়ে, হস্তশিল্পের কাজ করে আর অপেরা গ্লাস দিয়ে জানলার ফাক থেকে রাস্তার চলমান মানুষের মজার মজার দৃশ্য দেখে সময় কাটায়। স্বামী ভূপতি নবজাগরনের পরবর্তীকালের শিক্ষিত ও ধনী মানুষ। বাড়ির প্রেসে একটা ইংরাজী সংবাদপত্র প্রকাশ করে যার সম্পাদক ও মালিক সে নিজেই। স্ত্রীকে সময় দিতে পারে না বলে নিজেরও আফসোস আছে। এই সময় স্বামীর পিসতুতো ভাই অমল (সৌমিত্র চ্যাটার্জী) কলকাতার কলেজ হস্টেল ছেড়ে এই বাড়িতে চলে আসে। স্বামীর ইচ্ছেতেই সে এই বাড়িতে আসে যাতে চারুর একাকীত্ব কিছুটা কমানো যায়। অমলের তারুন্যের উচ্ছ্বাসে চারুর থেমে থাকা স্তিমিত জীবন যেন ঝড়ে বন্যার মত ভেসে গেল। সমবয়সী দুজনের মধ্যে ভাব হয়। চারু যেন অকস্মাৎ নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে। তাস খেলা, গান, কবিতা, সাহিত্য নিয়ে আলোচনা চলতে থাকলো। অমলের ইচ্ছায় চারু একটা গল্প লিখলো যেটা সাহিত্য ম্যাগাজিনে ছাপা হলো ও প্রশংসিত হলো। অমল ভাল গান গাইতো। এই মেলামেশার মধ্য দিয়ে চারুর মন অমলের দিকে আকৃষ্ট হয়, এবং দুর্বল মুহূর্তে অমলের কাছে সে প্রেম নিবেদন করে। একজন অনুগত অন্তপুরবাসিনী সাধারন গৃহস্থ বধূ ধীরে ধীরে প্রেমিকা হিসাবে নিজের অস্তিত্ব প্রমান করে।
এই গল্পটি রবিঠাকুর লিখেছিলেন ১৮৮০ সালে।
নরেন্দ্র নাথ মিত্রের ছোট গল্প অবলম্বনে সত্যজিৎ মহানগর চলচ্চিত্র নির্মান করলেন ১৯৬৩ সালে। ৫০-এর দশকে কলকাতা শহরের এক মধ্যবিত্ত পরিবার জীবনের পটভূমিকায় এই সিনেমা। এক সাধারন গৃহবধূ আরতীকে কেন্দ্র করে এই সিনেমা। অভিনয় করেছিলেন মাধবী মুখার্জী। এক মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহবধূ সমাজ ও পরিবারের ধ্যান ধারনা ভেঙ্গে স্বামীর সঙ্গে সেও চাকরি করতে শুরু করে। উদ্দেশ্য অর্থসংকট থেকে পরিবারকে কিছুটা সাহায্য করা। বহু বাধাবিঘ্ন ও শ্বশুর শাশুড়ির মতের বিরুদ্ধে গিয়ে আরতী চাকরী করতে গেল। কয়েকমাস পর ব্যাংক বন্ধ হয়ে যাবার কারনে স্বামীর চাকরি চলে গেলে আরতীই তখন সংসারের একমাত্র অর্থ উপার্জনকারী সদস্যা। সংসারে শ্বশুর শাশুড়ি ননদ ও সন্তানকে নিয়ে ৬ জনের পরিবার। এই অবস্থায় একটি ঘটনা আরতির জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সহকর্মিনীকে অন্যায়ভাবে ছাটাইয়ের প্রতিবাদে সে চাকরী থেকে ইস্তফা দিয়ে অফিস থেকে নীচে নেমে এলো। নীচে স্বামী সুব্রতর সাথে দেখা। স্বামী স্বীকার করলো এই প্রতিবাদ করবার সাহস হয়তো তার নিজেরও হতো না। আরতি বললো এত বড় শহর এত লোক চাকরি করে, সেখানে আমাদের একজনেরও কি চাকরি হবে না! ‘আমাদের নিশ্চই দুজনেরই চাকরি হবে’ বলে সুব্রত আরতীকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় নেমে এলো।
এই ছবির মাধ্যমে সত্যজিৎ রায় একজন মহিলার ঘরেবাইরে সংগ্রামের দিকটা দেখিয়েছেন। যৌথ পরিবারে সুখসাচ্ছন্দ আনবার জন্য প্রয়োজনে প্রতিবাদও করেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক নারীর প্রতিবাদ।

‘মহানগর’ সিনেমায় স্বামীর সঙ্গে নায়িকা আরতি।
প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোট গল্প অবলম্বনে দেবী সিনেমা মুক্তি পায় ১৯৬০ সালে। ১৮৬০ সালে বাংলার এক গ্রামাঞ্চলের পটভূমিকায় এই সিনেমা। সিনেমা প্রদর্শনের সময় কিছু গোঁড়া হিন্দু এই সিনেমার বিরুদ্ধে নিন্দা ও প্রতিবাদ করেছিল। সিনেমায় দেখা যায় অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার কিভাবে এক নারীকে তার আবর্তে গ্রাস হয়েছিল ।

‘দেবী’ সিনেমায় দয়াময়ির ভূমিকায় শর্মিলা ঠাকুর।
নারীকেন্দ্রিক চলচ্চিত্রে দয়াময়ীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন শর্মিলা ঠাকুর। দয়াময়ীর ১৭ বছর বয়স, অবস্থাপন্ন জমিদার বাড়ির ছোট পুত্রবধূ। স্বামী উমাপ্রসাদ (সৌমিত্র চ্যাটার্জি) কলকাতায় কলেজে পড়াশোনা করে। সেই নবজাগরনের সময় সে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের একজন সমর্থক। পিতা দোর্দন্ড প্রতাপশালি জমিদার কালীকিঙ্কর রায় (ছবি বিশ্বাস) এই বাড়ির কর্তা। তাঁর স্ত্রী বিগত হয়েছেন। তাই সারাদিন পূজাআর্চা নিয়ে থাকেন। ছোট পুত্রবধূ দয়াময়ীকে খুব স্নেহ করেন। দয়াময়ীও ভাসুর ও তাঁর পত্নীর একমাত্র সন্তান খোকাকে খুব ভালবাসে। খোকা তার কাছেই বেশিরভাগ সময় থাকে। একদিন রাতে কালিকিঙ্কর মা কালীর স্বপ্ন দেখে মা কালীর মুখের সঙ্গে দয়াময়ীর মুখের মিল খুঁজে পেলেন, ও দয়াময়ীকেই মা কালীর অবতার বলে মনে করলেন। এবার দোতলায় তাঁর নিজের ঘর ছেড়ে দয়াময়ীর স্থান হলো নীচতলায় ঠাকুরঘরে। দয়াময়ীকে ঠাকুরের আসনে বসিয়ে পূজা শুরু হলো। ছোট পুত্রবধূ এই অবস্থা মেনে নিতে পারে না, কিন্তু তাঁর কোন মতামত নেই। স্বামী কলকাতায়। বড়’জাকে বলে কলকাতায় স্বামীর কাছে খবর পাঠানো হলো। উমাপ্রসাদ গ্রামের বাড়িতে এসে পিতার দয়াময়ীর উপর এই আদেশ মানতে অস্বীকার করলেও পিতাকে কিছুতেই টলানো গেল না। কারণ গ্রামের এক প্রজার মৃত্যুমুখী বালক দয়াময়ীর চরনামৃত খেয়ে অলৌকিকভাবে প্রান ফিরে পেয়েছে। রাত্রিবেলায় উমাপ্রসাদ স্ত্রী কে নিয়ে পালিয়ে গেলেও মাঝপথে এসে দয়াময়ী ভয় পেয়ে যায়। অজানা আশঙ্কায় স্বামীর সঙ্গে যেতে অস্বীকার করে দয়াময়ী বাড়ি ফিরে আসে। ধীরে ধীরে তার মনেও অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার আচ্ছন্ন করেছে।
গ্রামগ্রামান্ত থেকে মানুষ দয়াময়ীকে ‘দেবী’ হিসাবে দেখতে আসতে শুরু করলো। ইতিমধ্যে বড় জায়ের ছেলে খোকার অসুখ করলো। ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা না করিয়ে শ্বশুরমশাই ও ভাসুর অসুস্থ খোকাকে দয়াময়ীর কোলে তুলে দিলো কিন্তু খোকা মারা গেল। খবর পেয়ে উমাপ্রসাদ কলকাতা থেকে গ্রামের বাড়িতে এলো। দয়াময়ী তখন প্রায় উন্মাদ। উমাপ্রসাদকে বললো এক্ষুনি পালিয়ে যেতে হবে, তা না হলে তাকে খুন করা হবে। অপেক্ষা না করে দয়াময়ী ‘দেবী’র সাজসজ্জা অলংকার পরে বাড়ি থেকে পালিয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অজানা উদ্দেশ্যে পালিয়ে যেতে থাকলো।
সত্যজিৎ রায়ের এটি এক ভিন্নধর্মী সিনেমা যেখানে এক কিশোরীর চরিত্রের মাধ্যমে সমাজের অন্ধভক্তি ও কুসংস্কারের ফল মানুষকে কিভাবে সুস্থ ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা থেকে সরিয়ে দেয়, তারই একটা উদাহরন।
বিভূতিভূষনের আরকটি গল্প অবলম্বনে সত্যজিৎ তৈরি করলেন অশনিসংকেত। ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় বাংলার এক গ্রামের ছবি। মানবিকতা, নারী চরিত্রের মায়া মমতা, খাদ্যের জন্য হিংসা মারামারি , খাদ্যের জন্য নিরন্ন মানুষের দলে দলে গ্রাম থেকে শহরে গমন , ইত্যাদি নিয়ে ছবি। এত অভাবের মধ্যেও দেখা যায় কিছু নারীচরিত্র পুরুষের অগোচরে ক্ষুধায় তাড়িত মানুষকে লুকিয়ে খাদ্যের সামান্য কিছু ব্যবস্থা করছে। কিছু নারী ক্ষুধার তাড়নায় বিপথেও চলে যাচ্ছে। তখন অঙ্গনা (পন্ডিত মশাই গঙ্গাচরনের স্ত্রী) নারীর দৈহিক মর্যাদা বাঁচাতে অন্য মহিলার অপরাধীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। গঙ্গাচরন (সৌমিত্র চ্যাটার্জী) গ্রামে যজমানি, বৈদ্যগিরি ও শিক্ষকতা করেও খাবারের ব্যবস্থা করতে অসমর্থ হলেন। দলে দলে মানুষ খাবারের সন্ধানে শহরের দিকে যাত্রা করলো। এত দুঃখের মধ্যে অঙ্গনা ( ববিতা – বাংলাদেশের অভিনেত্রী) এক খুশীর খবর স্বামীকে দিল – সে সন্তান সম্ভবা। পরিশেষে গঙ্গাচরন তার স্ত্রীকে (অঙ্গনা) নিয়ে মানুষের দলে যোগ দিল কলকাতা শহরের উদ্দেশ্যে।

‘অশনিসংকেত’ ছবিতে ববিতা।
রবিঠাকুরের লেখা ১৯১৬ সালের ঘরেবাইরে উপন্যাস অবলম্বনে একই নামে চলচ্চিত্র নির্মান করেন ১৯৮৪ সালে। ঘটনার প্রেক্ষিত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তি সময়। ত্রিকোন প্রেমের মাধ্যমে তৎকালীন স্বদেশী রাজনৈতিক পরিস্থিতির কাহিনী। নিখিলেশ গ্রামের জমিদার। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত উদার ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী। বাড়িতে গভর্নেস রেখে স্ত্রী বিমলাকে ইংরাজী লিখতে পড়তে শিখিয়েছে। গান গাইতে শিখিয়েছে। বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বইপুস্তক পড়তে শিখিয়েছে। স্বামী চায় বিমলা অন্দরমহল থেকে বাইরে আসুক। অন্দরমহল থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে বিমলা পুরুষ মানুষদের সঙ্গে পরিচিত হলো। এককালে কলেজে নিখিলেশের বন্ধু সন্দীপ গ্রামে এলো স্বদেশী রাজনীতি করতে। প্রানোচ্ছাসে ভরপুর সন্দীপের দেশ প্রেম দেখে বিমলা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর সন্দীপ আকৃষ্ট হলো বিমলার রূপ ও প্রজ্ঞা দেখে। দুজনের মধ্যে প্রেম হলো।
বিদেশী দ্রব্যের বর্জনের জন্য সন্দীপ গ্রামের মানুষের আহ্বান করলে গরীব মুসলমান প্রজারা তার ডাক অস্বীকার করে। বিদেশী দ্রব্য শস্তা ও টেকসই। তখন সন্দীপ ও তার দলের লোকেরা গরীব মানুষের বস্তিতে আগুন লাগিয়ে দেয়, তাঁদের নৌকা ডুবিয়ে দেয়। গ্রামে দাঙ্গা লেগে গেল। সন্দীপের প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করে বিমলা তখন তাঁকে অস্বীকার করে। সন্দীপ গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়, এবং বিমলাও নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং নিখিলেশের কাছে ফিরে আসে। স্বামীও তাকে গ্রহন করে। দুই দলের হিংসা দাঙ্গা থামাতে নিখিলেশ গ্রামে গেলে সে নিহত হয়। চলচ্চিত্রে স্বদেশী রাজনীতির মধ্যে নারীচরিত্রের একটা দিক এখানে দেখানো হয়েছে।
জলসাঘর তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়ের কাহিনী নিয়ে ১৯৫৮ সালে পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের চতুর্থ চলচ্চিত্র। পদ্মাদেবী ছাড়া মোটামুটি নারীচরিত্র বর্জিত এই সিনেমার পর্দায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকায় বেগম আখতার ও রওশন কুমারী। সত্যজিৎ চাইতেন সেরা শিল্পীদের নিয়েই চিত্রনির্মান করবেন। বেগম আখতার (প্রকৃত নাম আখতারি বাই ফৈজাবাদী) এই সিনেমায় গজল গায়িকা দুর্গা বাই চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তাঁকে বলা হয় “মল্লিকা-ই-গজল” (গজলের রানী), যাকে হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের গজল, দাদরা, ও ঠুমরি ঘরানার অন্যতম সেরা গায়িকা হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

অন্যদিকে পদ্মশ্রী সন্মানিত রোশন কুমারী ফকির মোহাম্মদ ছিলেন ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যশিল্পী, অভিনেতা এবং কোরিওগ্রাফার, যাকে অনেকে কথকের ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের অন্যতম প্রবর্তক হিসাবে বিবেচনা করেন । তিনি জয়পুর ঘরানা অনুসরণ করেন এবং মুম্বাই নৃত্যকলা কেন্দ্রর জলসাঘরের আগে ১৯৫৩ সালে, বিমল রায় তাঁকে একটি কথক গান পরিবেশনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। এরপর ১৯৫৬ সালের বসন্ত বাহার, সোহরাব মোদি’র ওয়ারিস, এবং হিন্দি / উর্দু দ্বিভাষিক মির্জা গালিব- এ অভিনয় করেন। জলসাঘরে তার দ্বারা সম্পাদিত একটি নাচের ক্রম ব্যবহার করেছিলেন।
অভিযান সিনেমায় গুলাবি (ওয়াহিদা রেহমান) একজন বিষণ্ণ, প্রদর্শক এবং সুন্দর গ্রামের বিধবা। প্রধান চরিত্রে জাতিতে রাজপুত ট্যাক্সিচালক নরসিং এক বেপরোয়া প্রকৃতির মানুষ, কারও তোয়াক্কা সে করে না। একদিন এস.ডি.ও সাহেবের গাড়িকে ওভারটেক করে বেরিয়ে গেলে এস.ডি.ও সাহেবের আত্মসম্মানে ঘা লাগে – তিনি নরসিং-এর লাইসেন্স বাতিল করে দিলেন। নিরুপায় নরসিং সব ছেড়ে চলে যাওয়ার পথে ব্যবসায়ী সুখনরামের সঙ্গে দেখা হওয়ায় পুনরায় ফিরে আসতে বাধ্য হল। উনি একজন স্থানীয় মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী যিনি চোরাচালান ও মানব পাচারের রেকর্ড করেন। অন্যদিকে গুলাবী (ওয়াহিদা রহমান) নামে যে মেয়েটিকে নরসিং সেদিন দেখেছিল সুখনরামের সঙ্গে, তার প্রতি একটা টান অনুভব করে নরসিং। যদিও জোসেফের (জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়) বোন নীলিমার (রুমা গুহঠাকুরতা) প্রতি অনুরাগ ছিল নরসিং-এর, কিন্তু যেদিন সে জানতে পারলো নীলিমার অন্য এক ভালবাসার মানুষের কথা, সেদিনই সরে এসেছিল সে। একদিন সুখনরামের চোরাই মাল নিয়ে বেরিয়েও নরসিং ঠিক করে, এই চোরাই মাল সে ফেরত দিয়ে দেবে। সুখনরামের গো-ডাউনে গিয়ে সে শোনে, সুখনরাম গুলাবীকে নিয়ে চলে গেছে। সে বেড়িয়ে পড়ে অভিযানে, সুখনরামের সন্ধানে। যেভাবেই হোক, এই অভিযানে গুলাবীকে তাকে ফিরে পেতেই হবে।
গুলাবি সহজাতভাবে নরসিংহের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তার মর্যাদা হারানো সত্ত্বেও, তিনি এখনও জীবনের উজ্জ্বল দিকটি দেখেন এবং বিশ্বাস করেন যে নরসিংহ অনৈতিক নয়। সে প্রথম থেকেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং শারীরিক সম্পর্কের জন্য প্রস্তুত হয়, যদিও সে সময় সুখরাম তাকে যে পতিতা হতে চেয়েছিল তা নয়, বরং একজন গ্রামের মেয়ে হিসেবে।

আগন্তুক সিনেমায় ব্যাবহার করেছেন বীরভূমের লোকগীতি ও লোকনৃত্য। যেহেতু সিনেমায় নাচের দৃশ্য আছে, সেই কারণে তিনি মমতাশঙ্করকেই নির্বাচিত করেছিলেন। অরন্যের দিনরাত্রি সিনেমায় এক সাঁওতালি যুবতী দুলি’র ভূমিকায় ছিলেন সিমি গারেওয়াল। ছোট্ট একটি ভূমিকা, কিন্তু সত্যজিৎ বম্বে থেকে সঠিক শিল্পীকেই বেছে নিয়েছিলেন।
ঠিক সেরকমই খুবই ছোট ভুমিকায় নিয়েছিলেন ক্যাবারে শিল্পী মিস শেফালী’কে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আর সীমাবদ্ধ সিনেমায়। কারণ সেই এক, তাঁর ধারণায় মিস শেফালী হবেন এই ভূমিকায় সবথেকে উপযুক্ত।
আরও দুটি নারীচরিত্র বর্জিত সিনেমায় বিশিষ্ট গুণী নারীদের ব্যাবহার করেছেন। সে দুটি হলো সোনার কেল্লা ও জয়বাবা ফেলুনাথ। সোনার কেল্লায় ছিল রাজস্থানী লোকগীতি। আর জয়বাবা ফেলুনাথে বেনারসের ঘাটে দুর্দান্ত কন্ঠে একজন গাইছেন “মোহে লাগি লগন”। এই অসাধারন ভজনটি গেয়ে ছিলেন রেবা মুহুরী। এর আগেই শতরঞ্জ কী খিলাড়ি সিনেমায় দুটি ঠুংরী ও দাদরা গেয়েছিলেন।
সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে আমরা দেখি নারী চরিত্র পুরুষদের পাশাপাশি ভাবে থেকেছে। পুরুষ চরিত্রের ছায়ায় নারীচরিত্র ঢাকা পরে যায়নি। নবজাগরনের ধারা অটুট রেখে উনি চলচ্চিত্রে নারী চরিত্রকে পুরুষের পাশাপাশি মুখ্য ধারায় স্থান দিয়েছেন।
তথ্যসংগ্রহ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার –
১) উইকিপিডিয়া
২) আমাদের কথা – বিজয়া রায়




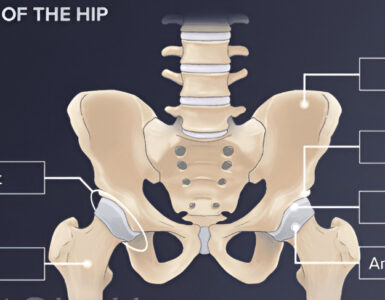











লেখাটি খুব ভাল লাগল। সত্যজিত রায়ের চলচ্চিত্রে নারী চরিত্র সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। ওনার থেকে আরো এই ধরনের লেখা আশা করি।
লেখক অনেক সময় নিয়ে পড়াশোনা করে এটা লিখেছেন। সঙ্গে ছবিগুলিও বেশ মানানসই। অনেক ধন্যবাদ, আরও লিখুন
অনেক পড়াশোনা করে, সুন্দর একটা প্রবন্ধ। সাহিত্যিকার সাথে যুক্ত সকলকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। বেশ উচ্চমানের পত্রিকা হিসেবে সাহিত্যিকা নিজের স্থান করে নিয়েছে।
এর আরও সাফল্য কামনা করি।
লেখা টি খুব ভাল লাগল।