
সাঁওতালি ভাষার ‘রাঢ়ো’ (পাথুরে জমি) শব্দটি থেকে রাঢ় শব্দটি গৃহীত হয়েছে। অন্যমতে, গ্রীকদের দেওয়া গঙ্গারিডাই পরবর্তীকালে গঙ্গাহৃদি, গঙারাঢ় থেকেই রাঢ়রাজ্য নামটির উৎপত্তি। উত্তর ও দক্ষিণের বিচারে এই জনপদ উত্তর রাঢ় এবং দক্ষিণ রাঢ় নামে অভিহিত হয়ে থাকে। অজয় নদ এই রাঢ় অঞ্চলের সীমানা ছিল। বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের হওড়া, হুগলি ও বর্ধমান জেলার কিছু অংশ নিয়ে দক্ষিণ-রাঢ়দেশ গঠিত ছিল। দক্ষিণ রাঢ়ের উত্তরদিকের পুরো অংশটুকু উত্তর রাঢ় বলা হয়।পশ্চিমের মালভূমি থেকে কাঁকুড়ে পলিমাটি বয়ে এনে এই অঞ্চলের নদীগুলি এই সমভূমি সৃষ্টি করেছে। এই অঞ্চলে ল্যাটেরাইট লাল মাটির প্রাধান্যই বেশি। মাটির স্তর এখানে অগভীর। মাটির জলধারণ ক্ষমতা কম। নদী অববাহিকাগুলি বাদে অন্যত্র তাই মাটি খুব একটা উর্বর নয়। এই অঞ্চলের প্রধান নদনদীগুলো হলো- ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, দ্বারকেশ্বর, শিলাই ও কংসাবতী (কাঁসাই)। এই নদীগুলির উৎপত্তিস্থল ছোটনাগপুর মালভূমি ও এগুলির প্রতিটিই ভাগীরথী-হুগলি বা তার কোনও উপনদীতে মিলিত হয়েছে। সুবর্ণরেখা নদীর অংশবিশেষও এই অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। এই নদীগুলিতে বর্ষাকালে প্রায়ই দুকুল ছাপিয়ে বন্যা দেখা দেয়।

সমুদ্র থেকে দূরে অবস্থিত হওয়ায় রাঢ় অঞ্চলের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। গ্রীষ্ম ও শীতকালের গড় তাপমাত্রা এখানে যথাক্রমে ৩৫ ডিগ্রি থেকে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও ১২ ডিগ্রি ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এই অঞ্চলে বছরে গড়ে ১৪০-১৬০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। তবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ উত্তর রাঢ়ের তুলনায় দক্ষিণ রাঢ়ে বেশি। এপ্রিল-মে মাস নাগাদ কালবৈশাখী ও অক্টোবরে আশ্বিনের ঝড়ও এই অঞ্চলের জলবায়ুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক উদ্ভিদের মধ্যে শাল, মহুয়া, শিমূল, কুল, বাবলা, বাঁশ ও বিভিন্ন প্রজাতির ঘাস উল্লেখযোগ্য। এক সময় এই অঞ্চলে গভীর বন ছিল। বর্তমানে চাষাবাদের কারণে গাছপালা বিহীন প্রান্তরে পরিণত হয়েছে।






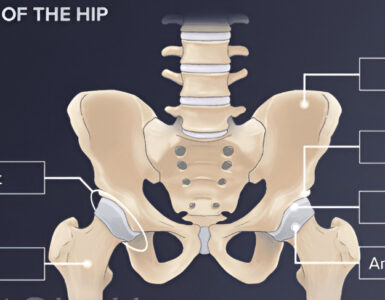











[…] ইঞ্জিনিয়ারিং Berhampore Sankar Dhar, 1977 Mechanical Engineering আমার কয়েকটি প্রবন্ধ ডঃ আশীষ ভট্টাচার্য্য, ১৯৭৭ […]