রঙ লাগালে মনে মনে
প্রমিত বসু, ২০০১ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
‘রঙ যেন মোর মর্মে লাগে, আমার সকল কর্মে লাগে’
‘রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোক পলাশে,
রাঙা নেশা মেঘে মেশা প্রভাত-আকাশে,’
‘তোমার অশোকে কিংশুকে
অলক্ষ্য রঙ লাগল আমার অকারণের সুখে’
প্রতি বছর বসন্তোৎসব এলেই যেন মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের বসন্ত পর্যায়ের এই রকমই গুটিকয়েক গানের কলি। ওয়াশিং পাউডার কথাটা শুনলেই প্রথমেই যেমন মনে আসে নিরমা, ঠিক তেমনই যেন দোলের কথা এলেই যেন এইরকম কিছু গান ঘুরে ফিরে মনে এসে পড়ে। অথচ বাস্তবিক জীবনে নিরমা যেমন ওয়াশিং পাউডার হিসেবে বাঙালিদের ঘরে খুব বেশি ঢুকতে পারে নি, তেমনই এই গানগুলোও আমাদের মর্মে ও কর্মে আর ঢুকতে পারলো কোথায়!
রবীন্দ্রনাথ জীবনভর নিজের জীবনকে রঙিন করে তোলার প্রয়াস করে গেছেন। তাঁর প্রতি পরতে রয়েছে রঙের মর্মে আর কর্মে সদর্প উপস্থিতি। সেই রঙের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেই ‘যাত্রীর উৎসব’ প্রবন্ধে লেখেন ‘বিশ্বভুবনে ফুলের যে রঙ সহজে পুষ্পকাননে প্রকাশ পেয়েছে, নক্ষত্রলোকে যে আলো সহজে জ্বলেছে, এখানে তো সে রঙ লাগা সহজ হয় নি, এখানে সম্মিলিত চিত্তের আলো তো সহজে জ্বলে নি।’
সারাজীবন রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির রঙিন রূপকে তাই নিজের মধ্যে আত্মস্থ করার প্রয়াস করে গেছেন। প্রকৃতিতে যেমন সাম্যবাদের জয়গান সেখানে বেজে চলে অবিরাম, শূণ্য আর পূর্ণর মাঝে যেমন থাকে নিরবিচ্ছিন্ন সহাবস্থান, ঠিক সেই রকম ভাবেই নিজস্ব জীবনদর্শনে রবীন্দ্রনাথ সাম্যবাদের চর্চা করে গেছেন জীবনভর। ‘সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে’ দর্শনে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ তাই ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে পরিণত করেছিলেন সামাজিক উৎসবে। দুর্গাপুজো হয়ে ওঠে শারদোৎসব, বড়দিনের নামকরণ করেন খৃষ্টোৎসব, আর দোল পরিণত হয় বসন্তোৎসবে। আর রাখীবন্ধনকে নিয়ে এলেন সমাজের সকলের মাঝে, কোনো নিষেধের তোয়াক্কা না করে সম্প্রীতির নতুন বার্তা নিয়ে রাখীবন্ধন পালন করলেন আস্তাবলের সহিসদের সাথে, মসজিদের ইমামের সাথে।
শিলাইদহে জমিদারিতে মুছে দিতে চাইলেন সকল সামাজিক বিভেদরেখা। শিলাইদহতে জমিদারির দায়িত্ব নিয়ে দেখেন জমিদারিতে মুসলমান প্রজারা বরকন্দাজের চাকরি করেন, যেজন্য তারা দুঃখিত। রবীন্দ্রনাথ তাদের মধ্যে সামান্য শিক্ষিত অনেককে জমিদারির মুহুরী আর আমিনের কাজ শেখানোর ব্যবস্থা করলেন। কিছু শিক্ষাভিলাষী তরুণ মুসলমানকে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলেন। অন্য জমিদারি থেকে নমশূদ্র সমাজকে এনে বসালেন নিজের জমিদারিতে, তাদের জমি দিলেন। একসাথে সহাবস্থান আর কাজ করার ফলে হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিরোধ অনেকাংশেই কমে গেলো।
রবীন্দ্রনাথ একেবারে প্রথম থেকেই চেয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে জাতপাতের অস্পৃশ্যতা বা ধর্মের বিভেদ কাটিয়ে উঠে এক সর্বজনীন বিদ্যালয় তৈরী করতে। প্রথম দিকে বেশ বাধাও জুটেছিল, অভিভাবক, ছাত্র, এমনকি কিছু শিক্ষকদের কাছ থেকে। শিক্ষকদের মধ্যে বেশ কিছু তাবড় তাবড় শিক্ষকও ছিলেন। একবার ঠিক হয়েছিল, এক শূদ্রকে দিয়ে রান্না করানো হবে, বিধুশেখর শাস্ত্রী, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যের মতো শিক্ষকরা রাজি হন নি। শান্তিকেতনের শুরুর লগ্ন থেকেই রবীন্দ্রনাথ মুসলমান ছাত্রগ্রহণে আগ্রহী ছিলেন। কোনো কোনো শিক্ষকরা বিরোধিতা করেন, রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হয়ে বলেন ‘আপনারা মুসলমান রুটিওয়ালা অবধি চালাইয়া দিতে চান, ছাত্র কী অপরাধ করিল?’ সেই শান্তিনিকেতনে অনেক পরে ১৯২১ সালে প্রথম মুসলমান ছাত্র এলেন; তিনি আমার শ্রদ্ধেয় সিতু মিয়াঁ (সৈয়দ মুজতবা আলী)।
এই রঙের অর্থ আজও আমাদের মর্মে ও কর্মে আর ঢুকলো কোথায়!!
রবীন্দ্রনাথের নাটকের প্রৌঢ় রাজা যখন নিজের সাদা চুল দেখে বিষন্ন হয়ে পড়েন, তখন তাঁর কবি তাঁকে বোঝান যে এই সাদা রঙের মধ্যেই তো সব রঙের বাস। তাই তো সেই সাদা কালোর মধ্যেই প্রকৃতিতে এতো রূপের খেলা রঙের মেলা। এ যৌবন ম্লান যদি হল তো হোক না। এরপর না হয় আরেক যৌবনলক্ষ্মী আসুক বৈরাগীর বেশে। যে বৈরাগী মনের শান্তির উপরে কোনো আসক্তি নেই, সম্পদের ওপর একটুও লোভ নেই, সে সংসারের মধ্যে থেকেই বেড়িয়ে পড়ে বৈরাগ্যসাধনে। পাহাড়ের গুহা ছেড়ে যে-নদী বেরিয়ে পড়ে সেও যেন বেরোয় এক বৈরাগ্য থেকে। সে অনায়াসে আপনাকে ঢেলে দিতে দিতেই নিজেকে খুঁজে পায়।
আর আপনাকে ঢেলে দেওয়ার সেই আনন্দেই যেন চল্লিশোর্ধ্ব রবীন্দ্রনাথ নিজের যাবতীয় পুঁজি উজাড় করে তৈরী করে ফেললেন এক ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয়, যার ভবিষ্যৎ রূপরেখা থাকে আক্ষরিক অর্থে এক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের। এর পিছনে ছিল রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ নিজস্ব দর্শন যেখানে শিক্ষাকে করে তুলতে চেয়েছিলেন জীবনের অঙ্গ, যেখানে শিক্ষার সঙ্গে যোগ হবে আনন্দের। ১৮৯৪ সালে ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন: ‘যে শিক্ষায় মানুষের মনকে সচেতন করে দেয়, বিশ্বসংসারকে নানাভাবে অনুভব করবার শক্তি সঞ্চার করে, সেইটেই হচ্ছে মানুষে র পক্ষে খুব একটা মূল্যবান শিক্ষা।’
রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন তাঁর বিশ্বভারতীতে ভারতবর্ষের নিজের ভাবনার সঙ্গে হোক বিশ্বভাবনার মেলবন্ধন। ১লা বৈশাখ ১৩৩০ (১৯২৩) নববর্ষের ভাষণে কবি বলেন: “আমরা এখানে কোন্ মন্ত্রের রূপ দেখব বলে নিয়ত প্রত্যাশা করব। সে মন্ত্র হচ্ছে এই যে— ‘যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্ (অর্থাৎ কিনা বিশ্ব যেখানে মিলেছে এক নীড়ে)।’ তাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে জগদানন্দ রায়, ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসুর মতো ভারতীয় শিক্ষকের সঙ্গে থাকেন বিদেশী অধ্যাপকেরা। চিন থেকে আসেন তরুণ তান-য়ুন-শান, আসেন জার্মান ভাষাতত্ত্ববিদ মার্ক কার্লঙ্ক, ফরাসী অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি প্রমুখ। আজ আমরা একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির এতো অগ্রগতির মধ্যেও আমরা দেখি কোনো ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আন্তর্জাতিক কোলাবোরেশন কত কঠিন, সেখানে রবীন্দ্রনাথ সেই ধারণার প্রকৃত বাস্তবায়ন করেন একশো বছরেরও বেশি সময় আগে।
কোনো পরিপূর্ণ উপার্জন কাঠামো ছাড়াই তৈরী হল সেই প্রতিষ্ঠান। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সময় থেকেই অর্থাভাব তাড়না করে চলেছে বিশ্বভারতীকে। স্ত্রীর গয়না বিক্রি করে, নিজের বাংলা বইয়ের লভ্যাংশ বিশ্বভারতীকে উৎসর্গ করেও সে অর্থসঙ্কট মেটেনি। তবু কর্মী, জ্ঞানী তৈরির লক্ষ্যে, মুক্তবন্ধ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে মাধুকরী হাতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, জমিদার রবীন্দ্রনাথ বেরিয়ে পড়লেন দেশ দেশান্তরে। কখনও অর্থের জন্য অভিনয়ের দল নিয়ে দেশে দেশে ভ্রমণ করছিলেন, কখনও বা দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করে বক্তৃতা দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করেছেন তিনি। অপমান, বিদ্রুপ আর উদাসীনতার প্রাপ্তিও জুটলো পদে পদে, তবুও সেই প্রয়াসের একরত্তি খামতি রইলো না কোথাও। কবির ভাষায়: “ভিক্ষাবৃত্তির ঘূর্ণি হাওয়ায় আমাকে দ্বারে দ্বারে ঘুরপাক খাইয়ে বেড়াচ্ছে।” নিরন্তর ভ্রমণ তাঁকে পরিশ্রান্ত করছিল, তারই মধ্যে সান্ত্বনা পেয়েছেন এই ভেবে যে বিশ্বভারতীর অন্তরের কথা তিনি নানা জায়গায় বলতে পারছেন; জানাতে পারছেন বিশ্বভারতী সব জাতি-ধর্ম-ভাষার মিলনকেন্দ্র হবে, এই তার উদ্দেশ্য। নিজের নাটকের কবির দর্শনের মতোই নিজের জীবনকেই নদীর মতো নিজেকে ঢেলে দিতে দিতেই নিজেকে আবিষ্কার করেন রবীন্দ্রনাথ।
জীবনের সেই রঙের অর্থই বা আজ আমরা বুঝলাম কোথায়!!
আবার ষাটোর্ধ্ব জীবনে পৌঁছে পরিবারহারা সন্তানহারা বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ ঝরা পাতার মধ্যে আবার নতুন করে খুঁজে পান জীবনের অর্থ। ধুলোয়, ঘাসে পড়ে থাকা ঝরা পাতার মধ্যে দেখতে পান হোলিখেলা, আর তাই সেই ঝরা পাতার রঙ নিতে চান নিজের উত্তরীয়তে। লিখে ওঠেন:
‘অস্তরবি লাগাক পরশমণি
প্রাণের মম শেষের সম্বলে।’
আর প্রায় সেই সময় থেকে কবি, নাট্যকার, দার্শনিক, সংস্কারক, শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথের সাথে নতুন করে দেখা যায় চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথকে। ১৯২৮ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথের রঙের হিল্লোল ছড়িয়ে পড়ে তুলি থেকে ক্যানভাসে। ‘পূরবী’ কাব্যগ্রন্থর পরিমার্জনা বা কাটাকুটি যেন রবীন্দ্রনাথের শিল্পী হয়ে ওঠার শুরুর গল্প। সেই সময় থেকে পরবর্তী দশ বারো বছরে সৃষ্টি হল আড়াই হাজারের ওপর ছবি। সেই ছবিগুলোতে যেমন রয়েছে প্রেম ও প্রকৃতি, তেমনই রয়েছে নির্জনতার নিবিড় আশ্রয়, নারী ও মায়া। নিজের প্রজ্ঞার প্রয়োগে যেমন গড়েছেন , ছবির শরীরকে আধুনিক করতে তেমনি ভেঙেছেন প্রথাগত ছক। ‘শনিবারের চিঠি’ তে প্রকাশিত ‘চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ’ শিরোনামে স্বয়ং যামিনী রায় তাঁর আঁকা ছবি নিয়ে বলেন ‘তাঁর কল্পনার অসামান্য ছন্দময় শক্তিতে তিনি রেখা ও রঙের ব্যবহার আশ্চর্যরকম ভাবে ব্যবহার করেছিলেন।’
জীবনকে নতুন করে রঙিন ভাবে শুরু করার এই উদ্যম আজ আমাদের মধ্যে কতটাই বা আছে!!
প্রতি বছর দোল আসে, দোল যায়! কিন্তু আমাদের উপলব্ধির আর কোনো উত্তরণ ঘটে না! পরে পাওয়া চোদ্দো সিকে এই দানবিক সৃষ্টি থেকে আমরা বেছে নিই বাঁধা গতের কিছু গান বা কবিতা, তোতাকাহিনীর তোতার মতো একই জিনিস আউড়ে বেড়াই কিছুদিন ধরে, তারপর আবার সেই আসছে বছর আবার হবে! অথচ জীবনের রঙের অর্থের অনুধাবন করতে হলে আমাদের হাতের কাছে রয়েছেন সেই আদ্যিকালের জোব্বা পরা মানুষটা। যিনি জীবনের এতো প্রতিকূলতার মধ্যেও বলে ওঠেন:
‘অরুণবীণা যে সুর দিল রণিয়া সন্ধ্যাকাশে সে সুর উঠে ঘনিয়া
নীরব নিশীথিনীর বুকে নিখিল ধ্বনি ধ্বনিয়া।
আয় রে তোরা, আয় রে তোরা, আয় রে–
বাঁধন-হারা রঙের ধারা ওই-যে বহে যায় রে॥’




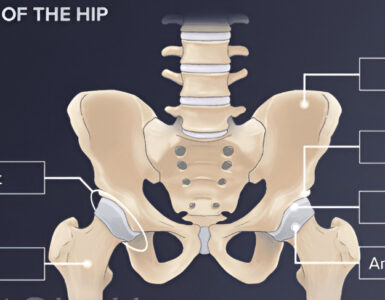











Add comment