বাঙ্গালীর শারদীয়া দুর্গোৎসবের নানান দিক
প্রদীপ ভৌমিক, ১৯৭৪ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
ভূমিকা
বাঙালীর দুর্গাপূজা কখন, কেন, কিভাবে, এই নিয়ে এর আগে সহস্র সহস্র লেখা হয়েছে। আমি এই “কখন, কেন, কিভাবে” এবিষয়ে সামান্যমাত্র বুড়ি ছুঁয়েই অন্যবিষয়ে চলে যাবো, যা বহুলপ্রচলিত বা সর্বজনজ্ঞাত নয়।
পৌরাণিক উপাখ্যান
ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ (মূল নিবন্ধ: ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ)। এই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে, কৃষ্ণই প্রথম দুর্গাপূজা করেছিলেন। আর বিভিন্ন দেবদেবীরা কীভাবে দুর্গাপূজা করেছিলেন, তার একটি তালিকা এই পুরাণে পাওয়া যায়। তবে কোনো পৌরাণিক গল্পের বিস্তারিত বর্ণনা এই পুরাণে দেওয়া হয়নি। বলা হয়েছে:
প্রথমে পূজিতা সা চ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
বৃন্দাবনে চ সৃষ্ট্যাদ্যৌ গোলকে রাগমণ্ডলে।
মধুকৈটভভীতেন ব্রহ্মণা সা দ্বিতীয়তঃ।
ত্রিপুরপ্রেষিতেনৈব তৃতীয়ে ত্রিপুরারিণা।।
ভ্রষ্টশ্রিয়া মহেন্দ্রেন শাপাদ্দুর্বাসসঃ পুরা। চ
তুর্থে পূজিতা দেবী ভক্ত্যা ভগবতী সতী।।
তদা মুনীন্দ্রৈঃ সিদ্ধেন্দ্রৈর্দেবৈশ্চ মুনিমানবৈঃ।
পূজিতা সর্ববিশ্বেষু বভূব সর্ব্বতঃ সদা।।
অর্থাৎ, সৃষ্টির প্রথম যুগে পরমাত্মা কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের আদি-বৃন্দাবনের মহারাসমণ্ডলে প্রথম দুর্গাপূজা করেন। এরপর মধু ও কৈটভ নামে দুই অসুরের ভয়ে ব্রহ্মা দ্বিতীয় দুর্গাপূজা করেছিলেন। ত্রিপুর নামে এক অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে শিব বিপদে পড়ে তৃতীয় দুর্গাপূজার আয়োজন করেন। দুর্বাসা মুনির অভিশাপে লক্ষ্মীকে হারিয়ে ইন্দ্র যে পূজার আয়োজন করেছিলেন, সেটি ছিল চতুর্থ দুর্গাপূজা। এরপর থেকেই মুনিঋষি, সিদ্ধপুরুষ, দেবতা ও মানুষেরা নানা দেশে নানা সময়ে দুর্গাপূজার বিভিন্ন প্রথার প্রচলন করেছেন।
দেবীমাহাত্ম্যম্
 বৈষ্ণবী ও বারাহী দেবী শুম্ভ-নিশুম্ভের অসুরসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধরতা, সপ্তদশ শতাব্দীর পুথিচিত্রণ
বৈষ্ণবী ও বারাহী দেবী শুম্ভ-নিশুম্ভের অসুরসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধরতা, সপ্তদশ শতাব্দীর পুথিচিত্রণ
মূল নিবন্ধ: শ্রীশ্রীচণ্ডী
দুর্গা ও দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে যতগুলি পৌরাণিক গল্প প্রচলিত আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় গল্পটি পাওয়া যায় শ্রীশ্রীচণ্ডী বা দেবীমাহাত্ম্যম্-এ। এটি হিন্দুরা এতটাই মান্য করে যে শ্রীশ্রীচণ্ডীর পাঠ দুর্গাপূজার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। দেবীমাহাত্ম্যম্ আসলে মার্কণ্ডেয় পুরাণ-এর একটি নির্বাচিত অংশ। এতে তেরোটি অধ্যায়ে মোট সাতশোটি শ্লোক আছে। এই বইতে দুর্গাকে নিয়ে প্রচলিত তিনটি গল্প ও দুর্গাপূজা প্রচলনের একটি গল্প রয়েছে। প্রতিটি গল্পে দুর্গাই কেন্দ্রীয় চরিত্র।
সম্প্রতি একটি জরিপে দেখা গেছে কৃত্তিবাস ওঝা যে কাহিনী সংকলন করেছিলেন, সেটি রামচন্দ্রের প্রকৃত জীবনী বাল্মিকী রামায়ণে বা রামায়ণের অন্যান্য অনুবাদসমূহ যেমন, অবধি ভাষায় তুলসীদাসের রামচরিতমানস, তামিলভাষায় কাম্ব রামায়ণ, কন্নড় ভাষায় কুমুদেন্দু রামায়ণ, অসমীয়া ভাষায় রামায়ণ, ওড়িয়া ভাষায় জগমোহন রামায়ণ, মারাঠি ভাষায় ভাবার্থ রামায়ণ, উর্দু ভাষায় পুথি রামায়ণ প্রভৃতিতে উল্লেখিত হয় নি। এছাড়াও যোগবাশিষ্ট রামায়ণেও উক্ত হয়নি।
আদিকালে মানুষ ছিলো প্রকৃতির পূজারি – সূর্য, চন্দ্র, আগুন, জল, পাহাড়, বজ্রবিদ্যুত। ইতিহাসবিদরা মনে করেন যে কয়েক হাজার বছর আগে বহিরাগত আর্য ও মূল অধিবাসী অনার্যদের যুদ্ধে আর্যরা যুদ্ধে জয় করে নিজের সমাজ গঠন করে। আর্য পন্ডিত ঋষিরা সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ ধর্ম গ্রন্থ রচনা করলেন। সনাতন ধর্মের রাম, দূর্গা, ব্রম্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও অন্যান্য দেবদেবীদের উল্লেখ করলেন। আর কৃত্তিবাস রামায়ন পড়ে বাঙ্গালী জানলো রাবনকে যুদ্ধে হারাবার জন্য রাম শরৎকালে দূর্গার অকালবোধন করেছিলেন। বেলগাছতলায় মহাদেবের অনুমতি নিয়ে দেবীকে নিদ্রা থেকে জাগিয়ে বোধন পালন করা হয়।
এর থেকেই বাঙালীর শারদীয়া দূর্গাপূজার সূত্রপাত।
পুঁথিতে দুর্গার উল্লেখ আছে বৌধায়ন এবং সাংখ্যায়নের সূত্রে। আমাদের মহাকাব্যেও দেবীশক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু সিংহবাহিনী যুদ্ধরতা দশভুজা দেবীর বিশেষ উল্লেখ নেই। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে অর্জুন দুর্গার পূজা করছেন। স্কন্দ-কার্তিকের মহিষাসুর নিধনের কথাও আছে।
আশ্বিন-কার্তিকের দুর্গাপূজা কৃষিপ্রধান গ্রামবাংলার জীবনের সাথে জড়িত। এখানে আমন ধান আসার অনেক আগে থেকে আউশ ধানের প্রচলন ছিল, সেই ধান পাকার সময়েই এই পূজা। মহিষের সম্পর্কে অনেকের প্রচলিত মত এই যে এই প্রাণীটি নিচু জমিতে বাস করে, আর সেই অঞ্চলে চাষের প্রসারের জন্য কৃষিজীবী মানুষ মোষ তাড়িয়ে কৃষিজমি দখল করে। মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার আরাধনা হয়তো এই মহিষ নির্মূল অভিযানকে একটা ধর্মীয় বৈধতা দেওয়ার কৌশল ছিল, বিশেষ করে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বা কংসনারায়ণের মতো জমিদারদের পক্ষে, যাঁদের সমৃদ্ধির মূলে ছিল কৃষির প্রসার।
সূত্রে পাওয়া যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ এবং প্রবোধচন্দ্র বাগচী বলছেন, সিংহবাহিনী দুর্গাকে গুপ্তযুগের পরে বাংলায় বাইরে থেকে আমদানি করা হয়, কিন্তু অন্যদের মতে এই অঞ্চলেই তাঁর উৎপত্তি। এক অর্থে দুটো মতই ঠিক, কারণ এই দুর্গার স্থানীয় বৈশিষ্ট্য আছে, আবার বহিরাগত উপকরণও আছে। কিছু কিছু দুর্গামূর্তিতে দেখা যায়, সিংহের বদলে দুর্গার বাহন হলো গোধিকা বা গোসাপের মতো একটি প্রাণী, কালকেতুর কাহিনিতে যার কথা আছে। লক্ষণীয়, গোসাপ অনেক বেশি প্রাকৃত, সিংহ সে তুলনায় সংস্কৃত প্রাণী। উনিশ শতক পর্যন্ত বাংলার পটুয়া ও চিত্রকররা সিংহকে জীবনে এই প্রাণীটিকে দেখেননি। উত্তর ভারতে আবার দেবী এখনও রয়াল বেঙ্গল টাইগারের পিঠে, ‘শেরাবালি’। সুতরাং দুর্গার রূপ নিয়েও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক মতভেদ আছে। ইন্দোনেশিয়ায় বোরোবুদুর, সুরাবায়া, বান্দুং-এর মতো কিছু জায়গায় ছয় বা আট হাত বিশিষ্ট দুর্গার দেখা মেলে। জাভার একটি লিপিতে দেখা যায় এক রাজা যুদ্ধের আগে এই দেবীর পূজা করেছিলেন। জাভায় পনেরো ও ষোলো শতকে দুর্গাকে রক্ষয়িত্রী হিসেবে আরাধনার প্রবল প্রচলন হয়।
দুর্গার সন্তানদের নিয়েও মতভেদ আছে। কুমিল্লার দক্ষিণ মুহম্মদপুরে পাওয়া একটি দ্বাদশ শতকের মূর্তিতে দুর্গার সঙ্গে গণেশ ও কার্তিক আছেন, মেয়েরা নেই। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরসীকুমার সরস্বতী এবং এনামুল হকের মতো ইতিহাসবিদরা অনেক চেষ্টা করেও চার ছেলেমেয়ে সংবলিত দুর্গার একটিও প্রাচীন ভাস্কর্য খুঁজে পাননি। দুর্গা বাপের বাড়ি আসার সময়, শুধু নিজের চার সন্তানদেরই নয়, যুদ্ধক্ষেত্র হতে রক্তাক্ত মহিষাসুরকেও সঙ্গে নিয়ে এলেন। দাশরথি রায় এবং রসিকচন্দ্র রায়ের মতো কবিরা সেই দৃশ্যের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন।
আমাদের দুর্গার অনেক নাম। শরৎঋতুতে আবাহন, তাই শারদীয়া। এছাড়া মহিষাসুরমর্দিণী, কাত্যায়নী, শিবানী, ভবানী, আদ্যাশক্তি, চণ্ডী, শতাক্ষী, দুর্গা, ঊমা, গৌরী, সতী, রুদ্রাণী, কল্যাণী, অম্বিকা, অদ্রিজা এমনই অনেক নামে তিনি পরিচিতা।
সবার উপরে, মা দুর্গা আমাদের সকল অশুভ শক্তির বিনাশ করেন।
কৃত্তিবাস ওঝা তাঁর রামায়নে লিখেছেন – রাবন ছিলেন শিব ভক্ত। মা পার্বতীই তাকে রক্ষা করতেন। ব্রহ্মা রামকে উপদেশ দিলেন শিবের স্ত্রী পার্বতীকে পূজা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে। তাতে রাবন বধ সহজ হবে। ব্রহ্মার পরামর্শে রাম শরৎকালে পার্বতীর দুর্গতিনাশিনী রূপের বোধন, চন্ডীপাঠ ও মহাপূজার আয়োজন করেন। তবে কৃত্তিবাস ওঝা তাঁর রামায়নে অকালবোধন শারদীয়া পূজার বিবরণে উদ্ধৃতি করেছিলেন, তা বাল্মিকী রামায়নে বা তুলসীদাসের হিন্দী রামচরিতমানস বা ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষায় রচিত রামায়নে তার উল্লেখ নেই।
মহালয়া বা পিতৃপক্ষের দিন সম্পর্কে মহাভারতে এক কাহিনী বর্ণিত আছে যে – মহাদাতা কর্ণের মৃত্যুর পর তাঁর আত্মা স্বর্গে গমন করলে, তাঁকে খাদ্য হিসাবে স্বর্ন ও রত্ন প্রদান করা হয়। জিজ্ঞাসা করলে ইন্দ্র কর্ণকে বলেন – তিনি সারাজীবন শুধু ধন রত্নই দান করেছেন। পিতৃগনের উদ্দেশ্যে খাদ্য ও জল প্রদান করেননি। কর্ণ উত্তর দেন তিনি পিতৃগনের সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। ইন্দ্র কর্ণকে ষোল দিন সময় দিলেন মর্তে গিয়ে পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে অন্ন ও জল প্রদান করবার জন্য। এই পক্ষই পিতৃপক্ষ নামে পরিচিত। মহালয়া পিতৃপক্ষের শেষ দিন।
পশ্চিমবঙ্গ তথা বাংলাদেশ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যায় প্রচলিত “দুর্গোৎসব” মূলতঃ কালিকাপুরাণে বর্ণিত পদ্ধতি নির্ভর, তবে বলা হয়ে থাকে যে, বাংলায় দুর্গোৎসব মূলতঃ বৃহন্নন্দীকেশ্বর পুরাণ (যার অস্তিত্ব তর্কসাপেক্ষ), কালিকা ও দেবী পুরাণে বিধৃত রীতি অনুযায়ী তিনটি ভিন্নধারায় সম্পন্ন হয়। অনেক সময় আবার মহাকাল সংহিতায় বর্ণিত পদ্ধতির কদাচিৎ অনুসরণ করা হয়, যা তান্ত্রিক দুর্গোৎসব নামে পরিচিত। পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতির জন্য অবশ্য স্মার্ত রঘুনন্দনের দুর্গোৎসবতত্ত্ব ও তিথিতত্ত্বের অনুসরণ করা হয়। তবে ক্ষেত্রবিশেষে বিদ্যাপতির দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী বা শূলপাণি রচিত দুর্গোৎসববিবেক প্রভৃতি স্মৃতিভাষ্য বা মহাকালসংহিতা/কালীবিলাস তন্ত্র বর্ণিত পদ্ধতিরও অনুসরণ করা হয়। আবার বিহারে দুর্গোৎসব মূলতঃ দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী অনুসারে নিষ্পন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুর শহরের মৃন্ময়ী মন্দির এবং অনেক পরিবারে এই রীতি প্রচলিত আছে।
কিভাবে বাঙালীদের এই উৎসব অন্যদের থেকে অন্যরকম?
সবার আগে আসে আমাদের মহিষাসুরমর্দিনী অনুষ্ঠানটি। ১৯৩২ সাল থেকে দূর্গাপূজার অঙ্গ হিসেবে মহালয়ার প্রাতে বেতারে যে মহিষাসুরমর্দিনী অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হয়, সমগ্র বিশ্বে এই ধরণের অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় উদাহরণ নেই। এখন এই বিশেষ দিনে এই অনুষ্ঠানেরই এক হিন্দী সংস্করণ একই সময়ে বাতারে সম্প্রসারিত হয়। এই বিশেষ দিনে বেতার ছাড়াও প্রতিটি টিভি চ্যানেলেও মহিষাসুরমর্দিনী অনুষ্ঠানটি নানানভাবে নিবেদন করা হয়।
২০২১ সাল বাঙালীদের দূর্গাপূজার ইতিহাসে দুটি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ন। প্রথমটি, UNESCO পশ্চিমবঙ্গের দূর্গাপূজোকে Intangible Cultural Heritage রূপে স্বীকারোক্তি দিলো। এর আগে ভারতবর্ষে শুধুমাত্র যোগা ও কুম্ভমেলাকেই এই স্বীকৃতির প্রাপক। UNESCO-র এই স্বীকৃতির কারণে পশ্চিমবঙ্গের দূর্গাপূজার কৌলীন্য অনেকটাই বেড়ে গেল। আশা করা যায় ভবিষ্যতে আরও অধিক বিদেশি পর্যটক এইসময় পশ্চিমবঙ্গে আসবেন।
On December, 2021, Durgapuja was listed as “intangible cultural asset of humanity“ by UNESCO, based on Research Documents of Topoti Guhothakurta, submitted by her, through “SANGEET, NATAK ACADEMY” to UNESCO, as advised by GOI, Cultural Ministry,- complying the UNESCO requirements.
দ্বিতীয় ঘটনাটি সামাজিক দৃষ্টিতে বৈপ্লবিক। দক্ষিন কলকাতার ৬৬ পল্লিতে মহিলা পুরোহিত দ্বারা দূর্গাপূজা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা। সহস্রাধিক বছরের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী সকলের ধারণা যে পুরুষ ব্রাহ্মন পুরোহিতরাই দূর্গাপূজা করতে পারে। এবার মহিলা পুরোহিতরাও দূর্গাপূজা করবার সামাজিক স্বীকৃতি পেলো। বলা যায় রীতি ভেঙ্গেই। এই মহিলা পুরোহিতদের পূজার পদ্ধতি অন্যরকম। এনারা সংস্কৃত নিয়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যায়ে পড়াশোনা করেছেন। চারজনের একটা দল পূজো করেন। দুজন সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারন করেন, তার ভাব ব্যাখ্যা করেন। বাকী দুজন রবিঠাকুর ও পঞ্চ কবির গান করেন। এই মহিলা পুরোহিত গোষ্ঠীর নাম শুভমস্তু। উনাদের পূজার পদ্ধতি বাংলার সমাজে খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। এখন গোষ্ঠীতে চারজন সদস্য বৃদ্ধি পেয়ে মোট ষোল জন হয়েছে। অন্যান্য কিছু পূজাকমিটিও উনাদের দিয়ে দূর্গাপূজা আনুষ্ঠানিক ভাবে করাচ্ছেন। দূর্গাপূজা ছাড়াও উনারা বৈদিক বিবাহ, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করে থাকেন।
যদি অতীতে ফিরে যাই, দেখি যে ইংরাজী শিক্ষার গুনে বৃটিশদের সময়ে বাঙ্গালীরা চাকরীসূত্রে বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়লো, সঙ্গে নিয়ে গেল দূর্গাপূজা। ভারতের বহু জায়গায় স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় সর্বজনীন পূজার শুরু হয়। মূলতঃ দেবী দুর্গাকে মাথায় রেখেই দেশমাতা বা ভারতমাতা বা মাতৃভূমির জাতীয়তাবাদী ধারণা বিপ্লবের আকার নেয়। দেবী দুর্গার ভাবনা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বন্দে মাতরম গানটি রচনা করেন। সুভাষচন্দ্র বসু, তাঁর দাদা শরৎ বোস প্রমুখ বিল্পবী ও জাতীয়তাবাদী নেতারা বিভিন্ন সর্বজনীন পূজার সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। বিপ্লবী দল অনুশীলন সমিতি দূর্গাপূজোতে লাঠি-তরোয়াল খেলার প্রচলন করেছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান কার্যালয় বেলুড় মঠের অন্যতম প্রধান উৎসব হল শারদীয়া দূর্গাপূজা । ১৯০১ সালে স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে প্রথম দূর্গাপূজা ও কুমারী পূজা করেন। সারদা দেবী এই পূজোয় উপস্থিত ছিলেন। মা দূর্গার অলংকরন – দুই রকম ভাবে মা দূর্গাকে অলংকরন করা হয়। শোলার সাজ বা ডাকের সাজ। প্রথাগত ভাবে দেবীকে সাজানো হয় শোলার সাজে। বাংলার জলাভূমিতে শোলা গাছ পাওয়া যায়। এই সাদা রংয়ের শোলা দিয়ে দেবীর মুকুট ও অলংকার তৈরি করা হয়। সময়ের সাথে সাথে যখন পূজা কমিটির বাজেট বাড়ল, রুপোর পাত বা রাংতা দিয়ে তৈরি অলংকারের প্রচলন হল। এই রুপোর পাত বা রাংতা জার্মানী থেকে আমদানী করা হত, যা পোস্ট বা ডাকের মাধ্যমে আসতো। সেই থেকে এর নাম হল ডাকের সাজ।
রবিঠাকুরের ভাগ্নি সরলা দেবী (স্বর্ণ কুমারী দেবীর মেয়ে) বীরাষ্টমী পূজার প্রচলন করেছিলেন। এই বীরাষ্টমীতে ব্যায়াম সমিতির ছেলেরা লাঠি খেলা-তরোয়াল খেলা দেখাতো। অনেক সর্বজনীন পূজোতেও বীরাষ্টমীর পূজার প্রচলন হয়েছিল। তবে মাঝখানে কয়েক বছর বৃটিশ সরকার এই প্রকাশ্যে লাঠি-তরোয়াল খেলা বন্ধ করে দিয়েছিল।
পূজার তিন-চার মাস আগে থেকেই বিভিন্ন পেশার মানুষ ব্যস্ত হয়ে যায়। কুমোর, পুরোহিত, ঢাকি, security guard, ক্যাটারিং সার্ভিস, ইত্যাদি পেশার মানুষ পূজাকমিটি থেকে বরাত পেতে শুরু করে। এছাড়া জামাকাপড়, বই- ম্যাগাজিন পাবলিশিং হাউস, ফ্যাশন, জুতো, ট্যুরিস্ট এজেন্ট, হোটেল, রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যবসায়ীরাও কয়েকমাস আগে থেকেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। চলচ্চিত্রশিল্প নির্মাতারাও ব্যস্ত হয়ে পড়েন নতুন ছবি মুক্তি যাতে পূজার সময় হয়। আর পূজার দু’আড়াই মাস আগেই বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে স্কিলড লোকজন পাড়ি দেয় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, মূলত প্যান্ডেল নির্মানকাজে। এক একটি থীম প্যান্ডেল তৈরি করতে আট দশজন লোকের লাগে দুই-আড়াই মাস।


ইতালীয়ানরা আশ্চর্য হয়ে দেখলো যে শুধু বাঁশ আর থার্মোকল দিয়েই ভ্যাটিকান প্রাসাদের অনুরুপ বানানো যায়, আরবের লোকজন দেখলো যে এক সরু গলির মধ্যেও বুর্জ খলিফার প্রায় অবিকল নকল তৈরি করা যায়। দিল্লী, মুম্বাইতে প্যান্ডেল তৈরি হয় বিভিন্ন থীমের আদলে। তেমনি ব্যাঙ্গালোর, চেন্নাই থেকে শুরু করে অপেক্ষাকৃত ছোট শহর ভাইজ্যাক, চন্ডীগড়, নাগপুরেও চোখ ধাঁধানো সব শিল্পের কাজ। বিভিন্ন সূত্র বা পত্রপত্রিকা পড়ে জানা যায় যে শুধু পূজার তিন-চার মাস সময়েই প্রায় এক লক্ষ লোক প্যান্ডেল বাঁধার কাজ করে, আর সামগ্রিকভাবে তিন লক্ষ লোকের মজুরির ব্যবস্থা হয়।

 মুদিয়ালি, কলকাতা ও তমলুকের দুটি প্যান্ডেলের ছবি
মুদিয়ালি, কলকাতা ও তমলুকের দুটি প্যান্ডেলের ছবি
প্রবাসে দূর্গাপূজার বৃদ্ধির সাথে সাথে নব্বই দশকের সময় কর্পোরেট কোম্পানীর বদান্যতায় দূর্গাপূজায় সার্বজনীন পূজার আভিজাত্য ও জাঁকজমক বৃদ্ধি পেলো। আজ ইন্টারনেটের যুগে, ভারতীয় ছাত্রদের মেধার গুনে বাঙ্গালীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছেন। তাঁরাও সঙ্গে নিয়ে গেল দূর্গাপূজা। আজ সারা বিশ্বে যে কোন ধর্মাবলম্বীর লোকজন দুর্পাপুজা সম্পর্কে অবহিত। পাশাপাশি আজ কর্পোরেট কম্পানিগুলিও বিভিন্ন পূজাকমিটিকে নানানভাবে স্পনসর করেন। ফলে দুর্গাপূজার দৌলতে কোম্পানির বানিজ্যিক পরিধি দিনদিন ক্রমবর্ধমান, তাঁরাও টাকা ঢালতে উৎসাহী। দুর্গাপুজার আরও একটি বিশেষ দিক আছে। প্রবাসের অবাঙালীরাও দুর্গাপূজার সময় বাঙালীদের সহায়তায় স্বতঃস্ফুর্ত হয়ে এগিয়ে আসেন।
পশ্চিমবঙ্গের দূর্গাপূজায় একটা অর্থনৈতিক দিকও আছে। বিভিন্ন অর্থ বিশেষজ্ঞরা বলেছেন প্রায় ষাট হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হয় পূজার তিন -চার মাসে। সংখ্যাটা বছর বছর বেড়েই চলেছে। ২০১৯ সালে ব্রিটিশ কাউন্সিল গননা করে দেখেছিল যে দূর্গাপূজার কয়েকমাসের ব্যবসাবানিজ্য পশ্চিমবঙ্গের GDP র প্রায় ২.৬ %। এখন সর্বজনীন পূজায় “থিম” বা নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক মণ্ডপ, প্রতিমা ও আলোকসজ্জার প্রবণতা দেখা যায়। থিমগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করে বিভিন্ন বানিজ্যিক সংস্থার পক্ষ থেকে “শারদ সম্মান” নামে বিশেষ পুরস্কারও দেওয়া হয়।
আমাদের প্রতিবেশী বাঙ্গালী অধ্যুষিত আসাম ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় আড়াই তিন হাজার দূর্গাপূজা হয়। দিল্লী চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীবাড়ির প্রধান পুরোহিত শ্রী মুক্তিপদবাবু প্রতি বছর আমেরিকা, বা সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া থেকে ডাক পান। মুক্তিপদবাবু একটি উদাহরণ মাত্র, ওনার মত অনেকে পুরোহিতই তখন বিদেশ পাড়ি দেন।
পূজোর এই কয়েকদিন কলকাতা নামী অনামী উঠতি গায়ক গায়িকা, বাউল গায়ক, লোকগীতি গায়ক, বড় ছোট সব ব্যান্ড এঁদের কাউকে কলকাতায় দেখা যাবে না। সব চলে যায় হিল্লী দিল্লী, আর যোগাযোগ বা হোমরাচোমরা দালালের সাথে লাইন করা থাকলে আমেরিকা ট্রিপ কে আটকায়? পাড়ার সেকেন্ড গ্রেড শিল্পী বা ব্রান্ডগুলোও এখন আমেরিকা কানাডা ট্রিপ মারে। আর যারা কোন জায়গা থেকে আমন্ত্রণ পেলেন না, তাঁরা কলকাতা বা শহরাঞ্চলের পূজো প্যান্ডেলে বিচিত্রানুষ্ঠানে নিজেদের পেশ করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। কলকাতার অনেক গায়ক-গায়িকাদের এই অনুষ্ঠানে দেখা যায়। আজকাল কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের হাউসিং কমপ্লেক্সেও এই ধরনের উৎসবের মেজাজ দেখা যায়।
পত্রপত্রিকা থেকে জানা যায় যে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই চল্লিশ হাজারেরও বেশি দূর্গাপূজা হয়। প্রবাসে রাজধানী দিল্লী ও NCR অঞ্চলে দূর্গাপূজা হয় পাঁচশোর কিছু বেশি। ১৯১১ সালে বৃটিশ সরকার যখন ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করে, অনেক বাঙ্গালী তখন চাকরী সূত্রে কলকাতা থেকে দিল্লীতে বদলী হন। দিল্লীর কাশ্মীরি গেটের সার্বজনীন পূজা ২০০৯ সালে একশো বছর পূর্ণ করেছে। দিল্লী দূর্গাপূজা সমিতি পরিচালিত এই পূজার কৌলিন্যই অন্যরকম। বহু অবাঙালী এই পূজায় নানানভাবে সহায়তা করেন।
বানিজ্যনগরী মুম্বইয়ে প্রায় একশোর বেশি দূর্গাপূজো হয়। সবথেকে পুরনো পূজো প্রায় ৭৫ বছর আগে শুরু হয়েছিল। কলকাতায় যেমন সার্বজনীন, বম্বেতে পূজোর নামে ট্যাগ করা থাকতো। যেমন নর্থ বম্বে সর্বজনীন দূর্গোৎসবের প্রচলন করেছিলেন বম্বের হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের প্রযোজক পরিচালক শশধর মূখার্জী। চেম্বুরে অশোককুমার। সম্প্রতি গায়ক অভিজিতের পূজোয় বেশ জাঁকজমক হয়। মুখার্জী পরিবারের পুজো এখন জুহুর তুলিপ স্টার হোটেলে হয়ে থাকে। ভোগ প্রসাদ বিতরনের সময় মুখার্জী পরিবারের লোকেরাও অংশ গ্রহন করে। আজকাল রানী মুখার্জী ও কাজলকেও ভোগ প্রসাদ বিতরণ করতে দেখা যায়। অনেক চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব এই পূজায় অংশ গ্রহন করেন। আরেকটি প্রাচীন দূর্গাপূজা ৭৫ বছর আগে সমসাময়িক সময় শুরু হয়েছিল সান্তাক্রূজে। এই পূজার পরিচালনা করে বঙ্গ মৈত্রী সংঘ। প্রবাসের পূজোতে দুপুরের ভোগ খাওয়া এক মধুর অভিজ্ঞতা। প্রত্যেক পূজোতে চার দিনে খিচুড়ি ভোগ খাবার ব্যবস্থা থাকে। পূজার চারদিন বাড়ীতে প্রায় রান্না হয়না। দিনের বেলায় পূজামন্ডপে খিচুড়ি ভোগ খাওয়া আর রাত্রিবেলায় বিভিন্ন স্টলে খাবার কিনে খাওয়া।
 এছাড়া বেলুড় মঠ সহ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘের বিভিন্ন কেন্দ্রের সন্ন্যাসীরা দুর্গাপূজার আয়োজন করেন।
এছাড়া বেলুড় মঠ সহ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘের বিভিন্ন কেন্দ্রের সন্ন্যাসীরা দুর্গাপূজার আয়োজন করেন।

ঢাকার রামকৃষ্ণ আশ্রমের পুজোও বেশ বিখ্যাত। ১৮৯৯ সালে প্রতিষ্ঠা হয় এই আশ্রম। এখানকার পুজোর মূল আকর্ষণ কুমারী পুজো।
প্রতিবেশী বাংলাদেশেও হিন্দুদের সবচেয় বড় উৎসব দূর্গাপূজা। বিগত ২০২২ সালে বাংলাদেশে ৩২ হাজার দূর্গাপূজা হয়েছে। ঢাকার রমনা কালীবাড়ির দূর্গাপূজা ও ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের দূর্গাপূজা খুব বিখ্যাত।
বাংলাদেশে দুর্গাপুজোর ইতিহাস অতি প্রাচীন। বাংলাদেশের দুর্গাপুজো নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই উঠে আসে রাজধানী ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দিরের দুর্গাপুজোর কথা। যা আদতে প্রায় আট শতাব্দী পুরনো। এটি বাংলাদেশের ‘জাতীয় মন্দির’ও বটে। এই মন্দিরে প্রথম দিকে অষ্টভুজার প্রতিমা এবং পরবর্তী সময়ে দশভুজা দুর্গা প্রতিমা স্থাপন করা হয়েছিল। জানা যায়, রাজা বল্লাল সেন এক সময়ে বুড়িগঙ্গার নদীর তীরে জঙ্গলে মা দুর্গার একটি মূর্তি খুঁজে পান। সেই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে দুর্গাপুজোর প্রচলন করেন তিনি। সেই থেকেই এই মন্দিরের নাম ঢাকেশ্বরী মন্দির। ঐতিহাসিকদের মতে, ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পূজিতা দুর্গার আরেক রূপ দেবী ঢাকেশ্বরীর নাম অনুসারেই ঢাকা শহরের নামকরণ করা হয়। মুঘল সম্রাট আকবরের সেনাপতি মান সিংহ চারটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এখানে।
তাহিরপুর রাজবংশের রাজা ছিলেন ইতিহাসখ্যাত কংস নারায়ণ রায়। ৮৮৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসের মহাষষ্ঠী তিথিতে অকালবোধনের মাধ্যমে কংস নারায়ণ দেবী দুর্গার প্রতিমা গড়ে প্রথম দুর্গাপূজা করেন। কংস নারায়ণের প্রথম দুর্গাপূজাটি হয়েছিল রাজবাড়ি সংলগ্ন প্রধান ফটকের পাশেই একটি বেদীতে। দেবী দুর্গার সমস্ত গহনা করা হয়েছিল স্বর্ণ ও মনি-মুক্তা দিয়ে। এর পাশেই তিনি নির্মাণ করেন প্রথম দুর্গা মন্দির। রাজপ্রথা বিলুপ্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত ওই মন্দিরে দুর্গাপুজা হত।
১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের হানাদাররা রমনা কালী মন্দির ধ্বংস করে দিয়েছিল। তার পর থেকে এখানে কোনও স্থায়ী মন্দির স্থাপিত না হলেও মণ্ডপ গড়ে পুজো হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে হওয়ায় মূলত ছাত্রছাত্রীদের ভিড়ই বেশি এখানে।
এছাড়াও ছিল ব্যবসায়ী নন্দলাল বাবুর মৈসুন্ডির বাড়ির দুর্গাপুজো। সিপাহী বিদ্রোহের কয়েক দশক আগে ১৮৩০সালে পুরনো ঢাকার সূত্রাপুর অঞ্চলের আয়োজিত হয়েছিল তৎকালীন ঢাকার সবচেয়ে বড় দুর্গাপুজো। ছিল তিনশো বছরের পুরনো শ্রীহট্টের রাজনগর উপজেলার পাঁচগাঁওয়ের দুর্গাপুজো। প্রতিমার গায়ের রঙের জন্য বিখ্যাত ছিল এই পুজো। দেশ-বিদেশ থেকে বহু দর্শনার্থী আসতেন এই পুজো দেখতে। এরপর বিংশ শতকের শুরুতে বাংলাদেশে দুর্গাপুজো সমাজের বিত্তশালী এবং অভিজাত হিন্দু পরিবারদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। গত শতাব্দীর শেষের দিকে এবং এই শতাব্দীর শুরুর দিকে বাংলাদেশের দুর্গাপুজো তার সর্বজনীন রূপ পায়।
ঐতিহ্যের চর্চা হলে পুরনো ঢাকার শাঁখারিবাজারের দুর্গাপুজো পুরনো ঢাকার মূল আকর্ষণ। শাঁখা, পলা-সহ হরেক মণিহারী সামগ্রীর দোকান রয়েছে এখানে। মোট ন’টি পুজো হয় শাঁখারিবাজারে। প্রতিটি পুজো ৪০ বা ৫০ বছরের পুরনো। এখানকার বেশ কিছু বাড়িতেও দুর্গাপুজো হয়।
বাংলাদেশে সাধারণত থিম পুজো হয় না। তবে বাগেরহাট জেলার শিকদার বাড়িতে থিম পুজোর চল রয়েছে। ২০১০ সালে এই পরিবারের তরফে লিটন শিকদার নামে এক ব্যবসায়ী ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই পুজো শুরু করেন। পুজোর থিমে প্রতি বছর তুলে ধরা হয় নানা পৌরাণিক কাহিনি।
দূর্গাপূজোয় শোক পালন!
দুর্গাপূজার পাশাপাশি আদিবাসীরা মহিষাসুরকে দেবতা রূপে পূজো করে। অনার্যদের যুদ্ধে হারিয়ে আর্যরা যখন ভারতবর্ষে নিজেদের বাসস্থান তৈরি করে, তখন অনার্যরা প্রত্যন্ত অঞ্চলের বনে জঙ্গলে নিজেদের স্থানান্তরিত করে। ঐতিহাসিকদের মতে আর্যরা সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন। রামকে আর্যদের প্রতিনিধি ও দেবতা হিসাবে গন্য করা হয়। আর আদিবাসীদের রাক্ষস, দৈত্য রূপে বর্ননা করা হয়।মহিষাসুর ছিলেন অনার্যদের রাজা। অনেকের মতে আজকের আদিবাসীরাই সেই অনার্যদের বংশধর। বাংলার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে, ঝাড়খণ্ড,মধ্য প্রদেশ, ছত্রিশগড় ইত্যাদি বেশ কিছু অঞ্চলে আদিবাসিরা দাঁশায় উৎসব পালন করেন। আদিবাসীরা রঙ্গিন শাড়ি-ধুতি, জামা-গেঞ্জি, মাথায় পাখির পালক গুজে মাদল, করতাল, বাঁশি সহযোগে নাচ আর গানের মাধ্যমে চলে শোকের প্রকাশ।
কলকাতায় দূর্গাপূজার প্রচলন
খুব সম্ভবত কলকাতায় প্রথম দূর্গাপূজা হয় বেহালার জমিদার সাবর্ন রায়চৌধুরীর বাড়ীতে ১৬১০ সালে। তাঁরা জমিদারপুত্রের আদলে কার্তিকেয়র রূপ দেন, যা ইতিপূর্বে ছিলো সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের আদলে যুদ্ধের দেবতারূপ। তবে দূর্গাপূজার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় ১৭৫৭ সালে যখন রাজা নবকৃষ্ণ দেব উত্তর কলকাতার শোভাবাজার বাড়িতে দূর্গাপূজা শুরু করেন। এটা কোম্পানির পূজা নামেও বিখ্যাত ছিল। এই নিয়ে এক গল্প আছে। পলাশীর যুদ্ধে কিছু বাঙ্গালী রাজা ও জমিদার সিরাজদৌল্লার বিরুদ্ধে লর্ড ক্লাইভকে সমর্থন করেন। এদের মধ্যে রাজা নবকৃষ্ণ দেবও ছিলেন। যুদ্ধে জেতার পর লর্ড ক্লাইভ Thanks giving ceremony করতে চাইলেন। উদ্দেশ্য যারা তাকে সাহায্য করেছে, তাদের সন্মান জানানো। এর জন্য উনি উপযুক্ত জায়গা খুজে পাচ্ছেন না। একবছর আগে সিরাজদৌল্লার সৈন্যরা ইংরেজদের একমাত্র গীর্জাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। রাজা নবকৃষ্ণদেব ঠিক করলেন তিনি দূর্গাপূজা শুরু করবেন যেখানে Thanks giving ceremony র আয়োজন করা যাবে। লর্ড ক্লাইভ রাজি হলেন। পূজোতে এলাহী আয়োজন হলো। ইংরেজদের খুশি করতে মদ-মাংস- বাইজী নাচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।
পরিবেশ দূষণ
কলকাতা শহরে প্রায় তিন হাজার দূর্গাপূজা হয়। দশমীর দিন হাজার হাজার মূর্তি গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়। যে সমস্ত কাঁচা মাল দিয়ে মূর্তি বানানো হয়, অধিকাংশই biodegradable। যেমন খড়, মাটি, কাঠ ইত্যাদি। অনেক জায়গায় মাটির বদলে প্লাস্টার অফ প্যারিস ( POP) ব্যবহার করা হয়। এটা জলজ প্রানী ও গাছের পক্ষে ক্ষতিকর। এছাড়া প্রতিমাকে আরো উজ্জ্বল দেখাবার জন্য বিশেষ ধরনের paint ব্যবহার করা হয়। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে এই হেভি মেটাল (যেমন lead বা শীষা) জলের পরিবেশকে ক্ষতি করে। মাছ, জলজ প্রানী ও জলজ গাছের জীবনের ক্ষতি করে। এছাড়া হেভিমেটাল জমে জমে জলের সাধারন স্রোত বন্ধ করে কাদার স্তর তৈরি করে। কলকাতা কর্পোরেশন কয়েক বছর ধরে ক্রেনের সাহায্যে তাড়াতাড়ি বিসর্জনের মূর্তিকে জলের বাইরে নিয়ে আসে। এতে জলের দূষণ কম হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিবেশ ক্ষতিকারক রং বেআইনি করে দিয়েছে ও শীষামুক্ত রং প্রতিমা শিল্পীদের বিনা পয়সায় সরবরাহ করছে।
পরিসংহার-
মানুষের দিনগত ঘাত প্রতিঘাতের জীবনে উৎসবের প্রয়োজন আছে। উৎসবের কয়েক দিন মানুষ পরিবার ও বন্ধু-বান্ধব মিলে আনন্দে কয়েকটা দিন কাটায়। সমস্ত দেশেই উৎসব আছে আনন্দ আছে। আমাদের দেশেরই অন্য এক প্রদেশ মহারাষ্ট্রে গণেশ পূজা মারাঠীদের সবচেয়ে বড় উৎসব। বাড়ী ও সর্বজনীন মিলিয়ে হাজার হাজার পূজা হয়। ১০ দিনের উৎসব । বৃটিশদের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে সর্বজনীন উৎসবের প্রসার ঘটে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। বাল গঙ্গাধর তিলকের উৎসাহে মহারাষ্ট্রের পাড়ায় পাড়ায় সর্বজনীন গনপতি উৎসবের প্রচলন ঘটে। অফিস – কাচারিতে দুদিন ছুটি থাকে প্রথম ও শেষে বিসর্জনের দিন। মানুষজন সারাদিন কাজকর্ম অফিস করে সন্ধের পর সেজেগুজে পূজামন্ডপে প্রতিমা দেখতে যায় ও আনন্দে মেতে ওঠে। কাজ ও উৎসব দুটোই সমান গুরুত্ব সহকারে পালন করা হয়। পশ্চিম বঙ্গে উৎসবের আধিক্য বেশি। এই সময়ে অফিস-কাচারিতে কর্মসংস্কৃতির বিরূপ প্রভাব পরে। এই নিয়ে চিন্তাভাবনার সময় এসেছে।
কাজ ও উৎসবের সামঞ্জস্যই মানুষকে সমাজ ও দেশের প্রতি দায়িত্ববান হতে শেখায়।
*****
১) তথ্য সংগ্রহ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার – উইকিপিডিয়া ।




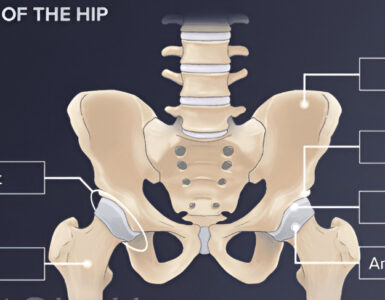











Add comment