দেশে-বিদেশে নারীবাদ
ডঃ শকুন্তলা চৌধুরী, প্রফেসর অনিল চৌধুরীর কন্যা
‘নারীবাদের’ কি স্বদেশ বিদেশ আছে? অনেকে হয়তো বলবেন – ‘নেই’; আমি বলব – ‘আছে’। কেন এ’কথা বলছি সেটা বোঝাতে গেলে একটু বিশদে বলতে হবে।
‘নারীবাদ’ কথাটার আক্ষরিক অর্থ হল ‘মানুষ হিসাবে (এবং পুরুষের তুলনায়) নারীর সর্বাঙ্গীণ সমতা ও স্বাধীনতায় বিশ্বাস করা’। মূলত বিংশ শতাব্দী থেকে এটা আন্দোলন হিসাবে শুরু হলেও, নারীর ভূমিকা এবং স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা বহুদিনের। সময়ের সঙ্গে নারীর ভূমিকা পাল্টেছে, সব দেশেই।
কিন্তু কিছু কি রয়ে গেছে, যা আজও দেশিক সীমানায় আবদ্ধ? সময়-সম্পর্কিত নয়?
পৃথিবীর দুই প্রান্তে — প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই বৃহৎ গণতন্ত্রে — জীবনের প্রায় সমান সমান সময় কাটিয়ে, আজ সেই বিশ্লেষণটা যেন মনে হচ্ছে অপরিহার্য।
গত শতাব্দীর শেষভাগে, আমার কলকাতার ছাত্রীজীবনে, আমি একবার নারীস্বাধীনতা নিয়ে খুব ধারালো প্রশ্নোত্তরের মুখোমুখী হয়েছিলাম। প্রশ্নকর্তা কোনো সংবাদপত্রের হয়ে ইন্টারভিউ করছিলেন।
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ তখন সরগরম সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদের আলোচনায়।
বামপন্থী রাজত্বে ‘আমরা সবাই রাজা’র স্লোগান জোরদার — হিন্দু-মুসলিম, ধনী-দরিদ্র, বাঙালী-শিখ, পুরুষ-নারী, সবাই একই জয়রথের যাত্রী। কলকাতার রাস্তায় মেয়েরা তখন নিশ্চিন্তে হাঁটছে এবং ছেলেদের সঙ্গে সমান অধিকারে মিটিং-মিছিলে যোগ দিচ্ছে।
এমন সময় এই প্রশ্ন।
আমি তাকে বলেছিলাম যে – “আমি নিজেকে আমার ঠাকুমা বা দিদিমার থেকে এতো বেশী প্রিভিলেজড্ বলে জানি যে, আজকের যুগে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র নারীস্বাধীনতা নিয়ে অভিযোগ জানাতে আমার লজ্জা করে। সমস্যাটা বোধহয় আরও গভীরে — সামাজিক কুশিক্ষা-অশিক্ষার মধ্যেই থেকে যায় নারীর প্রতি অসম্মানের বীজ, আর তাতে পরোক্ষে যোগ দেয় নারী নিজেই। স্বাধীনতার মানে বুঝতে হবে, স্বাধীনতার যোগ্য হতে হবে — নাহলে শুধু নারীবাদী আন্দোলনে গলা মিলিয়ে লাভ হবে কি? সে স্বাধীনতা সামলাবে কে? সামলাবে কি করে? আসলে সব ‘অবদমিত’ মানুষেরই প্রয়োজন স্বাধীনতার মানে বুঝে তারপর স্বাধীনতা অর্জন করা।” আমার উত্তরটি প্রশ্নকর্তার মনঃপুত হয়নি, সুতরাং তিনি আমাকে ‘প্রিভিলেজড্ ক্লাসে বিলং করা আহ্লাদী কন্যা’ ভেবে একটি তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি প্রদান করেছিলেন এবং কয়েকটি তির্যক মন্তব্য ছেড়েছিলেন।
আসলে যেটা তাঁকে আমি বলতে চেয়েছিলাম সেটা হল এই যে, নারী স্বাধীনতার কোনো চীৎকৃত আন্দোলনে আমি বিশ্বাস করিনা। তার কোনো প্রয়োজনও দেখি না। শিশু যখন হাঁটতে শিখে যায়, তখন তার হাত ধরে থাকা মানে তাকে সাহায্য করা নয় — পরনির্ভর করে রাখা। পৃথিবীর যেখানেই আজ ব্যক্তিস্বাধীনতা আছে, সেখানেই নারী আজ হাঁটতে শিখে গেছে। এবারে পথ তাকে নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে। নিজের ছন্দে, নিজের মতো করে, নিজের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে —“ওয়ান সাইজ ফিটস্ অল্” কথাটা আর যেখানেই খাটুক্ না কেন, এখানে নয়। তার মানে কিন্তু এই নয় যে পিছিয়ে থাকা মেয়েদের সাহায্য করতে কেউ হাত বাড়াবে না, নারীর (বা যে কোনো ‘অবদমিত’ মানুষের) সমান অধিকারের দাবীতে সংসদে কেউ বিল আনবেনা।
‘পিছিয়ে থাকা’ সমাজকে, নারী-পুরুষ যেই হোক্ না কেন, টেনে তোলার দায়িত্ব হচ্ছে ‘এগিয়ে থাকা’ সমাজের। কিন্তু তার জন্যে মাইক নিয়ে নারীবাদী বক্তৃতা করার প্রয়োজন আছে কি? এই অতি-উৎসাহের প্লাবনে অনেকসময় লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশী হয়। বিপ্লবের আগুন জ্বালান যত সোজা, সেই আগুনে মশাল জ্বেলে পথের দিশারী হওয়া ঠিক তত সোজা নয়।
ছোটবেলায় আমাদের বাড়ীতে কাজ করতে আসতো মেনকাদি’ — তাকে নাকি তার স্বামী ‘নেয় না’। বড়ো হতে হতে আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে আসলে মেনকাদি’ই তার স্বামীকে আর নেয় না। মেনকাদি’র মাতাল স্বামী যখন কন্যাসন্তান জন্মের দোষ মেনকাদি’র ওপর চাপিয়ে মেনকাদি’কে কিল-চড় মেরে হাতের সুখ করত, আশেপাশের কোনো পুরুষ বা নারী তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি — সে নিজেই নিজেকে সাহায্য করেছিল। সহ্যের বাঁধ ভেঙে যাওয়ার পর, একদিন হাতের খুন্তি স্বামীর কপালে ছুঁড়ে মেরে শ্বশুরবাড়ী ছেড়েছিল মেনকাদি’। বাপের বাড়ীর ওপরে বোঝা না হয়ে, সে খেটে খেতে শহরে এসেছিল এবং লোকের বাড়ী বাসন মেজে সেই কন্যাসন্তানকে কলেজ পড়িয়ে অফিসের চাকরিতে ঢুকিয়েছিল। এতো বড়ো বিপ্লবটা মেনকাদি’ কিন্তু একাই করেছিল, কোনো সংবাদপত্র তার খবরও রাখেনি।
আমার মা সেই যুগে অনার্স নিয়ে বি এস সি পাশ করেছিলেন, সঙ্গে দক্ষিণীর থেকে পাওয়া ডিগ্রী এবং অপূর্ব গানের গলা। গান রেকর্ড করার আমন্ত্রণ এসেছিল, একটি স্কুলে পড়ানোর সুযোগও এসেছিল। মেয়েরা তখন কাজ করতে নামছে, আমাদের সেই ক্যাম্পাসটাউনের ‘অণু’ পরিবারে আপত্তি করারও কেউ ছিল না। অথচ আমার বাবার উৎসাহ থাকা সত্ত্বেও, মা সেইসব সুযোগ দু’হাতে ঠেলে ফেলে বেছে নিয়েছিলেন তিনটি শিশুকে বড়ো করা এবং ‘মানুষ হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখানোর’ মতো কাজ — যার আপাতদৃষ্টিতে কোনো ব্যবহারিক মূল্য নেই। বাবা ছিলেন পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত — খোলা মনের এবং শান্ত স্বভাবের মানুষ। মা সর্বতোভাবেই ছিলেন স্বাধীন — কিন্তু তাঁর স্বাধীনতার প্রকাশটা ছিল অন্যরকম। মা আমাদের পড়াতেন, গানও গাইতেন। পড়তে পড়তে, খেলতে খেলতে, শোনা সেই গান আমার ভেতরে আজও নির্ভুল সুরে বেজে ওঠে।
তাই বলছিলাম যে ‘স্বাধীনতা’ কথাটার মানে সব নারীর কাছে এক নয় এবং পারিপার্শ্বিককে বাদ দিয়ে কোনো স্বাধীনতাই অর্থবহ হয় না। অতএব (পাশ্চাত্যের থেকে) আমদানী করা কিছু নারীবাদী বক্তৃতা তুলে এনে সব নারীর মুখে বসিয়ে দিলে, কোথাও না কোথাও তাল কাটতে বাধ্য। কারণ স্বাধীনতার ঐ বক্তৃতাগুলো ‘আরোপিত’, নিজের ভেতর থেকে ‘উদ্ভুত’ নয় এবং পারিপার্শ্বিকের সঙ্গেও সর্বদা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সবচেয়ে বড় কথা এই যে পারিপার্শ্বিককে তৈরী করার কথাই কেউ তুলছেন না – এমন পারিপার্শ্বিক যেখানে সমাজের প্রতিটি স্তরে এবং শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিফলিত হবে নারীর (এবং সমস্ত মানুষের) প্রতি সম্মান, যা দেখে শিশুরা বড়ো হবে। ফলস্বরূপ, অনেক ক্ষেত্রেই ভারতীয় নারীবাদের সামাজিক রূপটি হয়ে দাঁড়াচ্ছে একটি ‘হযবরল’, বা ‘দ্বৈতবাদ’ – যেখানে সমাজের এক অংশে থেকে যাচ্ছেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশ অফিসার কিরণ বেদী আর আরেক অংশে ছয় বছরের ধর্ষিতা বালিকা চৈত্রা।
একটা কথা ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে খুব গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার।
স্বাধীনতার দ্বিতীয় দশক পূর্ণ হওয়ার আগেই যে দেশ মহিলা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করার দৃষ্টান্ত রাখল পৃথিবীর সামনে, সেই দেশেই স্বাধীনতার ৪০/৫০/৬০ বছর পরেও আমরা প্রত্যক্ষ করি দেবযানী বণিক, নির্ভয়া, লক্ষ্মী আগরওয়ালকে — সংবাদমাধ্যম ভরে থাকে ধর্ষণ আর বধূনির্যাতনের খবরে, আজও। সমাজের প্রতিটি স্তরেই একই ব্যাপার — প্রিভিলেজড্ বা আনপ্রিভিলেজড্ ক্লাসের মধ্যে সেখানে খুব বেশী তফাত আছে বলে মনে হয় না। অথচ নারীবাদী কর্মযজ্ঞ, সভা-সমিতির তো বিরাম নেই!
গণ্ডগোলটা তাহলে ঠিক কোথায়? এটা কি শুধুই সংযোগের অভাব — একটা ধাপ থেকে পরের ধাপে যাওয়ার সূত্র ছিন্ন হওয়ার সমস্যা? নাকি, ভারতীয় সমাজের মূলেই আছে কিছু বৈষম্য যা আপাতবিরোধী সামাজিক কাঠামোর মাধ্যমে ঢুকে পড়ছে ঘরে ঘরে?
দেশের ছাত্রজীবন শেষ করে যখন বিদেশে এলাম, এই প্রশ্নটা তখন আমাকে আরও বেশী করে ভাবিয়েছে।
পাশ্চাত্যে, বাহ্যত, নারী-পুরুষের সমানাধিকার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো স্বাভাবিক।
আমার প্রফেসর জনকে দেখতাম বাড়ীতে নিয়মিত রান্না করত, আমাদের নেমন্তন্ন করে ‘চিকেন টেরিয়াকী’ খাওয়াত। স্ত্রী মেরী সব জোগাড় করে দিয়ে, হাসতে হাসতে জনের গলা জড়িয়ে ধরে বলত – “আয়াম্ সো ব্যাড এ্যাট কুকিং, রাইট হনি? ইফ জন হ্যাজ এ্যান ইভনিং ক্লাস, আই জাস্ট অর্ডার পিৎজা।”
আমাদের স্টুডেন্ট এ্যাপার্টমেন্টের প্রতিবেশী লিজ-ও তাই বলত — ও রাঁধতে পারে না, ওর স্বামীই বাড়ীর রাঁধুনী। লিজ ঘর পরিস্কার করে, বাসন ধোয়।
কাজের লোক বলে এ’দেশে কিছু নেই। স্বামী-স্ত্রী দু’জনেই বাইরে কাজ করছে, আবার ঘরে এসেও যে যার সুবিধা মতো কাজ ভাগ করে নিচ্ছে। তাতে লজ্জা পাওয়ারও কিছু নেই, দোষেরও কিছু নেই।
তবে, আমেরিকাতে চাকরি শুরু করার পর দেখেছি যে বৈষম্যও আছে — কর্পোরেট অফিসের বেশীরভাগ চাকরিতেই মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে কম মাইনে পায়। আমেরিকাতে আজ পর্যন্ত কোনো মহিলা প্রেসিডন্ট নির্বাচিত হননি, প্রথম মহিলা ভাইস-প্রেসিডন্ট নির্বাচিত হলেন ২০২০ সালের নির্বাচনে। তাই নিয়ে আলোচনা এবং আন্দোলনও চলে, কিন্তু প্রকাশ্যে নারীকে ‘দ্বিতীয় সারি’তে বসিয়ে নগ্ন উল্লাসে জয়ধ্বনি দেওয়ার কথা কেউ ভাবে না। যেমন এক সন্তানের জন্মের পর মেরী যখন “ব্যক্তিত্বের অমিল” বলে জনকে ডিভোর্স করে চলে যায়, তখন তাকে ছি-ছি করার কথাও কেউ ভাবে না। মিল হয়নি, চলে গেছে। পাশ্চাত্য মতে, সেই অধিকার জীবনের যে কোনো পর্যায়ে পুরুষ বা নারী দু’জনেরই আছে। সন্তানের মতামত, বা মানসিক অবস্থা, প্রাথমিক বিচার্য বিষয় নয়। আর বাকীদের তো মতামত দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।
আমার মতে, অধিকার দু’তরফেরই সমান হওয়া উচিত তবে দায়িত্ববোধ ছাড়া অধিকার সম্পূর্ণ হয় না আর কোনো অধিকারেরই অপপ্রয়োগ করতে নেই। সেটা পুরুষ এবং নারী দু’জনের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। “ব্যক্তিত্বের অমিল”-এর মতো একটা কারণে, ‘লাভ ম্যারেজে’র পাঁচবছর পরে এবং সন্তান জন্মের পরে, বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার প্রয়োগ করে দীর্ঘকালীন সুখ কেনা যায় কিনা জানি না — তবে তাৎক্ষণিক স্বাধীনতা যে কেনা যায় সেটা দেখেছি বা দেখছি। এদেশেও, এবং অধুনা ভারতবর্ষেও। তবে ভারতবর্ষে দোষটা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এখনও নারীর ওপরেই এসে পড়ে, বাঁকা দৃষ্টিটাও — যেটা পাশ্চাত্যে কখনো দেখিনি।…
কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা হল এই যে, (আমদানী-করা) এই ‘স্বাধীনতা’ কি সব দেশের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? নাকি, তাল কাটছে কিন্তু স্বাধীনতার স্লোগানে সব চাপা পড়ে যাচ্ছে? সব আগুনই কি আলো জ্বালছে?
পাশ্চাত্যে এসে এও দেখলাম যে ধর্ষণ বা বধূহত্যা এখানে হয়, কিন্তু তার ধরণটা আলাদা। ‘ডেট’ করতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার হওয়া, আর চলন্ত বাসে বা প্রকাশ্য গ্রামের রাস্তায় গণধর্ষণের পৈশাচিক উল্লাসের শীৎকার শোনার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত আছে। ঠিক তেমনি, অবৈবাহিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া স্ত্রীকে হত্যা করে স্বামী হয়তো এখানে কোনো ন্যাশনাল পার্কের মাটিতে পুঁতে রাখছে — কিন্তু পণের টাকা দিতে না পারার অপরাধে বাড়ীর বৌকে সপরিবারে পিটিয়ে হত্যা করে নিশ্চিন্তে বসে আমোদপ্রমোদ করছে কি?…
অপরাধ দু’জায়গাতেই হচ্ছে, কিন্তু একজায়গায় যেন অপরাধের সঙ্গে মিশে আছে অপমান। কেন?
যে দেশে নারীকে শক্তিরূপে পূজো করা হয়, সেদেশে নারীর এতো অপমান কেন? আবার মনে হয় — কেন এই সংযোগের অভাব? কোথায় ছিন্ন হয়েছে সূত্র?
পশ্চিমের দেশগুলোতেও নারীর প্রতি বৈষম্য আছে, কিন্তু পরিশীলিত এবং চাপা।
নারীর বিরুদ্ধে অপরাধও হয়, কিন্তু অসম্মানটা কম। কেন?
তবে কি সত্যিই আমাদের দেশে নারীস্বাধীনতা এখনও তার শৈশবেই আটকে আছে? ভারতীয় নারী কি সত্যিই পুরুষের মনে আজও একটি ‘গৃহপালিত পরাধীন জীব’, যাকে নিয়ে যা খুশী তাই করা যায়? নাকি বেশীরভাগ ভারতীয় নারী নিজেই জানে না যে তার ঠিক কতটুকু সম্মান প্রাপ্য বা কতটা অধিকার আছে? যে চাইতেই জানে না, তার পাওয়ার ভাগে সব সময়ই কম পড়ে। আর যে জানে, যেমন আমার ছোটবেলার মেনকাদি’, তাকে কেউ চিরকাল ‘পরাধীন’ করে বেঁধে মারতে পারে না।
আসলে স্বাধীনতা দান করার জিনিস নয়, তাকে অর্জন করতে হয়।…
আমরা তবে কাকে দোষ দেব? কোথায় খুঁজব সংযোগের অভাব? কোথা থেকে শুরু করব আমাদের নারীবাদ?
ছোটবেলায় মহিলামহলের আলোচনায় শোনা অনেক কথা এখনো স্মৃতিতে আটকে আছে —
“অমুকের বৌ খুব ভালো হয়েছে – সাত চড়ে রা কাড়ে না; ঐ মেয়ের বড়ো তেজ – স্বামী কেন মদ খেয়ে বাড়ী ঢোকে…আরে, তবু তো বাড়ী ঢুকছে…’সোনার আংটি আবার বাঁকা’; ঐ তো কালো মেয়ে – অনেক জন্মের পূণ্যে অমন ফরসা স্বামী পেয়েছে; তমুকের মেয়ে তো পড়াশোনা করতে করতে বুড়ো হয়ে গেল – আবার বলে নাকি পি এইচ ডি করবে…বিদ্যেধরীকে তখন নেবে কে, ঐ তো চেহারা…থাকবে খুঁটি হয়ে বসে বাপের ঘরে; পরীক্ষা আছে তো কি, শুকনো জামা ভাঁজ করে পড়তে বসতে বলেছি মেয়েকে – ছেলে তো আর নয় যে ঘরের কাজ না শিখলেও চলবে; অমুকের বৌ-এর আবার মেয়ে হয়েছে – এই নিয়ে তিনবারের চেষ্টা, তাও ছেলে হল না…খুব মন খারাপ; তমুকের ছেলেটা একদম বৌ-ভেরুয়া, ছুটির দিন হলেই বৌ নিয়ে চলল সিনেমায়…” ইত্যাদি ইত্যাদি।
যাঁরা ওগুলো বলতেন, তাঁরা সবাই কিন্তু তথাকথিত প্রিভিলেজড্ ক্লাসের শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। কিন্তু তাঁদের মনে স্বজাতির জন্য ঐটুকুই সম্মান ছিল। হয়তো বা এখনো তাই আছে! মেয়েকে তাঁরা সযত্নে শিখিয়েছেন যে বিয়ের পর স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ীর প্রতি তার কি কর্তব্য, কিন্তু ছেলেকে কোনদিন শেখাননি যে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ী এবং বৌয়ের প্রতি তার কি কর্তব্য। শুধু বিয়ের পরে কেন, তার আগেও মেয়েদের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটা কি কোনদিন শেখানো হয়েছে আমাদের দেশের ছেলেদের — কথায় বা কাজে? শুধু মা নয়, প্রতিটি মেয়েই যে সম্মানের যোগ্য — এটা কি ছেলেদের শেখানো হয়, না তারা আশেপাশে দেখতে পায়? শাড়ী ছেড়ে জিনস্ বা স্কার্ট তো পরেছে মেয়ে, কিন্তু সমাজের সম্মান কি সে পাচ্ছে? না পাচ্ছে শুধু সমালোচনা? শুনছে যে তার ‘উগ্র সাজপোশাক’ই কারণ যে সে ধর্ষণের শিকার হচ্ছে!
আর ‘বৌ-ভেরুয়া’ শব্দটার মতো একটা অশ্লীল, বৈষম্যমূলক বিশেষণ যে কি করে সমাজে এখনও চলছে ভাবলে অবাক লাগে; আশ্চর্যের কথা এই যে শব্দটার কোনো স্ত্রীলিঙ্গ নেই! ‘বর-ভেরুয়া’ বলে কোনো শব্দই নেই বাংলা অভিধানে!
এইরকম প্রেক্ষাপটে বড়ো হওয়া শতকরা নব্বই ভাগ মানুষের মনে, নারীর জন্য ‘দ্বিতীয় সারি’র আসন ছাড়া আর কিছু থাকতে পারে কি? সেই মানুষ ছেলে হলে, সে নারীকে সম্মান দেবে না। বৌয়ের কথায় বা বৌকে খুশী করতে, কিছু করার আগে ভাববে — ‘আমাকে লোকে বৌ-ভেরুয়া বলবে না তো!’ আর মেয়ে হলে, সে সম্মান দাবী করবে না — বাইরে নারীস্বাধীনতার সভায় যোগ দিয়ে, ঘরে এসে ‘দোষী’ মন নিয়ে রান্না করতে ঢুকবে…স্বামীকে বলবেই না যে ‘আমি আজকে কাজে ব্যস্ত, তুমি রান্নাটা করে নিও’। সে হয়তো বা নিজেই কন্যার বদলে পুত্রসন্তান কামনা করবে, যাতে সংসার খুশী থাকে…আর সে নিজেও।
বিদেশে এসে প্রথম দেখেছিলাম যে মেয়ে হলে ঘর গোলাপী রঙে সাজান হয়, ছেলে হলে নীল রঙে — না আছে রঙের গাঢ়তায় তফাত, না আছে আনন্দের প্রকাশে তফাত।
ছেলে-মেয়ে বড়োও হয়ে উঠছে একইভাবে।
১৮ বছরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে নিজেদের জীবন শুরু করে এরা — প্রথমে আবাসিক কলেজে, তারপর কর্মস্থলে। তার প্রস্তুতি হিসাবে, ছেলে মেয়ে সবাই এখানে ছোট থেকেই কয়েকটা জিনিস শিখে রাখে — বাজার করা, রান্না করা, ঘর পরিস্কার করা, গাড়ী চালানো। এমনকি বরফ পরিস্কার বা ঘাস ছাঁটার ব্যাপারেও লিঙ্গভেদ নেই। সবাই সব কাজ শেখে এবং করে। তার ফলটা হল এই যে কেউ কোনো ছাঁচে পড়ে যেতে বাধ্য হয় না, যেটা শারীরিক এবং মানসিক ভাবে খুবই স্বাস্থ্যকর।
আমেরিকায় মেয়েরা যখন থেকে চাকরি শুরু করল, তখন থেকে এদেশের গ্রসারি স্টোর্সগুলো, অর্থাৎ বাজারহাট, ৭ দিনই ২৪ ঘন্টা খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিল। স্বামী স্ত্রী যে পারে, যখন পারে, বাজার করে আনবে। এই সিদ্ধান্তটা যে কর্মরতা মায়েদের পরিবারের জন্য কি সুবিধাজনক, তা আমি নিজে কাজ শুরু করার পর বুঝেছি। শুক্রবার রাত্রে বাজার করে রাখলে, শনিবার সকাল সকাল রান্না চাপিয়ে দেওয়া যায় — ভারতীয় রান্না পৃথিবীর সব জাতির রান্নার চেয়ে সময়সাপেক্ষ, তাই কর্মরতা মহিলাদের জন্য সপ্তাহান্তই ভরসা। শনি-রবি দু’দিনের মধ্যে সপ্তাহের রান্না, কাপড় কাচা, বাচ্চাদের ‘এ্যাক্টিভিটিজ’ সামাল দেওয়া বেশ কঠিন — স্বামী স্ত্রী দু’জনে হাত লাগালেও। তাই কিছু কাজ এগিয়ে রাখলে এবং সময়ের বাধা না থাকলে একটু সুবিধে হয়।
হয়তো এটা ভারতবর্ষেও ক্রমশঃ হবে বা হচ্ছে।
আসলে কিছু জিনিস, যেগুলো মূলত বাহ্যিক — সেগুলো বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীতেই এক হয়ে যাবে বলে মনে হয়। কিন্তু কিছু জিনিস হচ্ছে আভ্যন্তরীণ — যেমন সম্মানবোধ। নিজেকে বা অন্যকে সম্মান করতে জানা। এগুলো যদি ভেতর থেকে না পাল্টায়, তবে পরিবর্তন আসা খুবই দুষ্কর। আর ভেতর থেকে পাল্টাত গেলে, শিকড়ের গোড়ায় দিতে হবে টান।
সব শেষে, লিণ্ডার গল্প বলে নারীবাদের এই আলোচনায় ইতি টানব।
আমার সঙ্গে পি এইচ ডি করত লিণ্ডা।
দশবছরের বিবাহিত জীবন কাটানোর পর, ওর স্বামী লিণ্ডাকে ডিভোর্স ক’রে অফিসের সেক্রেটারীকে বিয়ে করে। বেশ কিছুদিন ধরেই সেক্রেটারীর সঙ্গে সম্পর্ক চলছিল, পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত।
লিণ্ডা আগে কাজ করত না। বিবাহবিচ্ছেদের পর, স্বামীর কাছ থেকে ‘ক্ষতিপূরণ’ হিসাবে মাসিক টাকা পেলেও, ও আবার পড়াশোনা করার সিদ্ধান্ত নেয়। লিণ্ডা নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়, যাতে স্বামীর টাকার প্রয়োজন ওর না হয়।
খুব হাসিখুশী ছিল লিণ্ডা। অনেক গল্প করত।
আমি একদিন লিণ্ডাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে কেন ও স্বামীর টাকা নিতে চায় না — বিনাদোষে যে লিণ্ডাকে ছেড়ে চলে গেছে, লিণ্ডার জীবনের মূল্যবান দশটা বছর নষ্ট করে দিয়ে, তার তো ক্ষতিপূরণ দেওয়াই উচিত। খুব সহজভাবে লিণ্ডা আমাকে যা বলেছিল, তা’ হল এই – “জীবন তো একটাই, সেই জীবনে গর্ডন (ওর স্বামী) যদি কারুর সঙ্গে থেকে বেশী সুখী হয় তবে সেটা ও করতেই পারে। গর্ডন আমাকে সোজা বলেছে যে ও বিচ্ছেদ চাইছে, ও কোনদিন আমাকে অপমান করেনি। দশবছর তো আমরা সুখে ছিলাম, সেটা তো মিথ্যে নয়। এই যে আমি আজ পি এইচ ডি করছি, আমার দিগন্ত প্রসারিত করছি, এগুলো তো কিছুই হত না যদি গর্ডন আমাকে ডিভোর্স না করত। এরপরেও আমার জীবনটা নিয়ে আমি যদি অন্য কিছু করতে চাই, তাহলে করব। আর সেটা নিজের রোজগারে করব, গর্ডনের দেওয়া পয়সায় নয়। জীবনে সব অভিজ্ঞতারই দাম আছে, কিছুই নষ্ট হয় না।”
শুনে আমার মনে হয়েছিল যে লিণ্ডা যেন পাঁচ মিনিটে আমাকে নারীবাদের সারকথা বুঝিয়ে দিল। মনে হয়েছিল — যেদিন সব নারী এইভাবে ঋজু দৃঢ়তায় সম্মানের সঙ্গে নিজের জীবনকে নিজে পরিচালিত করবে, এবং তার চেয়েও বড়ো কথা যেদিন সব গর্ডনরা লিণ্ডাদের সঙ্গে অন্যায় করলেও তাদের অপমান করবে না, সেদিন স্বদেশে-বিদেশে ‘নারীবাদ’ এক হয়ে যাবে। সেদিন নিউজ-চ্যানেল এবং ইন্টারনেটে ভাইরাল-হয়ে-যাওয়া কোনো ভারতীয় সংবাদের জন্য আমাকে মাথা নীচু করতে হবে না।
সেদিন পাশ্চাত্যে বসে ‘নারীবাদ’ নিয়ে আবার নতুন করে লিখব।
সেইদিনের অপেক্ষায় রইলাম।




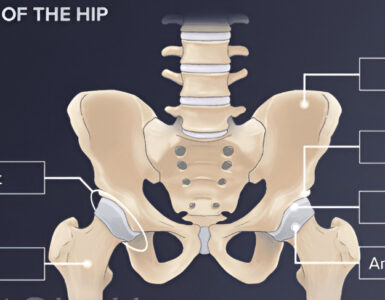











Add comment